জমিদার রবীন্দ্রনাথ
লিখেছেন:জমিদার রবীন্দ্রনাথ
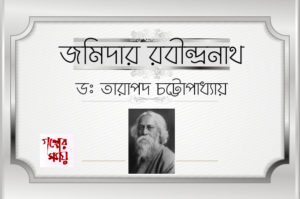
রবীন্দ্রনাথকে জমিদার হওয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার ও উপেক্ষা করার সবরকম চেষ্টা করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন বিরল প্রতিভার মানুষ। তিনি নানা দিকে বিশাল ব্যবসা বাণিজ্যের স্থপতি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে এ বিষয়ে সারা ভারতেই পথিকৃৎ বলা যায়। বিপুল ধন সম্পত্তির মালিক হয়েও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারীদের এই সব ব্যবসা সার্থকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা নেই। তাই প্রথমবার বিলেত যাবার আগে ১৮৪০ সালের ২০ অগস্ট তারিখে তাঁর যাবতীয় জমিদারি একটা ট্রাস্ট ডিড্ করে সুরক্ষিত করে রেখে গিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে জোড়াসাঁকোর বসত বাড়ি আর দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়িটিও তিনি সুরক্ষিত করে গিয়েছিলেন। মাত্র ৫২ বছর বয়সে ইংলন্ডে দ্বারকানাথের জীবনাবসানের পর তাঁর বিশাল ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যের পতন হতে শুরু করে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া বিস্তীর্ণ জমিদারি রক্ষা পায়। এবং এই জমিদারির সাহায্যে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ জীবন ভোর আর্থিক সচ্ছলতা ভোগ করে গেছেন।
প্রিন্স দ্বারকানাথের জমিদারির অন্তর্গত ছিল নদিয়ার বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ, পাবনা জেলার সাজাদপুর এবং রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগণা। কালীগ্রাম পরগণার সদর ছিল পতিসর। উড়িষ্যা ও অন্যান্য জায়গায়ও দ্বারকানাথের কিছু জমিদারি ছিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠতম হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ এজমালির সম্পত্তি যাবতীয় জমিদারির দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের কাজ পরিচালনা করতেন। তারপর দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ্যপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব পান। সবশেষে এই দায়িত্ব পান রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথমেই এই দায়িত্ব পান নি – পেয়েছেন পুরো পাঁচ বছর শিক্ষানবিশি এবং ইনস্পেকশনের অভিজ্ঞতার পর। ১৯৮০ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির কাজ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেন। রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল সদর কাছারিতে নিয়মিত উপস্থিত থেকে প্রতিদিনের আয় ব্যয় ও হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে তার সারমর্ম নোট করে রাখা এবং প্রতি সপ্তাহে তার রিপোর্ট পির্তৃদেবকে পাঠান এবং তার ওপর পিতৃদেবের উপযুক্ত উপদেশ মত কাজ করা। দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে রবীন্দ্রনাথের তৎপরতা ও বিচক্ষণতার উপযুক্ত পরিচয় পেলে তবেই তাঁর ওপর জমিদারির দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই কঠোর শিক্ষানবিশির কাজ খুবই দুশ্চিন্তার ছিল। কারণ দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি বিষয়ের খুটিনাটি খুব ভাল করে বুঝে নিতেন – কোনও কিছু এদিক সেদিক হবার উপায় ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হয়েই রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৫ সালের ৮ আগস্ট “পাওয়ার অব এটর্নির” মাধ্যমে পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সমগ্র এজমালির জমিদারি সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব পান অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জমিদার রূপে নিযুক্ত হন।
অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু অনভিপ্রেত দিক থাকলেও জমিদার হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্য। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, “এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি – রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।” পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার ‘পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদারি জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয় – এর মধ্যে পৌরুষও নেই গৌরবও নেই।” (কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ ৩৪৭)।
যে জমিদার এই কথাগুলি বলেন, তিনি যে অন্য জমিদার থেকে ভিন্ন প্রকারের হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জমিদার হয়ে রবীন্দ্রনাথ পূন্যাহ উৎসব যোগ দিতে শিলাইদহে যান। সেখানে গিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের পথে হাঁটবেন না। পূন্যাহ হল জমিদারিতে নতুন বৎসরের খাজনা আদায়ের সূচনা উৎসব। ধুতি – পাঞ্জাবি – চাদর পরে যুবক জমিদার এলেন কাছারিতে। বন্দুকের আওয়াজ, রোশনাই আলো, উলু আর শঙ্খধ্বনিতে কাছারিবাড়ি মুখর। প্রথামত প্রথমে আদি ব্রাক্ষ্ম সমাজের আচার্যের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হ’ল। পরে হ’ল হিন্দু মতে পূজা। পুরোহিত মশাই জমিদার বাবুর কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিলেন।জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মর্যাদা অনুযায়ী বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে পূন্যাহ অনুষ্ঠানে। হিন্দুরা সতরঞ্চির ওপর চাদর ঢাকা দেওয়া আসনে একধারে বসবেন। তার মধ্যে ব্রাক্ষ্মণদের স্থান আলাদা করা হয়েছে। অন্যধারে মুসলমানদের বসবার জায়গা করা হয়েছে। তাঁদের বসবার জায়গায় শুধু সতরঞ্চি, চাদর নেই। সদর কাছারিতে ও অন্যান্য কাছারির কর্মচারীদের মর্যাদা অনুযায়ী বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রথা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে চলে এসেছে। জমিদার বাবুর বসবার জন্য মখমল মোড়া সিংহাসন।কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সিংহাসনে বসলেন না। তিনি সদর নায়েবকে বললেন যে পূণ্যাহ হ’ল মিলনের উৎসব। এই আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা চলবে না। সদর নায়েক যখন বললেন এই আনুষ্ঠানিক দরবারে পুরনো রীতি বদলাবার অধিকার কারও নেই। বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন, আসনের জাতিভেদ তুলে না দিলে তিনি কিছুতেই বসবেন না। জমিদার হিসাবে তাঁর প্রথম হুকুম হ’ল সবার জন্য এক আসন করতে হবে। তিনি উপস্থিত প্রজাদের সব আলাদা আসন ব্যবস্থা সরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে বসতে বললেন। প্রজারাও সব চাদর ও চেয়ার সরিয়ে দিয়ে ঢালাও সতরঞ্চির ওপর বসে পড়লেন। মাঝখানে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। নায়েব গোমস্তার দল অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু প্রজারা অবাক হয়ে তাদের নতুন জমিদার বাবু মশাইকে দেখলেন।
রবীন্দ্রনাথ প্রারম্ভিক ভাষণেই ঘোষণা করলেন “সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।” যেহেতু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ মহাজনই সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু সেজন্য রবীন্দ্রনাথ মহাজন অর্থে “সাহা” শব্দের ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে তাঁর জমিদারিতে অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র মুসলমান। তাই দরিদ্র প্রজা বলতে তিনি “শেখ” শব্দ ব্যবহার করেছেন।
তাঁর জমিদারির সময় দরিদ্র প্রজাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সব কল্যাণমূলক কাজ করেছেন তা অন্যান্য অধিকাংশ জমিদাররা কল্পনাও করতে পারবেন না। তিনি প্রজাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছেন।জমিদারির দায়িত্ব পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, গ্রামই ভারতের প্রাণ, গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। গান্ধীজীও একই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন এবং সারা জীবন গান্ধীজী গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি এমন কি গ্রাম স্বরাজের কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে পল্লী উন্নয়নের দিকে নজর দেন এবং সচেষ্ট হ’ন। পল্লীর সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত “পল্লী প্রকৃতি” পুস্তিকায় গ্রন্থিত হয়েছে। কবি বলেছেন, “শিলাইদা পতিসর এই – সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ দুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরু তলে তাদের কুটীর – আর এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌছত।” (“পল্লীপ্রকৃতি,” রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ ৫৩৬)। জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে “উপেক্ষিতা পল্লীর” সমস্যা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
প্রজাদের উন্নতিকল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি এলাকায় একের পর এক কাজ করে গেছেন। শিলাইদহে স্থাপিত হ’ল মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়। পতিসরে বড় হাসপাতাল তৈরি করলেন। কালীগ্রাম পরগণায় তিনটি বিভাগে রাখলেন তিনজন ডাক্তার। ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথই হেলথ্ – কো অপারেটিভ করে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাঁর জমিদারিতে।
প্রজাদের দান খয়রাতের ওপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্বেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন হিতৈষী বৃত্তি ও কল্যাণ বৃত্তি। এই দুই বৃত্তি বাবদ যে টাকা সংগৃহীত হ’ত তার সবটাই প্রজাদের ও জমির উন্নয়নের জন্য খরচ করা হ’ত। প্রজাদের কাছ থেকে হাল – বকেয়া খাজনার টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসাবে হিতৈষী বৃত্তি আদায় করা হ’ত। মোট আদায়ের সমপরিমাণ টাকা জমিদারি সেরেস্তা থেকে দেওয়া হ’ত। প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হিতৈষী সভা সেই টাকা কী ভাবে খরচ হবে ঠিক করত । এ ছাড়া কল্যাণ বৃত্তি আদায় করা হ’ত। এর জন্য রসিদ দেওয়া হ’ত। কল্যাণ বৃত্তিতে যত টাকা আদায় হ’ত, জমিদার ঠিক সমপরিমাণ টাকা দিতেন। বছরে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা সংগৃহীত হ’ত। তা ছাড়া নাম খারিজের নজরানা সরকারি শতকরা পাঁচ টাকা আদায় হ’ত। এই সব টাকা খরচ করা হ’ত রাস্তাঘাট নির্মাণে, মন্দির – মসজিদ সংস্কারে, স্কুল – মাদ্রাসা স্থাপনে। চাষীদের বিপদ – আপদে সাহায্যের জন্যও এই টাকা খরচ করা হ’ত।
রবীন্দ্রনাথ কুষ্ঠিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা তৈরি করিয়ে দেন এই শর্তে যে ঐ রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। আবার জলের জন্য কুয়ো খোঁড়ার দায়িত্ব দেন গ্রামবাসীদের আর রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নেন জমিদারি এস্টেট থেকে কুঁয়ো বাঁধানোর। ঠিক একই পদ্ধতিতে পুকুর সংস্কারও চলে। পতিসরে তিনি একটি ধর্মগোলাও স্থাপন করেন।
চমকপ্রদ ব্যাপার হ’ল শিলাইদহ ও পতিসরে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন। সেখানে সুদূর অতীতে সেই ১৯১০ সালে ব্যবহৃত হয় ট্রাকটর, জল দেবার জন্য পাম্পসেট, জমিতে ব্যবহৃত হয় সার এবং চাষ হয় উচ্চ ফলনশীল ফসল। অধিক ফলনের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি ল্যাবরেটরি। প্রজাদের বসতবাড়িতে খালি জায়গায় তিনি আনারস, খেজুর, কলা ও অন্যান্য ফলের গাছ লাগাবার জন্য উৎসাহ দেন। আলুচাষের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন।
শুধু কৃষিকার্য নয়, প্রজাদের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বয়ন শিল্প শিখতে একজন তাঁতীকে তিনি শ্রীরামপুরে পাঠান। এক মুসলমান জোলাকে শান্তিনিকেতনে পাঠান তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি ফিরে এসে তাঁতের স্কুল খুললেন। এছাড়া পতিসরে ধানভাঙা কল, শিলাইদহ অঞ্চলে পটারির দ্বারা মাটির জিনিষ তৈরি, ছাতা তৈরির কল বসানোর কাজেও কবির নজর ছিল। সাধারণ প্রজারা পয়সার অভাবে টিনের চালা করতে পারে না। ব্যপকভাবে খোলা তৈরি করতে পারলে লোকের খুব উপকার হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।
পল্লী উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর “সমবায়নীতি” পুস্তিকায় কবি সমবায়ের গুরুত্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং চেয়েছেন, তাঁর দরিদ্র প্রজারা সমবায়ের সাহায্যে নিজেরাই তাঁদের দারিদ্র দূর করতে সচেষ্ট হোক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র। …… বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা কিছু দামী এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি – জমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না। তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়।” (“সমবায়নীতি”, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ ৪১৫)। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যদি প্রত্যেক চাষী নিজের ছোট জমিটুকুকে অন্য জমি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে না দেখে, সকলের জমি এক করে একযোগে চাষ করতো, তবে অনেক হাল কম লাগত, অনেক বাজে মেহনত ও খরচ বেঁচে যেত। তেমনি অনেক চাষী মিলে যদি এক গোলায় ধান তুলতে পারত ও এক জায়গা থেকে বেচবার ব্যবস্থা করত তাহলে স্বতন্ত্র গাড়ির খরচ ও স্বতন্ত্র মজুরির হাত থেকে বাঁচা যেত। যার বড়ো মূলধন আছে, এই সুবিধা থাকায় সে অনেক বেশি মুনাফা করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ডেনমার্কের মত দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, সেখানে সাধারণ মানুষ জোট বেঁধে মাখন-পনির-ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসা খুলে দেশ থেকে দারিদ্র্য একেবারে দূর করে দিয়েছে। এমনি করে অনেক গৃহস্থ, অনেক মানুষ একজোট হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার যে উপায় তাকেই যুরোপে কোঅপারেটিভ প্রণালী বা বাংলায় সমবায় নাম দেওয়া হয়েছে। এই কোঅপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় বলে কবি মনে করেন। সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। উদ্ধৃতি ভারাক্রান্ত হওয়ার ত্রুটি স্বীকার করেও কবির অননুকরণীয় ভাষায় সেটা উপস্থিত করতে চাই। কবি বলেছেন “লঙ্কার বহু খাদ্যখাদক দশমুন্ডধারী বহু–অর্থ – গৃধনু–দশ–হাত–ওয়ালা রাবণকে মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধশক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই – সংঘটি বেঁধে ছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচন্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্যে সেই প্রেমকে চাই, সেই মিলনকে চাই, (তদেব পৃ ৪২৭)। সাধারণ মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কবি বলেছেন, “… এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত সভ্যতায় ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে (তদেব, পৃ ৪৩৬)।
মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্য কবি সমবায় পদ্ধতিতে পতিসরে ১৯০৫ সালে একটি কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। চাষিদের অল্প সুদে ঋণ দেবার জন্যই এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল। ফলে প্রজাদের দারুন উপকার হয়। তাঁরা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মহাজনের দেনা শোধ করে দেন, এবং মহাজনেরা ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যান। এই ব্যাঙ্ক কুড়ি বছর চলেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কো – অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অ্যাক্ট ১৯০৪ সালে পাশ হয় এবং ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক ছিল ভারতবর্ষে প্রথম কৃষি ব্যাঙ্ক। ১৯১৩ সালের সময় পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। কবি ওই সময়ে নোবেল পুরস্কার বাবদ যে এক লক্ষ ষোল হাজার টাকা পান তা থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা ওই ব্যাঙ্কে রাখেন। অবশ্য ওই টাকা কবি আর ফেরৎ পান নি।
চাষীদের ধান ও পাট ন্যায্য মূল্যে কিনে নেবার জন্য কবি ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় “ট্যাগোর এন্ড কোং” স্থাপন করেন। এর ফলে উৎপাদকদের ন্যায় সঙ্গত দাম পাওয়ার সুবিধা হ’ল। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পথ সুগম হয়।
জমিদারি সেরেস্তার কাজেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ব্যবস্থার সূচনা করেন। বিরাট শ্রম সাপেক্ষ জমা–ওয়াশিল কাগজের বদলে তিনি কার্ড ইনডেক্স প্রথা প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ মন্ডলী প্রথার প্রবর্তন, এটা হ’ল কেন্দ্রীভূত জমিদারি ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি বিরাহিমপুর পরগণায় প্রথমে করলেন তিনটি বিভাগীয় কাছারি। এরই নাম দেওয়া হ’ল মন্ডলী। এর ফলে প্রজা ও জমিদারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হ’ল এবং প্রজা –জমিদার সমবায়ে গড়ে উঠল বলিষ্ঠ এক শক্তি। আমলাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও অবৈধ অর্থ আদায়ের সুযোগ দূর হ’ল। এতদিনের উপেক্ষিত প্রজারা আনন্দিত হলেন। এই ব্যবস্থায় সাফল্য দেখে কবি পরে আরও দুটি কাছারি খুললেন। ১৯০৮ সালে চালু এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মন্ডলীতে নায়েব (অধ্যক্ষ) বাদে দুজন হিন্দু আর দুজন মুসলমান প্রজা সভ্য থাকতেন। এরা প্রতি সপ্তাহে সভা করে সব ব্যবস্থা নিতেন। এই ব্যবস্থায় শিলাইদহ সদর কাছারির গুরুত্ব কমে গিয়েছিল।
প্রজাদের মধ্যে বিবাদের বিচার ও মীমাংসা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সালিশির ব্যবস্থা করেন। এটা এক নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা একজনকে প্রধান মনোনীত করতেন। পরগণার সব প্রধানদের মধ্য থেকে গ্রাম প্রধানরা পাঁচজনকে মনোনীত করতেন। তাঁদের পঞ্চপ্রধান বলা হত। এরা গ্রামের লোকেদের বিবাদ – বিরোধ মিটিয়ে দিতেন। এদের রায়ে কেউ অসন্তুষ্ট হলে শেষ আপিল হ’ত রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ আদালতে গেলে গ্রামের লোকেরা তাকে সমাজচ্যুত করতেন। এই বিচার ব্যবস্থায় কোন খরচ লাগতো না, বিচারে বিলম্বও হ’ত না। এই ব্যবস্থা কালীগ্রাম পরগণায় রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরেও দেশ বিভাগ পর্যন্ত চলেছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের আমলে বিবাদ বিরোধ মীমাংসার জন্য কেউ আদালতে যেত না।
প্রজাদের তথা গ্রামের উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি আন্তরিক ছিলেন তা বোঝা যায় একটি ঘটনায়। সে যুগে সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা বিদেশ যেতেন আই. সি. এস, ব্যারিস্টার বা ডাক্তার হবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর এন্ট্রান্স পাশ করা জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে ১৯০৬ সালে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শিক্ষা করতে। আবার পরের বছর ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকেও রবীন্দ্রনাথ বিদেশে পাঠালেন কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য। পল্লী উন্নয়নের জন্য নিজের ঘনিষ্ঠ জনদের শিক্ষার পরিচিত পন্থা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পথে পাঠানো তখনকার দিনে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নেই।
সে যুগে অধিকাংশ জমিদাররা শহরে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, বাস করে, নায়েব, গোমস্তা দিয়ে জমিদারি শাসন করতেন ও মাঝে মাঝে মহলে গিয়ে ফুর্তি করতেন আর কর্তৃত্ব জাহির করতেন। আবার দয়ালু সাজবার জন্য নিজের ইচ্ছামত দানধ্যান করতেন।
প্রয়োজন অপ্রয়োজনে প্রজাদের খাজনাও মকুব করতেন ইচ্ছামত। রবীন্দ্রনাথ এর কোনটাই করলেন না। খেয়াল খুশিমত সাধারণ খাজনা মকুবের পরিবর্তে শুধু প্রকৃত দুঃস্থদের অথবা অজন্মা হলে চাষিদের রেহাই দিতেন। বিশেষ করে প্রান্তিক চাষিরা যাতে অসুবিধায় না পড়ে, তা তিনি দেখতেন। আবার উন্নত ব্যবস্থাপনায় ফসল ভাল হলে খাজনা বাড়িয়েও দিতেন। প্রকৃতপক্ষে উন্নত ধরণের চাষাবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির আয়ও বাড়িয়ে ছিলেন। উন্নত কৃষিব্যবস্থা ও সমবায়ের মাধ্যমে কবি প্রজাদের নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন যাতে জমিদারের দান খয়রাতির উপর প্রজাদের নির্ভর করতে না হয়। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ণের উদ্দেশ্যও ছিল তাই।
জমিদারি এস্টেটকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ ওয়েলফেরায় এস্টেটে পরিণত করেছিলেন। ১৯১৬ সালের রাজশাহী জেলা গেজেটায়ারে এল. এস. এস. ও–ম্যালে, আই. সি. এস. –এর বিস্তারিত প্রশংসাসূচক বর্ণনা থেকে এ বিষয়ে বিশদ জানা যায়। গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে, – “It must not be imagined that a powerful land lord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer’s account of the estate of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zamindrs ………”
তবে শিলাইদহ পতিসরে পল্লী মঙ্গল সাধনে কবি যে সাফল্য পেয়েছিলেন, শ্রীনিকেতনে চেষ্টা করেও তার অর্ধেক সাফল্য তিনি লাভ করতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করেছেন।
পরবর্তীকালে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। শিলাইদহের জমিদারি পান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ। সাজাদপুর যায় গগনেন্দ্র–সমরেন্দ্র–অবনীন্দ্রদের অধীনে। একমাত্র রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণা রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি হিসাবে থেকে যায়। পতিসর কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত যান ১৯৩৭ সালে। সেখানকার শতকরা ৮০ জন প্রজাই ছিলেন মুসলমান চাষি। তাঁরা সদর কাছারিতে একত্রিত হয়ে “মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরগণায় শুভাগমন” উপলক্ষে সংবর্ধনা দেন। তাঁরা এই বলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন – “প্রভুরূপে হেথা আস নাই, তুমি/দেবরূপে এসে দিলে দেখা/ দেবতার দান অক্ষয় হউক/ হৃতিপটে থাক স্মৃতিরেখা/” অভিভূত রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, “তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না।” রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, “তোমরা আমার বড় আপনজন, তোমরা সুখে থাক। …… তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি। …… তোমাদের সবার উন্নতি হোক – এই কামনা নিয়ে আমি পরলোক চলে যাব।” জমিদার প্রজার এই মধুর সম্পর্ক বিরল।
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ও জমিদারের কনসেপ্ট বা ধারনাই পাল্টে দিয়েছিলেন। প্রজাদের জন্য তাঁর দরজা সব সময়েই খোলা থাকত। সকাল, দুপুর, রাত্রি যে কোনও সময় কবির কাছে প্রজারা তাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে পারত। কবিও ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনতেন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ জমিদারিকে আর পাঁচটা ব্যবসার মতই পরিচালনা করতেন। যদিও তিনি দেখতেন এবং নির্দেশ দিতেন যেন তাঁর জমিদারিতে প্রজা পীড়ন না হয়। দেবেন্দ্রনাথের কাছে জমিদারি ছিল খাজনা আদায়ের উৎস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জমিদারি শুধু খাজনা আদায়ের যন্ত্র ছিল না; তিনি ছিলেন প্রজাদের প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক। তাই জমিদার রবীন্দ্রনাথকে আমরা অন্যান্য জমিদার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রচেষ্টায় জমিদারির চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল। বড় বড় রাস্তা তৈরি হ’ল, মন্দির দরগার সংস্কার হ’ল, ঘরে ঘরে তাঁত বসল, উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হ’ল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হ’ল, …… মাদ্রাসা, টোল–স্কুল বসল, ঋণ সহজলভ্য হ’ল, উৎপাদিত ফসল সহজে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হ’ল, বিনা খরচে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা হ’ল – এক কথায় প্রজাদের জীবন যাত্রার পদ্ধতিই পাল্টে গেল।
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করে এই নিবন্ধের ইতি টানতে চাই। বাংলা তথা ভারতের পরম সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারি পরিচালনায়র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এর ফলে কলকাতা নিবাসী কবি নদীমাতৃক বাংলার রূপটি সযত্নে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। শস্য শ্যামলা বাংলার উন্মুক্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নদীর কলধ্বনি–রূপসী বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল এবং কবির রাশি রাশি অমূল্য সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা পরিণতি লাভ করেছিল পল্লীবাংলার সঙ্গে এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলেই। এবং এর ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। জমিদার রবীন্দ্রনাথই ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার-
১) অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , কলকাতা ৭৩, ১৪০৫।
২) আবদুশ শাকুর, রবীন্দ্রনাথ মানুষই ছিলেন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা – ৭৩, ২০১২।
৩) সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , কলকাতা – ৭৩, ১৪১৮।
৪) কৃষ্ণ কৃপালনী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিস্মৃত পথিকৃৎ, অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৮৪।
৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্ন পত্রাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা – ১৪০৯।
৬) শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবন কথা, বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ। ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা – ৭, ১৯৬১।

মতামত
আপনার মন্তব্য লিখুন
আপনার ইমেল গোপনীয় থাকবে।