রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা ভাবনা
লিখেছেন:ডা. পি কে দাস
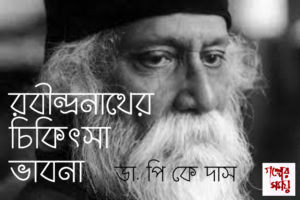
জোড়াসঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলের বৈঠকখানায় ঝোলানো একটা পূর্ণাবয়ব মানব স্কেলিটন। গাঢ় অন্ধকারে গা ছমছম করে। এক অজানা ভয়ে হিম হয়ে যায় সারাটা দেহ। তবুও ভয়ডর নেই সদ্য যুবক রবীন্দ্রনাথের। গৃহশিক্ষক একজন মেডিকেল কলেজে পড়া ছাত্র। তার কাছে জানার অন্ত নেই অল্প বয়সী যুবকের। ওই বয়সেই মুখস্থ মানবদেহের সব হাড়গোড়ের নাম। এমন কি দেহের মধ্যে হাতে পায়ে যে কটা ছোট্ট ছোট্ট হাড় আছে সেটাও তার কণ্ঠস্থ। যুবক মনে সদাই জাগে মানবদেহের রহস্য। দেহটাকে জানলে পরে তবেই না বাইরের জগত্টাকে চেনা যাবে! কৌতূহলে ভর করে বায়না জানানো হল গৃহশিক্ষককে। একবার অ্যানাটমির ডিসেকশন হলটা দেখতে যাবে। কেমন করে শব ব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীরা সেটা দেখা তার ঐকান্তিক ইচ্ছে। কিছুটা ইতস্তত করেও গৃহশিক্ষক নিয়ে গেলেন অ্যানাটমির ডিসেকশন হলে ছাত্রের অপার কৌতূহল মেটানোর জন্যে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমির ডিসেকশন হলে দাঁড়িয়ে যুবক রবীন্দ্রনাথ তো হতবাক! মুখে কথা সরছে না। অবাক চোখে দেখতে লাগলেন ছাত্রছাত্রীদের শব ব্যবচ্ছেদ করার পদ্ধতিগুলো। বাড়ি ফিরে এলেন মনের আনন্দে। ওই বয়সে পড়ে ফেললেন অ্যানাটমি, ফিজিওলজির সব বইগুলো। জ্ঞানের সমৃদ্ধতায় ভরে উঠলো মনপ্রাণ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন ৩১ বছর। ‘সাধনা’ পত্রিকায় জীবনের শক্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের হৃৎপিণ্ড চারটি কোটরে বিভক্ত, তাহার মধ্যে দুইটি কোটরে শরীরের রক্ত আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি অংশে স্যাকরার হাপরের মতো সংকুচিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। … সুস্থ শরীরে বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫/৭৬ বার সংকুচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘন্টায় যে শক্তি ব্যয় করে সেই শক্তি দ্বারা তিন হাজার মণের অধিক (২২০ টন) ভার এক ফুট উর্দ্ধে তুলা যাইত।’ আর একটি অংশে উল্লেখ করেছেন, ‘বিশ্রামকালে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গইঞ্চি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং পরিশ্রমকালে সেই বায়ুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো নব্বই বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িতে পারে।’
সাধনা পত্রিকায় ওনার আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ‘মানব শরীর’ নামে। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই সমস্ত কাজ কত শৃঙ্খলাপূর্বক নির্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা যোগাইতেছে কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষু তারকা সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস, নির্মাণ করিতেছে…”।
‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘রোগ শত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য’ প্রবন্ধে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের কঠিন বিষয়গুলিকে সাধারণ লোকের বোঝার জন্যে তিনি লিখেছেন, ‘রোগস্বরূপ বাহিরের যে সকল জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে ইহারা (শ্বেতকণিকা) তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতিমত হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণকারীগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরে রক্ষক সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।’ ওই প্রবন্ধের একেবারে শেষের দিকে লিখেছেন, শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাস্ত করিতে পারে। অনাচার, অতিশ্রম, অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউটা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।
স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য যথাযথ পুষ্টির প্রয়োজন আছে একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি পুষ্টি বিষয়ক এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই যে জার্মানি, অস্ট্রিয়ায় প্রতিভা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দৈহিক দুর্বলতা তার অন্যতম প্রধান কারণ । আবার মায়ের দুধের যে কোন বিকল্প হয় না সে বিষয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন এই বলে যে, ‘যে সমস্ত সমস্ত প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুগের শিশুরা অপুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল’। গ্রামের উন্নতির কথা তিনি বিশেষভাবে ভাবলেন। গাঁয়ের মানুষের হতশ্রী চেহারা দেখে তিনি মনে মনে দারুণ কষ্ট পেলেন এবং সেটাকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, ‘গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু অসহায় ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে দগ্ধ করেছিল।’ তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, দারিদ্র থাকলে রোগ কোনদিনই দূর হবে না। আর এই কাজে কেউ বাইরে থেকে এসে করে দিলেও সেটা স্থায়ী হবে না। এরজন্য প্রয়োজন গ্রামীণ মানুষের সঠিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ। তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে দেশের প্রতিটি গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে অবিরোধী একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্রের বাহক, তেমনি আবার দারিদ্রও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী বারোটি গ্রাম একত্র করে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সকলে বলতে পারে, ‘আমরা পারি, রোগ দূর করা আমাদের অসাধ্য নয়। যাদের মনে তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে। ইতিহাসে তা দেখা গেল’ (দেশের কাজ, ১৩৩৮)। ‘পল্লী সমাজ’, স্বদেশী সমাজ’, ‘পল্লীপ্রকৃতি’ ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে বলেছেন – ‘আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম, সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বারবার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করেনি।’ গ্রামের মেয়েরা নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যাতে কতিপয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন কবি। যেমন, প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিদের ঔষধপত্র, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা। পল্লীর জল, নদীনালা, পথঘাট, সৎকার স্থান, ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা। গৃহ সংখ্যা, জন্মমৃত্যুর সংখ্যা ইত্যাদি এবং ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, তাদের মৃত্যুর সংখ্যা … এসব ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা …।
সুস্বাস্থ্য গঠনে যে খাদ্যের ভূমিকা আছে তিনি একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, নিজে অবশ্য খাদ্য রসিক ছিলেন। খাদ্য নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন নিজের দেহের মধ্যে। বৌমা প্রতিমা দেবীও কথায় কথায়, ‘খাওয়া নিয়ে নানারূপ পরখ করা ছিল ওর চিরকালের বাতিক – সেটা যখনই বাড়াবাড়ি মাত্রায় হত, তখনই দেখেছি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ত।’ তবে খাবার ব্যাপারে নিজেও কয়েকটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেন।
রবি ঠাকুরের রচিত নানা কবিতায় ও লেখার মধ্যে চলে এসেছে অসুখ বিসুখের কথা। যেমন অভিসার কবিতায় রোগাক্রান্ত বাসবদত্তার সেবা করছেন এক তরুণ সন্ন্যাসী : ‘নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায় / ভরে গেছে তার অঙ্গ / রোগ মসীঢালা কালি তবু তার / লয়ে প্রকারণে পুর পরিবার / বাহিরে ফেলেছে করি পরিবার / বিষাক্ত তার সঙ্গ।’ ‘ছুটি’ গল্পে ফটিকের অসুখ, ‘দুই বোন’ গল্পে শর্মিলার অসুখ, ‘ভাইফোঁটা’ গল্পে সুবোধের মায়ের যক্ষ্মা রোগ। রোগের পাশাপাশি মৃত্যুর খবরও চলে এসেছে তাঁর কবিতায়। ‘এ মৃত্যু দেখিতে হবে, এই ভয় জাস’ অন্যভাবে আসিবে ঘুমের মতো মরণের রোল / ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল,” আবার ডাক্তারকে নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গোক্তি কবিতা এখনো সকলের মনে দাগ কাটে, ‘পাড়ায় এসেছে এক নাড়ি টেপা ডাক্তার / দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার / নাম লেখে ওষুধের / এ দেশের পশুদের / সাধ্য কি পড়ে তাহা, এই বড় জাঁক তার / যেথা যায় বাড়ি বাড়ি / দেখেছে ছেড়েছে নাড়ি / পাওনাটা আদায়ের মেলে না যে ফাঁস তার।’
পরবর্তীকালে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে ফেললেন হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকলাপের কাহিনী। ‘সাধনা’ পত্রিকায় ছাপা হল ‘জীবনের শক্তি’ নাম দিয়ে। এর পরে শরীরতত্বের নানান বিষয়ে বিশেষ করে রক্ত সঞ্চালন, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও সংক্রমণ নিয়ে তাঁর উৎসাহ দেখা গেল। এর প্রতিফলন দেখা গেল নানা পত্র পত্রিকায় মানব দেহ নিয়ে তাঁর রচিত বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ রচনা। ‘মানব শরীর’, ‘প্রাণ ও প্রাণী’, ‘রোগ শত্রু’ ও ‘দেহরক্ষক সৈন্য’ ইত্যাদি প্রবন্ধগুলো ছাপা হল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সাধারণ মানুষের কাছে ডাক্তারি ভাষার কঠিন শব্দগুলোকে তিনি বাংলা ভাষায় নতুন করে তর্জমা করে পরিবেশন করেন যাতে সাধারণ মানুষ দেহতত্বের গুরুগম্ভীরতাকে সরলভাবে বুঝতে পারে। যেমন মেডিকেল টার্মিনোলজিতে ‘ফ্যাগোসাইটিক’ কোষগুলোর কাজ হল ক্ষতিকর কোষগুলোকে গিলে ফেলা। তিনি ‘ফ্যাগোসাইটিক’ কোষের নামকরণ করেন ‘ভক্ষক কোষ’। আবার ‘ব্লাড প্লাজমা’র নামকরণ করেন ‘বর্ণহীন রস’ ইত্যাদি।
তৎকালীন সময়ে যে সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে অগ্রগণ্য এ্যালোপ্যাথি। এরপরে ছিল হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, কবিরাজি, হেকিমি ইত্যাদি। তিনি প্রথম থেকে উৎসাহী ছিলেন হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে। তবে এ্যালোপ্যাথি চিকিত্সায় তাঁর কোন রাগ ছিল না। হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক পদ্ধতি নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। ফাদার মুলারের লেখা ‘টুয়েলভ টিসু রিমেডিস’ বায়োকেমিক বইটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি ওই বইটা আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন। তিনি মনে করতেন হোমিওপ্যাথি সিস্টেমে রোগীর নানাবিধ লক্ষণের প্রতি ভাল করে নজর না দিলে চিকিৎসাটা ঠিক করে দেওয়া সম্ভব হবে না। চিকিত্সায় ভুল হয়ে যেতে পারে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ বায়োকেমিক চিকিত্সায় মনোযোগ দিতে হয় গুটিকয়েক লক্ষণের প্রতি। ঠিক ঠিক লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ারও সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। অতি ব্যস্ততার জগতে তাই তিনি বায়োকেমিক পদ্ধতিকে বেশি করে আঁকড়ে ধরতেন। উল্টোদিকে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা যে তাঁর খুব মন পসন্দ ছিল না তা নয়। তবে তাঁর মনে হয়েছিল এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সকলের জন্য নয়। অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব। উপরন্তু সে সময়ে যতজন ভাল ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন সকল স্তরের মানুষ তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারতেন না। এছাড়াও এসব চিকিৎসকদের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি যতটা মন ছিল, চিকিৎসা দর্শনের প্রতি তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সে সময় ছিল পুরোপুরি লক্ষণভিত্তিক। তার অর্ন্তনির্হিত কার্যকারণ বা মানবদেহের দর্শন সম্বন্ধে বেশিরভাগ চিকিৎসক ছিলেন নির্বাক। যতটা ছিল চিকিৎসকদের মান-যশ-খ্যাতি-অর্থের প্রতি টান, রোগীর মন-প্রাণের প্রতি ছিল না ততটা। সে কারণে তাঁর মনে খুব একটা জায়গা করে নিতে পারে নি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি। তবুও হোমিওপ্যাথি কিংবা বায়োকেমিক চিকিত্সার প্রতি তাঁর অন্তরের প্রগাঢ় টান থাকলেও, তিনি কখনো ইতস্তত করেননি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে যখন তার প্রয়োজন হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অর্শ অপারেশনের জন্য বিদেশে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এমনকি ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা নিতেও সম্মত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও অন্যান্য বহু চিকিৎসক। এছাড়া বিদেশে বহু এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের অনেকবারই স্বদেশে-বিদেশে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের এ্যালোপ্যাথি চিকিত্সার জন্যে। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের মেডিকেল বই ও জার্নাল পড়তেন তাঁর নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্যে। এরকম একটি মেডিকেল জার্নাল পড়ে তিনি ‘হাঁপানী’ রোগ সম্বন্ধে বিশদ জানতে পারেন ও তার কার্যকারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অবহিত হন। সে সময়ে তাঁর বৌমা প্রতিমা দেবী তখন ‘হাঁপানী’ রোগে আক্রান্ত। তাঁর অনুগত বৌমাকে সাবধান করেন বাড়ির পোষা জন্তু-জানোয়ার ও পাখির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। কেননা এদের মল-মূত্র অনেক সময় হাঁপানী রোগের কারণ হতে পারে। তাঁর মাথায় সে সময়ে যেটা কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল এটা আজ পরীক্ষিত সত্য যে পশু-পাখির মল-মূত্র মারাত্মক এ্যালার্জি সৃষ্টি করে হাঁপানী রোগ তৈরি করতে পারে। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির এটা একটা চমকপ্রদ দিক! শুধু পড়াশুনা করেই তিনি সময় কাটিয়ে দেন নি, তার ফলিত দিকটা নিয়ত তিনি চর্চা করেছিলেন। তিনি গ্রামের গরীব লোকেদের হোমিও-বায়োকেমিক চিকিৎসা করতেন। মৈত্রেয়ী দেবীর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় জনৈক গ্রামবাসী কাঁকড়া বিছের কামড়ে যন্ত্রণায় যখন ছটফট করছেন সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে হোমিওপ্যাথি চিকিত্তসায় সারিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, রোগীর যন্ত্রণার অনিভূতিটুকু তাঁর হৃদয়ে বহন করেছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোঁজ নিয়েছেন তার যন্ত্রণার উপশম ঘটেছে কিনা। শেষ পর্যন্ত তাঁর ওষুধে যন্ত্রণা কমতে তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণা কমেছিল।
শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিত্সার ভার ছিল সুশীল ভক্তের উপর। তিনি ছিলেন আবার সঙ্গীত ভবনের গানের শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যখনই কোন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়বে তার যেন চিকিত্সার ব্যবস্থা করা হয় সঙ্গে সঙ্গে। আর প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা যাতে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে রপ্ত হয় সে ব্যবস্থা করতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সুশীল ভক্তকে। রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিত্সায় কতটা পারদর্শী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় রাণী মহলানবিশের অসুখের সময়। রাণী মহলানবিশ ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সহধর্মিনী। একবার নির্মলকুমারী মহলানবিশ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিত্সার জন্যে ডাকা হয় সে সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার ও আরও অনেক চিকিৎসককে, কিন্তু তাঁর জ্বর কমাতে কেউ পারেন নি। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হোমিওপ্যাথি চিকিত্সায় নির্মলকুমারী মহলানবিশ টাইফয়েড জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁর সময়ে হোমিও চিকিত্সায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেন ডাঃ প্রতাপ মজুমদার। তিনিও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত নিতেন। কেউ তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে আসলে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। কিন্তু সে সময় তাঁর কাব্য, গান,গল্প,প্রবন্ধ নিয়ে প্রশংসা করলে ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানী। নতুন নতুন চিন্তা ভাবনাও তাঁর মনে অহরহ ঘোরাফেরা করত ও সেগুলোকে তিনি যথাসময়ে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন।
একবার বোলপুর গ্রামে বেশ কিছু অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক কাশির উপদ্রব দেখা দেয়। কোন কিছুতে কাশি যখন কমছে না তখন রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করতে থাকেন এর পেছনে কারণটা কি? তাঁর মাথায় আসে বোলপুর গ্রামটা সমুদ্রতট থেকে অনেক দূরে অবস্থান। তাই এই গ্রামের অধিবাসীদের স্বভাবতঃ নুনের অভাব ঘটতে পারে। এই চিন্তা করে তিনি তার চিকিৎসকদের খাওয়ার নুন বায়োকেমিক বড়ি হিসাবে খাওয়ার জন্য অধিবাসীদের পরামর্শ দেন। অবাক কাণ্ড! তাঁর নিদানেই অধিবাসীদের কাশি অচিরেই উপশমিত হয়।
মেজো মেয়ে রেণুকার অবস্থা খারাপ হওয়ার খবর পেয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন মেয়েকে দেখার জন্যে। মেয়ের অবস্থা দেখে তিনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সব ডাক্তার প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। দেখলেন রক্ত ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। কাশি কমে গেছে। বিকারের প্রলাপ বন্ধ হয়েছে। বেশ স্বাভাবিক লাগছে। একবার রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথের জ্বর সর্দিকাশি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে এ্যাকোনাইট ৩০ ও বেলেডোনা ৩০ পর্যায়ক্রমে দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন। বড় মেয়ে মাধুরীলতার ছেলের চামড়ায় একজিমা হয়েছিল, কবি তাকে হোমিও ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে তুলেছিলেন। পত্নী মৃনালিনী দেবীর অসুস্থতার সময়েও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পরে কবি তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় সারিয়ে তুলেছিলেন।
রোগের নিদান দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি ভাবনা চিন্তা করতেন কিভাবে রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। চিকিৎসা দেওয়ার থেকে রোগটাকে ঠেকানো গেলে সব দিক থেকেই মঙ্গল। তাই তিনি জোর দিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্যে। নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখা, মাঠে ঘাটে বাহ্য না করা, পুকুরের সংস্কার করে জল পরিষ্কার রাখার উপর জোর দিতেন তিনি। তাঁর মাথায় ছিল কো-অপারেটিভ হেলথ সেন্টার গড়ার ভাবনা যেটা গ্রাম ও মফস্বলে চালু করতে পারলে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-চিত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা থাকতো। জনস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। শান্তিনিকেতনের গ্রামে গ্রামে সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্য গড়ার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। গ্রামগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে, পুকুরগুলোকে পরিষ্কার করে গৃহকার্য্যে ব্যবহারের জন্য, জলনিকাশী ব্যবস্থা উন্নত করার কাজে, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর কাজে উৎসাহী হয়ে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ম্যালেরিয়া মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এক ধরণের মশা বিতাড়ন পাউডার তৈরি করেছিলেন যেগুলো শান্তিনিকেতনবাসীদের খুব কাজে লেগেছিল।
সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্য গঠনে তিনি ১৯২৫ সালে ‘বার্থ কন্ট্রোল রিভিউ’ পত্রিকার সম্পাদক মারগারে স্যাঙারকে একটি চিঠি লিখে জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে মতামত দেন। এমনকি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করতে এ ব্যাপারে তিনি পিছুপা হন নি। তিনি লেখেন … I am of opinion that Birth Control movement is a great movement … it will save women from enforced and undesirable maternity … it will help the cause of peace by lessening the burden of surplus population of a country scrabling for food and space outside its own rightful limit. In a hunger-stricken country like India, it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence that could properly be taken case of, causing endless suffering to them. তিনি বুঝেছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও অসুস্থ, অপুষ্ট সন্তানের সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে ভারতবর্ষে। তিনি ১৯২৯ সালে প্রবর্তিত ‘চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন এ্যাক্ট’-কে সমর্থন করেন যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল ছেলের বিয়ের বয়স ২২ ও মেয়ের বয়স ১৬ না হলে বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয়। বাংলায় ‘মেডিকেল শিক্ষা’কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি ১৯১৫ সালে ডাঃ নীলরতন সরকার ও অন্যান্য চিকিৎসকদের সমর্থনে গঠিত কলকাতায় দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (অধুনা আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হিসেবে পরিচিত) গঠনে সহায়তা করেন।
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মনে প্রাণে যে শরীর সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত আহার, যথাযথ ঘুম ও শারীরিক শ্রম করাটা খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এটা খুব মেনে চলতেন। তাঁর দীর্ঘায়ুর পেছনে এটা একটা কারণ। পথ্যের উপর তিনি খুব জোর দিতেন। পুষ্টিকর পথ্য মানেই প্রতিদিন ডিম, মাছ, মাংস খাওয়া নয়, বেশি পরিমাণে শাকসবজি, ডাল, ভাত, ফল খাওয়ার উপর তিনি জোর দিতেন। অল্প আহার বা বেশি আহার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর বদ্ধ ধারণা ছিল মানুষ না খেয়ে মরে কম, খেয়েই মরে বেশি। বিশেষ করে হাবিজাবি আহারের ফলে। মেশিনে তৈরি চালের থেকে বেশি পছন্দ করতেন ঢেঁকিছাঁটা চালের উপর। তিনি পুষ্টি বিশেষজ্ঞ কিংবা বিজ্ঞানী না হলেও তাঁকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আমন্ত্রণ জানায় ‘ফুড ও নিউট্রিশন’-এর উপর একটি আলোচনা সভার উদ্বোধক হিসাবে। দেহ রক্ষা করতে পথ্যের যে বিশেষ অবদান আছে সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্যে তিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক পশুপতি ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করেন। তাঁর আদেশ মান্য করে ডাঃ ভট্টাচার্য এরপরে ‘ডায়েট এ্যান্ড ফুড’, ‘ভারতীয় ব্যাধি ও তার প্রতিকার’ বই দুটি লিখে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ বই দুটি পড়ে উৎসাহিত হয়ে বিশ্বভারতীর ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’য় প্রকাশ করেন ধারাবাহিক ভাবে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ডাঃ ইন্দ্রভূষণ মল্লিক একটি বই লেখেন যার নাম দেওয়া হয় ‘আমাদের দেশের আহার ও শিক্ষা’ সেটি পরবর্তীকালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
চিকিৎসা শাস্ত্রে একটা মেডিকেল ছাত্রকে শিক্ষা দানের সময়ে কতকগুলো নির্দেশনামা শেখানো হয় যেগুলো মাথায় রেখে পরবর্তীকালে নিজের মতো করে চিকিৎসা পদ্ধতি বানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। শুধু বই-এ যা বলা হয়েছে তার আক্ষরিক অনুকরণ না করে তাকে ভাবতে হয় রোগীর মনের অবস্থা, বাড়ির অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা। সেই সব ভাবনা মাথায় রেখে রোগের নিদান ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে রোগের চিকিৎসা হয়তো হয়, কিন্তু রোগটা উপশমের দিকে যাবে কী না সঠিকভাবে বলতে পারবেন না চিকিৎসক। এতে যেমন রোগীর বিড়ম্বনা বাড়বে, তেমনি চিকিৎসকের বিড়ম্বনাও কম হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিকিৎসা দর্শনের কথা চিন্তাভাবনা করতেন সেই চিকিৎসা দর্শনকে মাথায় ঠিক ঠিক নিতে পারলে চিকিৎসক সমাজের প্রভূত উন্নতিসাধন হবে ও উপকৃত হবে আপামর সাধারণ মানুষ।
তাঁর নিজের জীবনেও বেশ কিছু চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটেছে। তাঁর অন্তিম শয্যায় যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাদের সকলের উদ্দেশে লিখেছিলেন :
“পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে
নাম নাই বলিলাম, তাহারা রইল মনে মনে।”
Tags: Dr P K Das, Rabindranath, ডা. পি কে দাস, রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা ভাবনা

মতামত
আপনার মন্তব্য লিখুন
আপনার ইমেল গোপনীয় থাকবে।