সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার
লিখেছেন:সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার
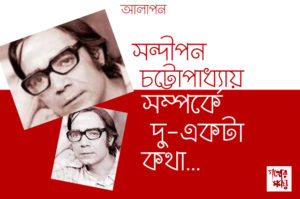
[ বাংলা সাহিত্যে একটি বিতর্কিত নাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন সন্দীপন। লিখন শৈলীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভিন্ন মেরুতে অবস্থান সত্ত্বেও আজও সমান আলোচিত তিনি। সন্দীপনকে নিয়ে লিটল ম্যগাজিন ছাড়া অন্যত্র সেভাবে আলোচনা হয়নি বললেই চলে। নব্বইয়ের দশকে সন্দীপন ভাবনায় আলোড়িত হন তাঁর এক নিবিড় পাঠক প্রবীর চক্রবর্তী। সন্দীপন সান্নিধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সদ্য প্রয়াত ও তৎকালীন তরুণ প্রাবন্ধিক অদ্রীশ বিশ্বাসের। উভয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় একটি অনন্য গ্রন্থ – ‘ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি।’ ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভূমিকা’ প্রকাশন থেকে। এই বইটির জন্য দীর্ঘ আলাপচারিতায় বসেছিলেন প্রবীর চক্রবর্তী, অদ্রীশ বিশ্বাস এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকারটি অনুলিখনের দায়িত্ব পড়েছিল তৎকালীন সাংবাদিক,লেখক এবং বর্তমানে গল্পের সময় পরিবারের অন্যতম সদস্য দেবাশিস মজুমদারের উপর।‘সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি’ বইটি এখন বইবাজারে দুর্লভ। প্রকাশের বছর কুড়ি পর সেই জুলাই মাসেই ‘গল্পের সময়’এর পাঠকদের জন্য সেই সাক্ষাৎকারটির সামান্য বাছাই করা অংশ তুলে আনলেন দেবাশিস মজুমদার। ]
‘সূর্যমুখী ফুল আর বিকালের আলো’। ওই গল্পটা পড়েই তো ফণীভূষণ আচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।
ওটা ফণীভূষণ লিখেছে বটে, তবে প্রথম আলাপ ওটা পড়ে হয়নি। তবে পরবর্তীকালে শুনেছি সুনীল ঐ গল্পটা পড়ে মন্তব্য করেছিল, ‘লোকটা বোধহয় জেলে’। কফি হাউসে কোনো এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম। তখনও সুনীলের সঙ্গে আলাপ হয়নি। আমরা কফি হাউসে আলাদা টেবিলে বসতাম। সুনীলরা আলাদা টেবিলে বসতো। ‘কৃত্তিবাসে’র গোড়ার দিক তখন।
তখন কারা কারা আপনাদের টেবিলে বসতেন?
মিহির সেন, মিহির আচার্য, বীরেন্দ্র নিয়োগী, পূর্ণেন্দু পত্রী, একটু পরে অসীম সোমও আসে।
‘কৃত্তিবাসে’র সঙ্গে আলাপটা কীভাবে ঘটেছে?
আমি তখন ধুতি-শার্ট পরতাম। একথা আগেও অনেক জায়গায় বলেছি – আমি তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে ২৪ বি নূর মহম্মদ লেনে আলাদা থাকতাম। আমার সঙ্গে থাকতো প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।ওখানে বসেই আমি ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ গল্পটা লিখতে শুরু করি।ওখানেই একটা কবিতাও লিখি, যার প্রথম লাইনটা মধুসূদন থেকে ধার করতে হয়েছিল – ‘দাঁড়াও পথিকবর’। ‘এপিটাফ’ নাম।সেটা আমি কোনো ক্রমে লিখি। সেটা পড়ে প্রণব বলল, ‘আরে এতো খাঁটি পয়ার ! চলুন আপনার সঙ্গে সুনীলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি’ – বলে দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে গেল। ওখানেই সুনীলের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর টেবিল বদল হল। পুরনো বন্ধুত্ব কিছু রইলো। ওখানে খুব ইমপর্টেন্ট ছিল যুগান্তর চক্রবর্তী। আমরা দুজনেই ইংরাজি পড়তাম। আমি একবছর পরীক্ষা দিতে পারিনি বলে সে সিনিয়র হয়ে যায়।
হঠাৎ ইংরেজি?
দেবীপদ ভট্টাচার্য বললেন, ‘তুমি তো দেখছি বরাবর বাংলায় কম ইংরেজিতে বেশি নম্বর পাও’। ইংরেজিতেই অ্যাপ্লাই করলাম। এবং চান্সও পেয়ে গেলাম। যাইহোক, যা বলছিলাম। দেশবন্ধু পার্কে ঢুকে দেখলাম ওরা সবে কবিতা লিখছে। মাঝে-মধ্যে মদ-টদ খেতে যায়। শক্তির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর ওরই সঙ্গে প্রথম দিকে ওইসব মদ বিক্রির ঠেকগুলোতে যাতায়াত শুরু করলাম। ওদের মধ্যে আমিই সেই ভাগ্যবান যে প্রথমেই একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল।আর চাকরি পাওয়ার প্রথম দিকে, মানে, মাইনে পাওয়ার প্রথম কয়েকদিন ওদের সঙ্গে থাকতাম। সবাই মিলে খুব পানাদি হত। তারপর চারআনা-আটআনা ওদের কাছ থেকে ধার নিয়ে চালাতাম। আমরা কিন্তু সোনাগাছিতে যেতাম। এই কথাগুলো কিন্তু আমি বলছি না। কারণ, এই যে আমি খরচ করে ফেলতাম, বা ধার নিয়ে কাজ চালাতাম, এগুলো তো আমি কখনও ভাবিনি, লক্ষ্যও করিনি। পরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুরনো দিনের কথা নিয়ে আড্ডা দেওয়ার সময় বিভিন্ন লোক রেফার করেছে।
‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ পর্যায়ের প্রথম যে গল্পটা লিখেছিলেন তা কি ‘বিজনের রক্তমাংস’ নয়?
 না, ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ আমি আগে থেকেই লিখেছিলাম।এসম্পর্কে সুনীলের কথা বলতে হয়।গল্পটা তখন অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছিল। সুনীল কিছুটা পড়েও ছিল। তা, সুনীল নাকি সমীর রায়চৌধুরীকে একটা চিঠি লিখেছিল চাইবাসায়, ‘ সন্দীপন একটা অসাধারণ গল্প লিখছে। শেষ হলে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। তো যাই হোক, এ বিষয়টা আমার কাছে একেবারে আশ্চর্যের নয়। কারণ, ও তো ভীষণ বন্ধু-বৎসল। অবশ্য শুধু ও নয়, সে সময় আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ট ছিল। যে কারণে সকলেই প্রায় প্রেম করতো লুকিয়ে। জানাজানি হলে মারধোর খাওয়ার একটা ভয় ছিল। বন্ধুত্বের বাইরে আর কিছুর যেন কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না আমাদের জীবনে – এরকম একটা ধারণা ছিল। আমাদের তাই এই নিয়মে লুকিয়ে প্রেম করতে হতো। খালি শক্তির ব্যাপারটা একটু আলাদা। ও তো প্রায় বুড়ো বয়সে প্রেম করেছে (চাইবাসায়)। আর তার আগে শক্তি তো কোনোদিনই ও সবের ধার ধারেনি। যে কটা প্রেম করতে গেছে সব কটাই গোলমেলে। এবং অনেকটাই এক তরফা। শক্তি অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষাই করেনি। ও একটা আলাদা ঘরানার মানুষ। ওর মধ্যে যেটা ছিল সেটা ওবিসি স্তরের ব্যাপার। এ জিনিস এসিটিস্ট বা ভদ্দর লোকেরা বুঝতে পারবে না।
না, ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ আমি আগে থেকেই লিখেছিলাম।এসম্পর্কে সুনীলের কথা বলতে হয়।গল্পটা তখন অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছিল। সুনীল কিছুটা পড়েও ছিল। তা, সুনীল নাকি সমীর রায়চৌধুরীকে একটা চিঠি লিখেছিল চাইবাসায়, ‘ সন্দীপন একটা অসাধারণ গল্প লিখছে। শেষ হলে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। তো যাই হোক, এ বিষয়টা আমার কাছে একেবারে আশ্চর্যের নয়। কারণ, ও তো ভীষণ বন্ধু-বৎসল। অবশ্য শুধু ও নয়, সে সময় আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ট ছিল। যে কারণে সকলেই প্রায় প্রেম করতো লুকিয়ে। জানাজানি হলে মারধোর খাওয়ার একটা ভয় ছিল। বন্ধুত্বের বাইরে আর কিছুর যেন কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না আমাদের জীবনে – এরকম একটা ধারণা ছিল। আমাদের তাই এই নিয়মে লুকিয়ে প্রেম করতে হতো। খালি শক্তির ব্যাপারটা একটু আলাদা। ও তো প্রায় বুড়ো বয়সে প্রেম করেছে (চাইবাসায়)। আর তার আগে শক্তি তো কোনোদিনই ও সবের ধার ধারেনি। যে কটা প্রেম করতে গেছে সব কটাই গোলমেলে। এবং অনেকটাই এক তরফা। শক্তি অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষাই করেনি। ও একটা আলাদা ঘরানার মানুষ। ওর মধ্যে যেটা ছিল সেটা ওবিসি স্তরের ব্যাপার। এ জিনিস এসিটিস্ট বা ভদ্দর লোকেরা বুঝতে পারবে না।
আপনার প্রথম পর্বের গল্পগুলোতে যে ব্যক্তির হতাশা ও সংকট চিহ্নিত হয়েছে, তা ওই বামপন্থী বন্ধুবান্ধবরা এবং পত্রপত্রিকাগুলো সমালোচনা করেনি?
হ্যাঁ, ‘বিজনের রক্তমাংস’ তো ‘পরিচয়’ পত্রিকা ফেরত পাঠিয়েছিল। এগুলোই আমায় পার্টি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আসলে তখন আমি ভেবে দেখলাম – এভাবে হবে না। কারণ, এর আগে আমি যত কমিটেড লেখা লিখেছি সেগুলো কিন্তু যথারীতি গুরুত্ব দিয়েই ছাপা হয়েছিল। দীপেন নিজের হাতে ‘বিজনের রক্তমাংস’ ফেরত দিয়ে যায়। যদিও পরে এ ঘটনাটা নিয়ে দেবেশ রায় আমাকে বলেছিল, ‘তুমি কি করে ভাবলে দীপেন ওই লেখা ফেরত দিল?’ পরে আমি ভেবে দেখেছি, দেবেশই ঠিক বলেছিল। কারণ তখন তো সম্পাদক ছিলেন সত্য গুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে এমএল পার্টিতে যোগ দেন। দীপেন সত্যবাবুর বাতিল করে দেওয়া লেখাটা কেবলমাত্র আমার হাতে তুলে দিতে এসেছিল। পরবর্তীকালে ‘বিজনের রক্তমাংস’ যখন ছাপা হয় তখন দীপেন ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। ওই সময়েই তো ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’ ছাপা হল। আউট-স্ট্যান্ডিং স্টোরি! ওইরকম গল্প হয়তো আর লেখা হবে না। হয়ওনি।
‘কৃত্তিবাস’-এর সূত্রেই শক্তির সঙ্গে আলাপ এবং শক্তির সূত্র ধরেই ‘হাংরি জেনারেশনে’র সঙ্গে যোগাযোগ। হাংরির প্রতি এই আকর্ষণের কারণটা কী ছিল?
প্রথম কথা, আমি হাংরি জেনারেশনের লেখক নই। যদিও বুলেটিনে হয়তো একবার ২/৪ লাইন লিখেছি কিনা মনে নেই। তাতে হাংরি বলে কিছু ছিল না। যেমন, হাংরি জেনারেশন বলে যদি কোনো আন্দোলন হয়ে থাকে তাতে যোগদান করার কোনো ব্যাপার ছিল না। তবে মলয়রা যাদের ‘হাংরি’ লেখক বলে মনে করেছিল তাদের মধ্যে অবশ্যই আমি একজন। জীবনানন্দ দাশও একজন। সমীর আর শক্তির প্রতি আমার বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই যেটুকু। কিন্তু সব খবর রাখতামও না। একবার একটা আড্ডায় আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তাহলে কিছু মুখোশ কিনে বিভিন্ন লোককে পাঠানো যাক। ওপর থেকে নিচে সমস্ত স্তরের লোককেই। সে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ই হোক আর সাগরময় ঘোষই হোক। ঠিক হল মুখোশে লেখা থাকবে – ‘মুখোশ খুলে ফেলুন।‘ দ্যাট ওয়াজ মাই আইডিয়া। আর আমার আইডিয়া বলে সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে মুখোশগুলো কিনতে হল। এই রকম সব ঘটনা আর কি। তারপর ওরা যখন অ্যারেস্ট হল তখন আমি বিয়ে করেছি, ৬৪ সালের কথা। সত্যিকথা বলতে কি রীণারা খুবই অভিজাত পরিবারের মেয়ে। এই যেমন ধরো ওর দাদা পাঁচটা আংটি পরে। যারা উত্তর কলকাতায় থাকে। চামড়া রক্তাভ। তা যাইহোক, বিয়ে করে দমদমে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে উঠেছি, এমন সময় একদিন লালবাজার থেকে ডেকে পাঠালেন। আমার কিন্তু সাহস বলতে যা বোঝায়, তা হল ভীরুর সাহস। আমাদের দলে সাহসী বললে বলতে হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। এবং বারবার যে ওর দিকে আকর্ষিত হই তা ওই সাহসের কাছে। আর বাকি সব ভীতুর দল। তখন তো সুনীল এখানে নেই – আইওয়াতে। এদিকে এখানে এরা সব আন্দোলন করেই খালাস। লিখতে যে হবে সে ধান্দা তো নেই। লেখক বলতে যা তা ওই আমি, শক্তি আর উৎপল। আর একজনের কথা বলতে হয়, তাকে হাংরি জেনারেশনই বল আর যাই বল, সে হচ্ছে বাসুদেব দাশগুপ্ত।
সত্যিই, আজও ‘রন্ধনশালা’র গল্পগুলো পড়লে অভিভূত হই।
ওই রকম বই ওই সময় ওই একটাই। তা, বাসুদেব তো লিখলো না। আসলে লেখাটাই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব করা আর সেটাই করে যেতে হয়। যাই হোক, হাংরি জেনারেশনের একটা সংখ্যা বেরিয়ে গেল পাটনা থেকে যাতে খুবই অশ্লীল লেখাটেখা ছিল। সেই পত্রিকার প্রিন্টার অ্যাণ্ড পাবলিশার হিসাবে ছিল আমার নাম।
আপনি জানতেন না?
উইদাউট মাই নলেজ – টোটালি। সেইজন্য লালবাজারে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, এই সংখ্যাটা আমি ছাপিনি বা প্রকাশ করিনি। কিন্তু সাক্ষী দেওয়ার সময় মলয়কে সম্পূর্ণভাবে ডিফেণ্ড করি। বলি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরকম এক্সপেরিমেন্ট হয়েই থাকে। আজ যা অশ্লীল, পরে তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। পরে কোনো একটা লেখায় বোধ হয় এই বিষয়টা স্বীকার করেছে সমীর রায়চৌধুরী। তবে সমীর শক্তির বিষয়ে যেটা বলেছে সে ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। যদি সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটে থাকে তবে তা দুঃখজনক। শক্তি যদি বলে থাকে বিষয়টা সত্যিই অশ্লীল তা হলে যা দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব খারাপ।
গিনসবার্গ প্রসংগে জানতে চাই।
হ্যাঁ, গিনসবার্গ। গিনসবার্গের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্টতা ছিল। বরেনরা টাটাতে গিনসবার্গকে যখন নিয়ে গেল, সুনীল থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমার বেশ পরিস্কার মনে আছে – হাওড়া স্টেশনে প্রত্যেককে আমায় বিদায় দিতে এল। একা আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরকম ঘটনা জীবনে বহুবার হয়েছে। যখন আনন্দবাজারে ঢুকে গেল শক্তি আর সুনীল, আমি একা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। টাটার ঘটনায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। তবুও গিনসবার্গের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় বেনারসে। যেখানে আমি, গিনসবার্গ আর পিটার অরলভস্কি ছিলাম। আর কেউ ছিল না। ওরা ওই সময় এক মাসের জন্য বেনারস, এলাহাবাদ এলাকায় ছিল। তখন রোজ দেখা হত। মণিকর্নিকার ঘটে যেতাম। একদিনের কথা তো খুব মনে আছে। জানো তো, ওরা একটু ইয়ে ছিল – মানে, হোমো সেক্সুয়াল ছিল আর কী। গিনসবার্গ তো পিটারের পরিচয়ই দিত মাই ওয়াইফ বলে। একদিন আমি গিয়ে পড়ি। তখন বোধহয় ওরা ব্যস্ত ছিল। তা গিনসবার্গ বেরিয়ে এসে সেই দরাজ অসাধারণ হাসি হেসে বলেছিল – তুমি আর আসবার সময় পেলে না। তবে ওদের সঙ্গে খুব ভাল একটা ডিনার খেয়েছিলাম মনে পড়ে। ওরা তো সেই সময় খুব গরিবের মতন দশাশ্বমেধ বোর্ডিং-এ মাত্র ত্রিশ টাকা ভাড়ায় থাকত। এটা ৬২ সালের ঘটনা। পিটার একটা বাঁধাকপি কিনে আনলো। এককেজি কড়াই শুঁটি, যার দাম ছিল তখন চারআনা। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে ফেলা হল। এর সঙ্গে অবশ্যই টমাটো আর আলুও ছিল। মাখন দিয়ে একটা ডেকচিতে বসিয়ে দিল অ্যালেন। জল বোধহয় দেওয়াই হয় নি বা, নামমাত্র। গিনসবার্গ বলেছিল ওর থেকে যে জল বেরবে তাতেই হবে। তবে মাখন বেশ অনেকটাই দেওয়া হয়েছিল। লেবু আর নুন। আহা, অপূর্ব খেতে হয়েছিল। সঙ্গে ছিল দিশি মদ। বড় অদ্ভূত ভাবে সে সব সময় কেটেছে। আসলে আমি তো বেনারসে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে, তো গিনসবার্গকে নিয়ে গেলাম আমাদের ওখানে। মা অনেক কিছু খাওয়ালেন। গিনসবার্গ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি এইরকম ঠাকুমার মতন মা পেলে কোত্থেকে?’ সকলেই জানেন গিনসবার্গের মা নাওমি তুলনায় যথেষ্ট ইয়াং ছিলেন। তাঁর পিরিয়ডের উল্লেখ গিনসবার্গের কবিতায় আছে। তুলনায় মা’র শেষ তিরিশের সন্তান আমি। এইরকম অনেক টুকরো স্মৃতি ধরা আছে। যেমন, একবার মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে গাঁজা খেয়ে ফিরছি হঠাৎ গিনসবার্গ ফুটপাতে বসে থাকা একটা লোককে দেখিয়ে বলে উঠল, ‘ওই লোকটা নিশ্চই মরে গেছে। ওর হাঁটুটা কিরকম খোলা রয়েছে দেখো। তুমি একটু হাঁটুটা ছুঁইয়ে এসো তো’। আমি সত্যি সত্যি ছুঁলাম। ঐটুকু ছোঁয়াতেই কাঁথা কম্বল সুদ্ধ লোকটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। খুবই অবাক হয়েছিলাম গিনসবার্গের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে। যাইহোক এরপর তো হিন্দু ইউনির্ভাসিটিতে ওর ওই লেখা পড়বার সময় আবার গোলমাল শুরু হল। অধ্যাপকরা ওর মায়ের পিরিয়ডের জায়গায় আপত্তি করলেন, গিনসবার্গ হঠাৎ বলে উঠল ‘দেন ফাক ইওরসেলফ’। এতে তার ওপরে সব রেগে আগুন। গিনসবার্গের কলার ধরে ঘা কতক দেয় আর কি। কিন্তু সাহেব-মারার দিন বোধহয় অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটমাট হয়। কোনমতে আমরা সে জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসি।
মিনিবুকের প্ল্যানের পেছনে কারণ কী ছিল?
হ্যাঁ, পুরোটাই আমার একেবারে নিজস্ব ভাবনা বলতে পারো। ডবল ক্রাউন ওয়ান-সিক্সটিন সাইজে ভাঁজ করে মুড়লে যা হয় সেভাবে ছাপা।  আমি ভাবলাম এর মধ্যে একটা গল্প যদি বের করা যায়। তবে এরজন্য আমাকে একটা প্রেস খুঁজতে হয়েছিল, যে প্রেসে এই ১৬টা পাতা একসঙ্গে ‘বর্জাইস’ টাইপে ছাপা যাবে। কারণ, একসঙ্গে না ছাপলে পড়তায় আসে না।
আমি ভাবলাম এর মধ্যে একটা গল্প যদি বের করা যায়। তবে এরজন্য আমাকে একটা প্রেস খুঁজতে হয়েছিল, যে প্রেসে এই ১৬টা পাতা একসঙ্গে ‘বর্জাইস’ টাইপে ছাপা যাবে। কারণ, একসঙ্গে না ছাপলে পড়তায় আসে না।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মিনি কবিতার বই ‘লাল রজনীগন্ধা’ নকশালরা পুড়িয়েছিল কেন?
কেন পুড়িয়েছিল তা আমি জানি না। তবে ওখানে সমস্ত কবিতাই হচ্ছে লাল কবিতা। তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যা আনন্দবাজারি ইমেজ তাতে ‘লাল কবিতা’ কেউ বিশ্বাস করবে না, সেইজন্যই ‘লাল রজনীগন্ধা’ নাম দিয়েছিলাম। ওদের হয়তো সেটা পছন্দ হয়নি।
এটা কি খুব যোগাযোগের মধ্যে থেকেই ঘটেছিল?
না না, ওদের কি কখনও চেনা যায়? কারা করেছিল জানি না। তবে কলেজ স্ট্রিটেই পাতিরামের স্টল থেকে কিছু কপি নিয়ে পুড়িয়েছিল।
কত ছাপা হয়েছিল ‘লাল রজনীগন্ধা’?
৫০০০। পরে ভেবে দেখলাম এভাবে তো ছবিও ছাপা যায়। তখন প্রকাশ কর্মকারের ছবি সহ শক্তির কবিতা ছেপেছিলাম। সেটা বোধহয় এগারো হাজার ছাপা হয়েছিল। বইমেলাতে প্রথম বেরয় পদ্ম ঘোষের কবিতার মিনিবুক। শ্যামবাজারের বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়েরর শাড়ির প্যাকেটে চারমিনার আর ওই মিনিবুকগুলো সাজিয়ে, গলায় চুল বাঁধার ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। লেখা শ্লোগানঃ চার্মিনার অথবা মিনিবুক। দাম ৩০ পয়সা তখন দুটোরই। এতে নিত্যপ্রিয় ঘোষ খুব আপত্তি করেছিনেল। তখনকার নিত্যপ্রিয় ঘোষ আর কি।
আপত্তিটা কী?
‘দাদার বই এভাবে আপনারা বিক্রি করছেন’। তবে আমার নিজের ধারণা শঙ্খ ঘোষের এ পর্যন্ত যত বই বেরিয়েছে তার মধ্যে সব থেকে দ্রুত বিক্রি হয়েছে মিনিবুক। দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলার মধ্যে বেরয় এবং তাও শেষ হয়ে যায়। কোনও স্টলে দিতে হয়নি।
শঙ্খবাবুর কোনো আপত্তি ছিল কি এই মিনিবুক ছাপার ব্যাপারে?
না, না। শঙ্খদা কোনো আপত্তি করেন নি। শঙ্খদার আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। সেটা হচ্ছে শঙ্খদার সেই টাই-পরা ছবি আমি প্রথম ছাপি প্রচ্ছদে।
সত্যি, এই ব্যাপারটা খুবই মজার। ছবিটা পেলেন কোথায়?
উনি তখন আইওয়া থেকে ঘুরে এসেছেন। ওখানেই বোধহয় টাই-পরা কোনো ছবি তুলেছিলেন। আর সেটাই আমি পেয়ে গিয়েছিলাম।

অনেক অজানা তথ্য পেলাম । গ ল্পে র স ম য় কে ধ ন্য বা দ ।
মতামত
আপনার মন্তব্য লিখুন
আপনার ইমেল গোপনীয় থাকবে।