শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মুখোমুখি
![]()
[ এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের অভিভাবক সমান, শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। ২০১২ সালে এটি প্রকাশিত হয় বিখ্যাত অনুবাদক ও সম্পাদক অনিন্দ্য সৌরভের নিজস্ব ‘শিল্প ও সাহিত্য’ পত্রিকায়।অনিন্দ্য সৌরভের অনুমতিক্রমেই এই মূল্যবান আলাপটি ‘গল্পের সময়’ এর পাঠকদের জন্য ফের প্রকাশ করা হল।]
 অনিন্দ্য সৌরভ: আপনার সৃষ্টি করা বেশ কিছু চরিত্র নিজের শরীরে বহন করে এক অমোচনীয় ব্যাধি। যেমন ‘পারাপার’–র ললিত। দূরারোগ্য অসুখ অনেক সময় আপনার লেখায় একটা প্রতীকী মাত্রা পেয়ে যায়। আপনি কি বলতে চান এটা আধুনিক জীবনের দান?
অনিন্দ্য সৌরভ: আপনার সৃষ্টি করা বেশ কিছু চরিত্র নিজের শরীরে বহন করে এক অমোচনীয় ব্যাধি। যেমন ‘পারাপার’–র ললিত। দূরারোগ্য অসুখ অনেক সময় আপনার লেখায় একটা প্রতীকী মাত্রা পেয়ে যায়। আপনি কি বলতে চান এটা আধুনিক জীবনের দান?
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়: এটা বোধহয় সাধারণীকরণ করা হচ্ছে। ‘পারাপার’-এ ললিতের ক্যানসার হয়েছিল, কিন্তু সর্বত্র আমি অসুখের কথা লিখি না। ‘মানব জমিন’-এ একটা চরিত্র অসুস্থ। সে রকম হয়তো আরও কোথাও কোথাও এসেছে। আমার উপন্যাসে তুমি খুব একটা অসুখ-বিসুখ পাবে না। তার কারণ অসুখ-বিসুখের কথা লিখতে আমার ভালো লাগে না। কোনও কোনও সময় হয়তো প্রয়োজন হয় কোনও একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য বা হয়তো দেখে দেখে, কারণ চারদিকে অসুখ- বিসুখের ছড়াছড়ি। সেগুলো কোনও কোনও সময় চলে আসে কিন্তু সে তো অল ইন দ্য গেম। জীবনযাপন করতে গেলে আমাদের সর্দিকাশি, হাঁচি, ক্যানসার, এইডস – এগুলো হতেই পারে। জীবনের কথা লিখতে গেলে এসব আসে। আমি একজন মৃত্যুবিরোধী মানুষ। ঠাকুর আমাকে এই দর্শনটায় দীক্ষিত করেছেন। সেই কারণে মৃত্যু দিয়ে শেষ করা বা মৃত্যু ঘটানোকে আমি অ্যাভয়েড করি। মৃত্যু কোনও সমাধান নয়। একটা উপন্যাস শেষ করার জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন হয় না। বিরহান্তক লেখা আমি কমই লিখি। একটা-দুটো তেমন লেখা আছে। যেমন ‘দূরবীন’-এ কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়েছিল, সেটা হয়েছিল তার ছেলেকে রক্ষা করার জন্য। সেটা স্যাক্রিফাইস – নট এ ডেথ। এই যে কথাগুলো আমি লিখি তার কারণ ঠাকুর। ঠাকুর বিরহান্তক লেখা পছন্দ করতেন না। তার কারণ ঠাকুর মানুষকে সব সময় জীবনে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। উইথ দ্য লাইফ, উইথ এনার্জি, উইথ প্লেজার, উইথ হ্যাপিনেস। মৃত্যু চিন্তা যদি করি তাহলে আমার জীবন থেকে ঐ হ্যাপিনেস, আনন্দটা চলে যাবে। ঠাকুর চাইতেন না একটা লেখা পড়ে মানুষ হতাশ, বিষণ্ণ হয়ে পড়ুক।
অনিন্দ্য: একধরনের পজিটিভ চিন্তা…
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ, পজিটিভ চিন্তা। ঠাকুর সবসময় বলতেন যে ডেথ ইজ এ কিউরেবল ডিজিজ। মৃত্যুকে হয়তো একদিন মানুষ জয় করবে। এখন সায়েন্টিস্টরাও বলছেন যে এই শতাব্দীর শেষ দিকে মানুষ হয়তো মৃত্যুঞ্জয়ী ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলবে। আসল কথা, মৃত্যু আমার ফিলজফি হতে পারে না। তাছাড়া আমি মৃত্যুর জয়গান গাইব কেন? একসময় মৃত্যু হয়তো আসবে, একটা যতিচিহ্ন। তবে এটাকে জয় করার জন্য আমাদের প্রয়াস থাকা দরকার। যে লোকটা বিশ্বাস করে না মৃত্যুর পর জীবন বা পুনর্জন্ম আছে, তার কোনও প্রবলেম নেই। সে বলবে, আমি শেষ হয়ে গেলাম। তার পাপ-পূণ্য কিছুই নেই। আমরা যারা বিশ্বাস করি যে দেয়ার ইজ এ লাইফ আফটার ডেথ বা দেয়ার ইজ রিবার্থ। আমাদের চিন্তা করতে হবে, যদি রিবার্থ থাকে, তাহলে রিবার্থ হয়ে লাভটা কী যদি আমি ইহজন্মের স্মৃতি পরজন্মে বহন করে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে আমার কাছে ডেথটা যে লোকটা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না তার মতোই হয়ে যাচ্ছে না কি! কেননা পুনর্জন্ম হয়ে লাভ নেই। কারণ আমি যে আগে জন্মেছিলাম তার সেই ব্যাটন আমার হাতে নেই। আমি যে দৌড়েছিলাম আগের জন্মে, এই জীবনে যে সেই আমি দৌড়চ্ছি, তার প্রমাণ আমার কাছে নেই। সুতরাং এই যে জ্ঞানের অভাব – এটাকে আমার জয় করতে হবে। এক্ষেত্রে স্মৃতিবাহী চেতনার কথা ঠাকুর বলতেন। তুমি যদি স্মৃতিবাহী চেতনার অধিকারী হতে না পারো, তাহলে তোমার পুনর্জন্ম হয়েও বা লাভ কী? তাই ইহজন্মে তোমাকে স্মৃতিবাহী চেতনার অধিকারী হতে হবে যাতে তোমার মনে হয় যে পূর্বজন্মের স্মৃতি অটুট থাকবে। এই জ্ঞান বা সম্পদের অধিকারী যদি মানুষ হতে পারে তাহলে মানুষ এক ধরনে মৃত্যুকে জয় করে। তখন সে জানে যে অনন্তকালে তার গতি, সে মৃত্যুতেই শেষ হবার নয়। সুতরাং, এই যে আমার অনস্তত্ব, এটাকে বোঝাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতার একটা শর্ত হল, নিজের অনস্তত্বকে আমায় বুঝতে হবে। আমি একটা প্রদীপ শিখার মতো, এটা বৌদ্ধরাও বিশ্বাস করে। এক প্রদীপ শিখা থেকে আরেক প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়ার কথা বলেন তাঁরা। ঠিক সেভাবেই স্মৃতিবাহী চেতনা যদি না থাকে তাহলে আমরা মৃত্যুকে জয় করতে পারব না। সুতরাং আমার লেখার মধ্যে পজিটিভ ফোর্স খুব প্রবল। আমি নিজে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি – এই তত্ত্বেই আমি মানুষকে অন্ততপক্ষে উদ্বুদ্ধ করতে চাই।
অনিন্দ্য: আপনার বৃহৎ আয়তনের উপন্যাসগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক চরিত্র এসে পড়ে। ‘মানব জমিন’-এ চরিত্র সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। আপনার কিছু ছোট উপন্যাসেও চরিত্রের মিছিল চোখে পড়ে। কয়েকটি উপন্যাসে একাধিক চরিত্র যেন সমান গুরুত্ব পেয়েছে। এর ফলেই পাঠক অনেক সময় ধন্দে পড়ে যায়, উপন্যাসটির প্রকৃত নায়ক কে?
শীর্ষেন্দু: একটা উপন্যাসে একজন নায়ক বা একজন নায়িকা থাকবে, এই পুরনো ধারণাকে আমি অনেকদিন আগেই বাতিল করে দিয়েছি। যেমন ‘পার্থিব’-এ অন্তত তিনজন নায়ক আছে। ঐ তিনজন নায়ক কেন – কারণ ঐ তিনজন সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাতে উপন্যাসটার কোনও ক্ষতি হয় নি। উপন্যাসটা তিনজনে ছড়িয়ে থেকে তিনটি কাহিনি সমান্তরাল গতিতে চলেছে। নায়িকাও দেখবে তিনজন বা চারজন। ধরতে গেলে নায়কও চারজন। কৃষ্ণকান্তের বাবাও একটা মস্ত জায়গা দখল করে আছে। সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে বলতে পারো, আমি প্রথাটি ভেঙে প্রোটাগনিস্টের সংখ্যা বাড়িয়েছি। আরেকটা কথা বলি, আমার অনেক ছোট গল্পেও দেখবে অনেক চরিত্র। আমার একটা ছোট গল্পেও হয়তো ছোট ছোট চৌদ্দ-পনেরোটা চরিত্র ঢুকে গেছে। অনেক চরিত্র নিয়ে লিখতে আমার স্ফূর্তি হয়। অনেক চরিত্র নিয়ে লেখা বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে হয়, আবার ভালোও লাগে।
অনিন্দ্য: মৃত্যু-চেতনাও আপনার অনেক চরিত্রকে ভীষণভাবে তাড়িত করে। তাদের বুকে যেন হিমশীতল মৃত্যু-উপত্যকা রয়েছে। ‘সর্বদা বাঁচিয়া থাকিয়া মৃত্যুর ধ্যান ইহজন্মে আমাকে ছাড়িবে না’ কথাটা ‘দূরবীন’-র হেমকান্তর। বিষধর সাপকে নিজের ভবিষ্যত প্রয়োজনের জন্য ঝাঁপিতে ভরে রাখে ‘নয়নশ্যামা’-র নয়ন। ‘মৃণালকান্তির আত্মচরিত’, ‘কার্যকারণ’, ‘অবহেলায়’ ইত্যাদি গল্পে মৃত্যুভাবনা লেখকেরই জীবনদর্শনের একটি সূত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেখকের অবচেতন মনে ক্রিয়াশীল মৃত্যু-ভয়ই কি এর কারণ?
শীর্ষেন্দু: আমার জীবনে মৃত্যুর বিরাট ভূমিকা আছে। মৃত্যু-চেতনা আমাকে ছেলেবেলা থেকে তাড়িত করছে। আমার বিষাদ রোগ আমার সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করেছিল। তার সঙ্গে মৃত্যু এবং অসীমের যোগ আছে। এই যে অনন্ত প্রসারিত একটা জগৎ, যার সীমা নেই, এটা আমাকে বরাবর ভীষণভাবে হতচকিত করে। আমার বুদ্ধিবিনাশ করে দেয়। আরেকটা কথা, ছেলেবেলা থেকেই একটা ক্রাইসিস অফ আইডেন্টিটি আমাকে আক্রমণ করেছে। বাল্যকাল থেকেই আমি খুব দুষ্টু ছিলাম। খেলাধুলো করতাম। খুব অ্যাক্টিভ জীবনযাপন করেছি। কিন্তু মাঝেমাঝেই এই ভূতটা এসে আমাকে চেপে ধরত। তখন আমি দৌড়ে মা’র কছে চলে যেতাম। মা ছিল আমার একমাত্র আশ্রয়। দৌড়ে মা’কে জাপটে ধরতাম – মা মা আমার মাথা কেমন করছে। তার কারণ ঐ আইডেন্টিটি ক্রাইসিস – আমি চারদিকের জগতকে চিনতে পারতাম না। কিছুক্ষণের জন্য জগতটা আমার কাছে অচেনা হয়ে যেত। কোনও কিছু চিনতে পারছি না, আমি কোথায়, আমি কে, আমি কেন এখানে! এই কিছুক্ষণ, ধরো, এক-দেড়-দু-মিনিট অসহনীয় ছিল। সেই ভয়ঙ্কর আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আমাকে পাগলের মতো করে দিত। সে কারণে মা খুব ভয় পেত। সেজন্য যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমাকে নিয়ে মা খুব চিন্তিত ছিলেন যে আমার ছেলেটার কী হবে! এই অবস্থা পরবর্তীকালে বাড়তে শুরু করে, অকেশনালি। এটা যে সব সময় হচ্ছে তা নয় – হয়তো এক বছর, দু-বছর পর। ছেলেবেলায় এক মাস দু-মাস পরপর হত। অল্প সময় হত, দু-মিনিট কি তিন মিনিটের জন্য। ওই সময়টায় একেবারে পাগলের মতো হয় যেতাম। পরবর্তীকালে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি, তখন আমার তীব্র এবং দীর্ঘ মেনালকোলিয়া দেখা দিত। সেই সময় আমার একটা বছর নষ্টও হয়েছিল। তখন অনেকে ভয় পেত যে ছেলেটা কি পাগল হয়ে যাবে। সেটা যে পাগলামি নয় – তা আমি বুঝতাম। ব্রেনের গণ্ডগোল নয়, এটা ফিলজফিক্যাল ক্রাইসিস। ভাবনাচিন্তা থেকে জাত সঙ্কট। এই আইডেন্টিটির সঙ্কট খুব স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষের কাছে আসতে পারে যে চিন্তাশীল, যে মানুষ গভীরভাবে জীবনকে দেখার চেষ্টা করে। ক্রাইসিসটা বারংবার আমার জীবনে এসেছে। এর থেকে তাড়িত হয়েই আমি ঠাকুরের কাছে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলাম। আমার জীবনের মোড় ঠাকুর ঘুরিয়ে দিয়েছেন। উনি আমাকে জীবনমুখি করে দিয়েছিলেন। আমার জীবনে ঠাকুরের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর অবদান বেশি শুধু নয়, বলতে গেলে তাঁর প্রভাবেই আমার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে আমি ঠাকুরকে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে ঠাকুর আমার জীবনে ডাইভিং ফোর্স। তিনিই আমার পথ-নির্দেশক, তিনিই আমার সব। তাঁর জীবনদর্শন আমাকে এতই প্রভাবিত করেছে যে অন্যদের চেয়ে আমার জীবনে ঠাকুরের প্রভাব বহু-বহু গুণ বেশি।
অনিন্দ্য: ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ গল্প অনেকটা কবিতাধর্মী, সেখানে প্লট একেবারে গৌণ। জানতে ইচ্ছে করছে – গল্পটা ওভাবে লিখলেন কেন?
শীর্ষেন্দু: গল্পটা আমার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণে লেখা, যে সময়টায় আমার হাত থেকে কলম খসে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। গল্পটা আমি যখন লিখতে শুরু করলাম তখন কতকগুলো ইউটোপিয় ভাবনা এল। একটা লোক অফিস থেকে বেরোবে এবং রাত্রিবেলা বাড়িতে ফিরে আসবে – এটুকু সময়ের গল্প। লোকটি রাত্রিবেলা মারা যাবে। শুধু ঐ লোকটিই এই গল্পে যা কিছু করছে। গল্পটা লিখতে লিখতে আমি মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলছিলাম। কারণ ওতে এমন অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো স্বাভাবিক নয়। ধরো একটা ওয়িং মেশিন, ওজন নেওয়ার যন্ত্র, সিনেমা হলের লবিতে রাখা ছিল – সেই যন্ত্রকে অ্যানিমেটেড করে তোলা হবে। হঠাৎ যেন একটা মানুষ পয়সা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে জেগে উঠল, তার হার্ট, রক্তস্রোত চলতে শুরু করল। তারপর সে হাতে একটা টিকিট দিচ্ছে। এই যে অ্যানিমেশন অফ এ ওয়িং মেশিন, এটা লিখতে গিয়ে আমাকে ভাষার ক্রাইসিসে পড়তে হল। … আজকাল অনেকে লেখে, যারা ভাষার চর্চা করে না, বাংলা ভাষার প্রাণটারই সন্ধান তারা জানে না – একটা গল্প লিখে ফেলল, উপন্যাস লিখে ফেলল। আরে ও হয় না। একজন লেখককে তার ভাষার প্রাণ খুঁজে বের করতে হবে। আমি লিখলাম আর লেখা হয়ে গেল! আমি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হয়ে গেলাম। এত সোজা নাকি! লিখতে গেলে তোমাকে ঐ ভাষাটাকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে, রগড়াতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখেছেন সেই ভাষায় তুমি লিখতে পারো না। কেননা ওটা তাঁর ভাষা, তাঁর স্টাইল। তোমাকে তোমার নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করতে হবে।…সেই পিরিয়ডে আমি ভাষা নিয়ে চর্চা করেছি। দিনের পর দিন বুকে বালিশ দিয়ে খেয়ে না-খেয়ে শব্দ সন্ধান করেছি যে কোন শব্দকে কোন শব্দের পাশে বসাব। বাক্য রচনা হয়তো এমনিতে সহজ। কিন্তু আবার ঠিকমতো বাক্য, যে বাক্যটা আমার ওই সিচুয়েশনটাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করবে, সেটা করতে গেলে আমাকে ঐ-ঐ শব্দকে খুঁজে বের করতে হবে। তারজন্য গোয়েন্দার মতো লেগে থাকতে হবে। সেই খুঁটে খুঁটে শব্দ সন্ধান করা। এই করতে করতে গল্পটা লিখতে গিয়ে আমার মোট দেড় বছর, পৌনে দু-বছর পার হয়ে গেল। লিখে উঠতে পারছি না। ফলে সেই পৌনে দু-বছর আমার কোনও গল্প কোথাও ছাপা হয় নি। তখন দেশ পত্রিকা থেকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে, এমনও সন্দেহ করা হচ্ছে যে আমি নিশ্চয়ই ঘোর কমিউনিস্ট হয়ে গেছি। সেই কারণে আমি আর দেশ পত্রিকায় লিখব না। আমি ওঁদের বললাম, তা নয়। আমার একটা ক্রাইসিস যাচ্ছে। দয়া করে আমায় একটু সময় দিন, আমি নিশ্চিত লেখাটা শেষ করতে পারব। তারপর পৌনে দু-বছরের মাথায় গল্পটা শেষ হল, ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’। গল্পটা প্রকাশিত হওয়ার পর যে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল, তাও তো নয়। এটা পাঠককে আকর্ষিত করার মতো গল্প নয়। এটা এমন গল্প যা মানুষকে বিষণ্ণ করে দেবে, জীবনযাপনে খানিকটা হতাশ করে ফেলবে। তখনও আমার দীক্ষা হয় নি। গল্পটা আমার লেখক জীবনের একটা মোড় ফেরার জায়গা। গল্পটা লিখতে গিয়ে আমি শব্দ, বাক্য এবং ভাষা নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করেছিলাম। এটা লিখতে আমার বোধহয় দেড়-দু’শো পাতা নষ্ট হয়েছে।
অনিন্দ্য: এই ছোট গল্পটা লিখতে গিয়ে?
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ, এটা লিখতে গিয়ে দেড়-দু’শো পাতার বেশিই জমে গিয়েছিল। পুরনো পাতা ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখেছি। এমন করতে করতে …
অনিন্দ্য: কতবার ড্রাফটিং করেছিলেন?
শীর্ষেন্দু: বহুবার! অন্ততপক্ষে সত্তর-আশিবার।
অনিন্দ্য: অতবার লিখেছেন?
শীর্ষেন্দু: ওই একটা গল্প আমাকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে। তবে গল্পটা যখন প্রকাশিত হল তখন আমি খুব প্রত্যাশা করি নি যে মানুষ খুব নেচে উঠবে। মানুষ একেবারেই নেচে ওঠেনি বা সেই অর্থে কোনও বিশাল অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া যায় নি। তবে বিমল কর গল্পটা পড়ে আমাকে বলেছিলেন যে তুমি অসাধারণ একটা গল্প লিখেছ। ঐ একজন মানুষই বলেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছুটা অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়। আমার সব লেখাই অনেক লেটে হয়তো খানিকটা অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছে, যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন কোনও অ্যাপ্রিসিয়েশন পায়নি।
অনিন্দ্য: ‘জাল’, ‘মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক’, ‘ফেরা’ ইত্যাদি উপন্যাস আর ‘তোমার উদ্দেশে’-র মতো গল্পে দেশভাগের প্রসঙ্গ সরাসরি এসেছে। আপনার কি মনে হয়, দেশভাগ তখনকার পরিস্থিতিতে অনিবার্য ছিল?
শীর্ষেন্দু: সেটা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় দেশভাগে অত্যন্ত অবিচার হয়েছে অনেক মানুষের প্রতি। দেশভাগ হওয়া উচিৎ হয় নি। আমাদের নেতৃবৃন্দ যে কাজটি করেছেন সেটি আত্মঘাতী কাজ হয়েছে। তার ফলে না পাকিস্তানের ভালো হয়েছে, না ভারতের। ফলে আমরা দেখতে পারছি, এখন যুযুধান দুটি গোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাস করছে। দুটি দেশই নানারকম সমস্যায় জর্জরিত এবং আক্রান্ত। আমরা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধের যেন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে রেখেছি। ফলে দেশভাগকে আমি কোনও মতেই সমর্থন করতে পারি না। দেশভাগের ফলে কিছু মানুষের যে কী শোচনীয় অবস্থা হল সেটা আমরা দেখতেই পারছি। … যদি দেশভাগ না হত, তাহলে আমি থাকতাম ঢাকায়। পূর্ববঙ্গের মানুষ আমি, হয়তো ঢাকাই হত আমার প্লেস অফ ওয়ার্ক। দেশভাগ হওয়ার ফলে আমি এদেশে নিক্ষিপ্ত হলাম। আমার হোমল্যাণ্ড, পিতৃপুরুষের বাসভূমি চলে গেল। সেটাও মস্ত বড় বেদনাদায়ক ব্যাপার। বিক্রমপুরের বাইনখাড়া গ্রামে আমাদের দেশ ছিল। সেটা একটা ছোট গ্রাম। সেখানে শুনেছি খালধারে আমাদের বাড়ি ছিল। খুবই সামান্য বাড়ি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা বড়লোক ছিলেন না। তাছাড়া বিক্রমপুরে অতটা চাষযোগ্য জমি ছিল না। বানভাসি এলাকা, খুব জল হত। কাজেই আমাদের দেশে লেখাপড়া করে রোজগার করার ব্যাপারটা ছিল। আমাদের পুরো পরিবার ছিল শিক্ষিত। আমার দাদুর এক ভাই চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলে পড়াতেন, ছাত্রদের প্রাইভেটও পড়াতেন। সেজন্য তাঁর খুব সুনাম ছিল। তার থেকে আমাদের বাড়ির নাম হয়ে যায় ‘পণ্ডিতবাড়ি’। আমার দাদু ওইখান থেকে চলে আসেন ময়মনসিংহ শহরে। সেখানে তিনি মোক্তারি করতেন।
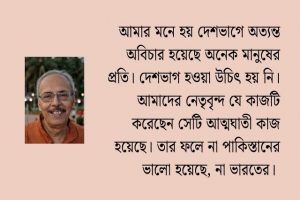
অনিন্দ্য: এটা আপনার ‘উজান’ উপন্যাসে আছে।
শীর্ষেন্দু: আছে। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার। গ্রাম-গঞ্জে আমরা ছিলাম। তা উই আর হ্যাপি ইন এ ওয়ে। দাদু একটু বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন, ময়মনসিংহ শহরে বাড়ি করেছিলেন। জমিজমা কিনেছিলেন। ময়মনসিংহ শহরটাই হয়তো আমার আস্তানা হয়ে যেত। সেই শহরের কথা আমার এখনও খুব মনে পড়ে। তার যে কি মধুর আকর্ষণ ছিল, কি অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল সেটা ভুলতে পারি না।
অনিন্দ্য: আপনি কি সেখানে আর যান নি, বড় হওয়ার পর?
শীর্ষেন্দু: একবার গিয়েছি। তবে সে আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।
অনিন্দ্য: সেটা কি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর?
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ, আমি বছর সাত-আট আগে গিয়েছি। ময়মনসিংহ শহরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার গুরুভাইয়েরা।
অনিন্দ্য: আপনার অনেক গল্প-উপন্যাসই ‘উত্তম পুরুষ’ নায়কের জবানিতে রচিত। যেমন, ‘তোমার উদ্দেশে’, ‘ঘরের পথ’, ‘খানা তল্লাশ’ ইত্যাদি।
শীর্ষেন্দু: ওটা একটা টেকনিক। অনেক সময় আমি একটা নয় অনেকগুলো উত্তম পুরুষও ব্যবহার করি।
অনিন্দ্য: ‘গয়নার বাক্স’ উপন্যাসে আছে।
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ। ‘বৃষ্টির ঘ্রাণ’ উপন্যাসেও আছে। দু’জনের জবানিতে লেখা। তিনজনের জবানিতে লেখাও আছে। আবার ছ’জনের জবানিতে একটা উপন্যাস লিখেছি কিন্তু কোথাও রিপিটেশন নেই। একজনের জবানিতে একটা চ্যাপ্টার, আবার আরেকজনের জবানিতে আরেকটা চ্যাপ্টার। উপন্যাসটার নাম ‘কোনওদিন এরকমও হয়’।
অনিন্দ্য: এই টেকনিকে কী ধরনের সুবিধা হয়?
শীর্ষেন্দু: একেক সময় এক একটা জিনিস মাথায় আসে। সব সময় এক রকম টেকনিকে আমি লিখি না। অনেক সময় থার্ড পারসনে, অনেক সময় ফার্স্ট পারসনে লিখি। আমার লেখার মধ্যে সব সময় কিছু না কিছু এক্সপেরিমেন্ট থাকে। কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমি করবই। সাদামাটা গল্প লেখার মানুষ আমি নই। আমি নানারকম প্রকরণ নিয়ে লিখি। ভাষাকে ভাঙচুর করে, নানান কায়দায়, নানান দিক থেকে একটা ঘটনাকে দেখা বা বিচার করা – সেগুলো আমার একটা প্রিয় অভ্যাস। সেটা আমি অল্প বয়স থেকে করে আসছি। এখনও করি। প্রথম গল্প থেকে শুরু করে আজও আমার এক্সপেরিমেন্টে কোনও ঘাটতি নেই।
অনিন্দ্য: ‘গয়নার বাক্স’-র নায়িকা সোমলতার বাল্যবিধবা পিসশাশুড়ি মৃত্যুর পরেও উপন্যাসে নানাভাবে উপস্থিত। মরণোত্তর জীবনেও সে নানারকম রসিকতা করে। সেই পিসশাশুড়ির নাম রসময়ী। এক্ষেত্রে পাঠকের মনে পড়ে যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রসময়ীর রসিকতা’ গল্পটির কথা। সেই চরিত্রটির কোনও প্রভাব কি আপনি এক্ষেত্রে স্বীকার করেন?
শীর্ষেন্দু: এটা স্বীকার অস্বীকারের কথা নয়। এখানে নামের মিল আছে ঠিকই। উপন্যাসে এরকম পুরনো নাম আমি খুবই ব্যবহার করি। এখানে ‘রসময়ীর রসিকতা’ গল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। যদিও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলী আমাকে একজন উপহার দিয়েছেন কিন্তু এখন আমার ‘রসময়ীর রসিকতা’ গল্পটা মনেই পড়ছে না। প্রভাব আছে কিনা সেটা যে পাঠক দুটোই পড়েছে তারা বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয় না কোনও প্রভাব আছে। এটা একেবারে অন্য ভাবনা নিয়ে লেখা।
অনিন্দ্য: নায়িকা সোমলতাকে মৃত পিসশাশুড়ি বারে বারে দেখা দেয়। তাকে গোপন তথ্য সরবরাহ করে, উপদেশ দেয়, এমন কি অন্য চরিত্রদেরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। ‘গয়নার বাক্স’ উপন্যাসে এমন অশরীরী চরিত্রের উপস্থিতি কি কাহিনির বাস্তববাদী গাম্ভীর্যকে লঘু করে দেয় নি? এটি তো কিশোরপাঠ্য ভূতের গল্প নয়।
শীর্ষেন্দু: লঘু করে দিয়েছে কিনা সেটা পাঠক বলবেন।… এই ভূত আসলে ভূত নয় – একটি চরিত্র। চরিত্রটি সারাজীবন নানারকম অনুশাসনে বাঁধা ছিলেন। নিজের কামনা-বাসনা – সবকিছুকে তাঁর বটলআপ করে রাখতে হয়েছিল। তিনি ভ্রষ্টাচার ব্যভিচার করতে গিয়েও পারেন নি- সামাজিকতার ভয়ে। সারাজীবন তাঁকে গয়নাগাটি দিয়ে ভরিয়ে রাখা হয়েছিল। সমস্ত কামনা-বাসনা ব্যর্থতার একটা প্যাকেজ যেন রসময়ী। রসময়ীর মৃত্যুকে একটা ঘটনা হিসেবে রেখে, তাঁকে আবার ফেরত এনেছি অ্যাজ ভূত। ভূত হলেও সে একটা সক্রিয় চরিত্র। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু সোমলতার। এখানে অন্য কেউ ভূত দেখছে না – তার কারণ এটা ভূতের গল্প নয়। শুধু সোমলতা কেন! কারণ সোমলতার মধ্যে কিছু কোয়ালিটি আছে। সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী আর দৃঢ় চরিত্র। যেরকম স্বামীর একটু ব্যভিচার দেখলে স্ত্রীরা অত্যন্ত আপসেট হয়ে পড়েন, নানারকম অশান্তি করেন, সংসার ভেঙে দেন। সোমলতা সেরকম নয়। সে স্বামীকে ডেকে বলেছে যে আপনার যদি সেরকম কেউ থেকে থাকে তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই কিন্তু আমাকে না জানিয়ে নয়। আমি যেন জানতে পারি। এটাই যথেষ্ট ছিল তার স্বামীকে শাসন করার জন্য। এতে স্বামী লজ্জিত-কুন্ঠিত হয়ে পড়ল, সংযত হল। এইভাবে সে নানা কাজ করেছে – দোকান করেছে। দোকানটার যে সাকসেস, লোককে না ঠকিয়ে, লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কীভাবে ব্যবসা করতে হয় সেটা যেন সোমলতা দেখিয়ে দিয়েছে।
অনিন্দ্য: সে সামান্য এক গৃহবধূ …
শীর্ষেন্দু: সেটা কোনও কথা নয়। এই গুণগুলো তার মধ্যে নিহিত ছিল বলেই সে প্রকৃতির সাহায্যটাও পাচ্ছে। সেই প্রকৃতি এই ভূত। ভূতটা প্রথম দিকে তাকে ডিস্টার্ব করত, তার মাংসে দু’বার নুন দিয়েছে, তাকে নানাভাবে ভয় দেখাত। পরে সেই ভূতটাই তাকে গয়না দিয়েছে, শেষে দেখা গেল সেই ভূতই তার মেয়ে হয়ে জন্মেছে। এইভাবে আমি একটা চরিত্র তৈরি করেছি। এখন এটা পাঠক কীভাবে নেবে! দায় আমার লেখা পর্যন্ত। পাঠকের ভালো লাগলে ভালো, না লাগলে কিছু বলার নেই।
অনিন্দ্য: ‘মুনিয়ার চারদিক’ গল্পে দেখি মেয়ের মৃত্যুর পর বামপন্থী নেতা মার্কসের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ‘শ্যাওলা’, ‘ফেরা’, ‘বৃষ্টির ঘ্রাণ’ ইত্যাদি উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের প্রতি আপনার বিরূপতা ফুটে উঠেছে। আপনি কি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অনাস্থা পোষণ করেন?
শীর্ষেন্দু: বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা আকর্ষণ কোনওটাই আমার নেই। তবে স্বীকার করতে হবে যে নকশাল আন্দোলন ভ্রান্ত পথে চলে গিয়েছিল। উই ওয়ার দ্য ওয়ার্সট সাফারারস অফ নকশাল মুভমেন্ট। তার কারণ আমার চোখের সামনে পুলিশ খুন দেখেছি। আমি যে স্কুলে চাকরি করতাম সেই স্কুলে দু-তিনবার আগুন লাগানো হয়েছে, বোমা ফেলা হয়েছে। আমার ছাত্রগুলো খুনি হয়ে গেল। তারা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে খুন করত। খুনের প্রয়োজন নেই। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন পান খাচ্ছিল – আমারই এক ছাত্র, ক্লাস এইটে পড়ত, সে গিয়ে দিনে দুপুরে খুন করে দিয়ে এল। এসব দেখার পর পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এর পিছনে বিপ্লবের প্রতি যে একটা ইচ্ছা, তার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল আমাদের। তারপর যখন ভ্রান্ত পথে ধাবিত হল নকশাল আন্দোলন, তখন আর তাকে সমর্থন করতে পারলাম না। এখনও যে নকশাল আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চলছে, তার কি ভালো দিক নেই? আছে। কিন্তু খারাপ দিকটা এত বেশি যে, একটু ভালোর জন্য অতটা খারাপ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একটু ভালো আছে, যেমন ধরো বিহারের গাঁয়েগঞ্জে যে ধরনের অবিচার রণবীর সেনারা করে বা ভূমিহার জমিদার জোতদাররা যে ধরনের অত্যাচার মানুষের ওপর করে, সেখানে নকশালদের উপস্থিতি তাদের অনেকটাই সংযত রাখে। সে ধরনের ছোটখাটো ভালো নিশ্চয়ই আছে। তবে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ভালো না। তারা এত বেশি খুনখারাপি করে, শ্রেণিশত্রু বলে একজনকে দেগে দিলেই তো হল না। যাকে তাকে মেরে দিচ্ছে। তাহলে আমার বেঁচে থাকার অধিকার তুমি হরণ করছ। কাজেই এই আন্দোলনকে আমি কী করে সমর্থন করব! মানুষের একে সমর্থন করার কথা নয়।
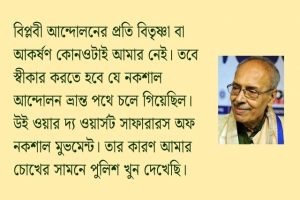
অনিন্দ্য: আর মার্কসবাদ সম্পর্কে?
শীর্ষেন্দু: মার্কসবাদ একটা সময় নিশ্চিত খুব প্রাসঙ্গিক ছিল এবং তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এখনকার পৃথিবীতে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। এখন সোস্যালিস্ট দেশগুলো ধীরে ধীরে তার থেকে সরে আসছে। চিন সরে আসছে, রাশিয়া তো ভেঙেই গেল। পূর্ব ইউরোপ সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে বর্জন করল। যে দেশগুলো এখনও আছে তাদের ভালোই সিফটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। চিনে গেলে এখন একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে মনেই হবে না। শাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য সেখানে শক্ত হাতে দমন করার ব্যাপার আছে। অন্যদিকে তারা উন্নতিও খুব করেছে। যেভাবে উন্নতি করেছে সেখানে বলতে পারি পুরোপুরি পুঁজিবাদ সমর্থিত ইকোনমিতেই তারা চলে গেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সুতরাং মার্কসবাদ এখন আস্তে আস্তে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। বামপন্থী আন্দোলনটাই আলটিমেটলি পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। কিছু পুরনো মানুষ, যাঁরা এরজন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা হয়তো এটা মানবেন না। আসল কথা, বামপন্থী আন্দোলন অলরেডি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এখনকার পৃথিবীতে এটা খাটছে না।
অনিন্দ্য: ‘দূরত্ব’ গল্পটা ভালো, তবে একটা খটকা আছে। নায়িকা অঞ্জলি যখন অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা, তখন তার বাবা তথ্য গোপন করে মন্দারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন, যাতে মেয়ের হবু সন্তান একটা পিতৃ পরিচয় পায়। সম্বন্ধ করে বিয়ে, এতে তাই নিশ্চয়ই পনেরো দিন থেকে এক মাস সময় লেগেছে। আমার প্রশ্ন, এক দেড় মাসের অবৈধ গর্ভের সমস্যা কি গর্ভপাত করিয়ে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যেত না? তাহলে কেন পাত্রকে প্রতারণা করে বিয়ে, কেনই বা অনিবার্য বিবাহ-বিচ্ছেদ?
শীর্ষেন্দু: সমাধানের নয়, এটা সমস্যার গল্প। দ্বিতীয় কথা, এর একটা সমাধান শেষ দিকে আছে। যে বাস্তব প্রয়োজনের কথা তুমি বলছ, গর্ভপাত করলে হত, তাহলে গল্পটা লেখা হত না। গল্পটা লেখার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। এই শর্তেই বিয়ে হয়েছে, সে অন্যের সন্তান পেটে নিয়েই বিয়ে করেছে। এরকম ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। অনেক সময় স্বামী জেনেশুনে গ্রহণ করে, অনেক সময় না জেনে করে। এটা চালিয়ে দেওয়া যাবে বলে ভেবেছিল তার বাবা। বাবা সরল অন্ত:করণের লোক, খারাপ নন। তিনি মেয়েকে রক্ষা করার জন্য আর মেয়েও রক্ষা পাবার জন্য এটা করেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যারজন্য সে গর্ভবতী হয়েছিল, সে তার প্রেমিক ছিল না, তাকে সে ভালবাসত না। তবে ঘটনাক্রমে হয়ে গিয়েছিল। সে ব্যাখ্যা করেনি কার সঙ্গে, কী পরিস্থিতিতে হয়েছিল। ফলে এগুলো তুমি জানতে চেয়ো না – যে লোকটি তার প্রেমিক কিনা! স্বামী-স্ত্রী দু’জনের যে শেষের দিকের ডায়ালগ, তারা শুয়ে আছে। তখন স্বামীকে সে বলেছে, তোমাকে আমার কিছু বলার ছিল, সেটা কী – আমার মনে পড়ছে না। যতদিন না মনে পড়ে ততদিন আমার কাছে তোমাকে বারে বারে আসতে হবে। এইখানেই গল্প, আর গল্পের অন্যদিকগুলো তোমার …
অনিন্দ্য: ইররেলেভেন্ট!
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ, ইররেলেভেন্ট।
অনিন্দ্য: আমার মনে হয়েছে সমস্যার সহজেই সমাধান করা যেত।
শীর্ষেন্দু: সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে গল্পটা লেখার দরকার হত না।
অনিন্দ্য: আপনার সিরিয়াস গল্প-উপন্যাসে শিক্ষিত, আধুনিকা নারীদের ভূমিকা অনেক সময় প্রশংসনীয় নয়। তারা সামান্য কারণে সংসার ছেড়ে চলে যায় নইলে সংসারকে অসহনীয় করে তোলে। যেমন ‘জীবনপাত্র’ উপন্যাসে অলকা, ‘ঋণ’ উপন্যাসে মিতালি, ‘চক্র’ উপন্যাসে সোনা। ‘ঋণ’-এ ক্ষণিকা নামে এক স্বঘোষিত নারীবাদী আসলে স্বার্থপর আর ঈর্ষাকাতর। সে নিজে যে স্বাধীনতা দাবি করে অন্যদের তা দেয় না। নিজের মেয়ের সম্বন্ধেও সে উদাসীন। – এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন?
শীর্ষেন্দু: এগুলো সব বাস্তব চরিত্র থেকে এসেছে। কোনওটাই আমার কল্পিত নয় বা এটা কাউকে মিনিমাইজ করার জন্য বা কাউকে অপমান করার জন্য লেখা নয়। এগুলো আমরা অনবরত চোখের সামনে দেখতে পারছি। নারী প্রগতির নামে কিছু মানুষ আছেন যারা লেখালেখি করেন বা অন্যান্য কাজে যুক্ত, তাঁরা অনেক সময় মানুষের ক্ষতি করে দেন। আমাকে একদিন একজন বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী গৃহবধূ, মোটামুটি সংসারেই আবদ্ধ। সেইখানে গিয়ে কিছু শিক্ষিত নারীবাদী তাকে টিজ করে, নানাভাবে তাকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে যে তোমার স্বামী তোমাকে দিয়ে খাটাচ্ছে। তোমাকে দিয়ে এটা-ওটা করাচ্ছে। এইভাবে ষড়যন্ত্রের মতো করে তার ভেতরে অল্প-অল্প করে বিষ ঢুকিয়েছে। হয় কি জানো, একটা সময় কোনও নারীর মনে হতে পারে যে আমি বঞ্চিত, আমি দাসি, আমি নির্যাতিত। তা তো নয়। সংসারটা যেন একটা বাড়ি-ইমারত তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে একটা কুলি আছে একটা কামিনও আছে। কুলি আর কামিন দু’জনে মিলে সেটা করছে। কুলি হয়তো ইঁট বয়ে আনছে, কামিন হয়তো মশলা তৈরি করছে কিংবা সে হয়তো রাজমিস্ত্রি, তার বউ তাকে মেটিরিয়াল যোগান দিয়ে যাচ্ছে। দু’জনে মিলে একটা নির্মাণ করছে। মানুষ ভুলে যায় যে আমরা দু’জনে মিলে একটা নির্মাণ করছি যার নাম সংসার। এই নির্মাণটা তার সন্তান-সন্ততি, পোষ্য, অতিথি-অভ্যাগত, শ্বশুর-শাশুড়ি, মা-বাবা – সবাইকে নিয়ে। ঘরের লোক, কাজের লোক, পোষ্য কুকুর-বেড়াল-আসবাবপত্র যা কিছু আছে – সব কিছু মিলে একটা সংসার। সংসারে দু’জনকেই খাটতে পিটতে হবে। কেউ যদি মনে করে যে আমি খাটছি, ও বসে আছে – তাহলেই মুশকিল। খাটতে দু’জনকেই হবে। না খাটলে সংসার তৈরি হবে কী করে! সেখানে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কোনও কোনও সুখকে বর্জন করতে হয়। সব মিলিয়ে এই নির্মাণ একটা মস্ত বড় জিনিস। ধরো খুব শিক্ষিত নারী যারা তারা নিজেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা করতে হলে তাকে ঘরে কাজের মেয়ে রাখতে হবে। তা সেই মেয়েটিরও জীবন কাজে নিবেদিত হয়ে গেল। কাজটা কাউকে করতেই হবে। তারজন্য কাজের মেয়েটি কিছু পয়সা পাচ্ছে। … এই যে ব্যাপার, এখানে একটা অসত্য, ভ্রান্তি আছে। ঘরে কেন আটকে থাকব! ঘরে আটকে থাকতে তোমাকে কেউ বলছে না কিন্তু ঘরটাকে তো রক্ষা করতে হবে। ঘরটা যদি ভেসে যায় তাহলে তোমার সংসার থাকল না। সংসার জীবনের আর কোনও শৃঙ্খলা থাকবে না। আগে বিবাহ প্রথা ছিল না। এই প্রথা চালু হল কেন? যখন মানুষ দেখল যে এই উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গগামী মিলন এবং তার ফলে যে সন্তান সন্ততি হচ্ছে – তাদের কারও কোনও পিতৃ পরিচয় নেই। কে কার বোঝা যাচ্ছে না। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে। দলগতভাবে না বাঁচলে আমাদের শক্তি হীন হয়ে যাবে। একটি মেয়ের সঙ্গে সব পুরুষের বিবাহ চলবে না, সুতরাং একজনকে বেছে নিতে হবে তোমায়। এইভাবে হয়তো একজন-দু’জন স্ত্রী নিয়ে একজন, তখন বহুবিবাহ খানিকটা ছিল। একজন শিকারে সাহায্য করবে, অন্য একজন ঘর সামলাবে, একজন সন্তান ধারণ করবে। বিভাজন ছিল বলে একাধিক বিয়ে ছিল। একটি পুরুষ দুটো-তিনটে বিয়ে করত। নারীর সংখ্যা ছিল বেশি, সেটা মিনিমাইজ করতে হবে। সব কিছুর পেছনে একটা প্রয়োজন কাজ করে। বিবাহ একটা প্রয়োজন, সংসার একটা প্রয়োজন। এগুলো প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল, না হলে হয়তো হত না। না হলে মানুষ আজকে মুক্ত জীবনযাপন করত। রাস্তাঘাটে যাকে তোমার পছন্দ হত তার সঙ্গে তুমি কিছুক্ষণ সময় কাটালে – তোমার কাজ শেষ হয়ে গেল। তা তো হচ্ছে না। তাতে জেনেটিক সিস্টেম, সন্তান-সন্ততি গণ্ডগোল হয়ে যাবে। বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্যই এই ঘর-সংসার – শৃঙ্খলা – সমস্তকিছু।
অনিন্দ্য: ‘পার্থিব’ উপন্যাসে অনেক উত্থান-পতনের পর নিমাই-বীণাপাণিতে এমন মধুর পুনর্মিলন বাস্তবে কি সম্ভব? কিছু অবাস্তবতার আভাস প্রৌঢ় কৃষ্ণজীবন আর তরুণী অনুর বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যেও রয়েছে। এ সমস্ত দিক কি উপন্যাসটির বাস্তবতার ভিতকে দুর্বল করে নি?
শীর্ষেন্দু: আমার উপন্যাসে সব সময় কঠোর বাস্তবতা খুঁজে পাবে না। কারণ আমি সেই অর্থে মেটিরিয়াল জগতের উপন্যাস লিখি না। যা ঘটছে তাই লেখা আমার ধর্ম নয়। আমি তাকে রিপোর্টাজ বলে মনে করি। যা ঘটছে তা আমি লিখতে যাব কেন! সে যারা লিখছেন তাঁদের আমি বাহবা দিই – তাঁরা ভালোই কাজ করছেন। বাট ইট ইজ নট মাই ফিলজফি। আমি সে সমস্ত চরিত্রের ভিতরে কিছু সঞ্চার করতে চাই। ধরো তুমি প্রথমে যে পয়েন্টটা বললে, বাস্তবতার অভাব তোমার মনে হয়েছে …
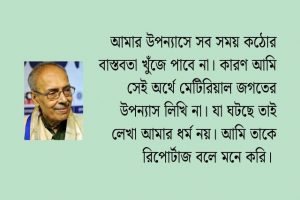
অনিন্দ্য: নিমাই-বীণাপাণি।
শীর্ষেন্দু: এক্ষেত্রে তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। বাস্তবে ওভাবে মিলন সম্ভব নয়। আবার একেবারেই যে হচ্ছে না – এমনও নয়। তুমি দেখবে যে এরকম মিলও হচ্ছে। কেন না মেয়েটা স্বামীকে ছাড়ল, ছেড়ে সে পড়ে গেল কতকগুলো স্মাগলারের পাল্লায়। সে দেখল সে একা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। তারপর এই অল্প সময়ের মধ্যেই আরেকটি ছেলে তাকে ভালবেসে ফেলল। তবে তাকে সে বিশ্বাস করতে পারল না। ছেলেটির বয়স কম। সে আজ তাকে নিয়ে যাচ্ছে তারসঙ্গে ঘর করবে বলে। আর পরশুই যে সে আরেকজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে যাবে না – এমনও বলা যায় না। যাকে আমরা মুরোদ বলি – ছেলেটির তাও নেই। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে, নিমাই অত্যন্ত সৎ মানুষ। বীণাপাণি যদিও এতদিন তার স্বামীর মূল্য বুঝতে পারে নি, কেননা স্বামী তার ওপর নির্ভরশীল ছিল, কাজ করত না। বীণাপাণিই তার সংসার চালিয়ে দিত। সে যাত্রায় কাজ করে সংসার চালাত, সেটাও ভালো জিনিস নয়। অনেক পুরুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাতে স্যানটিটি নষ্ট হয়। তাতে সে খানিকটা নিজেকে নষ্ট করে ফেলেছিল। সে ক্ষেত্রে দুজনের সম্পর্কটা বিয়োগান্তক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে আমি সেটা হতে দিইনি। কেন না আমি চাই ডিভোর্স না ঘটুক। স্বামী-স্ত্রী সারাজীবন একসঙ্গে কাটাক। খুব ভুল ভ্রান্তির বিয়ে যদি না হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে থাকাই ভালো। আজকালকার যুগে কি হচ্ছে, পাঁচ বছর প্রেম করল, তারপর বিয়ে হল, পাঁচ মাস সেই বিয়ে টিকল না। এই প্রেমকে বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং কতকগুলো ব্যাপারে প্রেমের থেকেও প্রয়োজনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন এমন জায়গায় চলে যায় তখন তাকে প্রেমের থেকেও বেশি মূল্য দিতে হয়। বীণাপাণির জীবনে সেটাই দেখা দিয়েছিল।
অনিন্দ্য: ‘পার্থিব’ উপন্যাসে কৃষ্ণজীবনের পল্লীপ্রেমকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তার গ্রামের টান কতটা কর্মমুখী, কতটাই বা অলস মনের বেদনা বিলাস – বোঝা মুশকিল। পেছুটান ছাড়া গ্রামজীবনের সঙ্গে কৃষ্ণজীবনের আজ সত্যিকারের যোগ কতটুকু?
শীর্ষেন্দু: যোগটা তার ছেলেবেলায় ছিল যখন সে চাষও করেছে নিজের হাতে। ছেলেবেলায় যোগ ছিল বলেই টানটা রয়ে গেছে। যেমন দেশের মাটির প্রতি আমাদের টান কেন! এটা আবেগ ছাড়া কিছু নয়। তোমাকে আমার পূর্ববঙ্গের কথা বললাম একটু আগে – কেন বললাম? তার কারণ আবেগটা আমার ভিতরে কাজ করে। ও যে চাষবাস করেছিল, জমিকে ভালবেসেছিল, মাটির গভীরে লাঙল চালিয়েছিল, একসময় বাবার পাশাপাশি নিজেও চাষ করত। পরবর্তীকালে সে বিদেশে গিয়ে মস্ত সায়েন্টিস্ট হয়। এরপরেও সে নিজের অতীত জীবনটা ভোলে নি। বিশেষ করে বিষ্ণুপদ’র মৃত্যুর পর বাবার প্রতি তার কর্তব্যবোধ এবং টান। সেই কারণে বউয়ের সঙ্গেও তার সম্পর্কটা দানা বেঁধে ওঠে নি। তার বাবা-মা’র প্রতি, মাটির প্রতি টান বউ সহ্য করতে পারছে না। ফলে তাদের মধ্যে একটা খটাখটি চলেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য তাকে গ্রহণ করেছে। অনুর প্রতি যে আকর্ষণ, এটা পুরুষের হবেই। অনু অল্পবয়সী একটি মেয়ে। সে পুরুষ মানুষ বয়সে তার থেকে অনেক বড়, তার বান্ধবীর বাবা। সে অনুর প্রতি আকৃষ্ট। তবে সেটা লঘু ধরনের আকর্ষণ – সিরিয়াস নয়। এমন নয় যে সে সংসার ভেঙে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল। এমন ঘটনা প্রচুর ঘটে। আমার পরিচিতদের মধ্যেও ঘটেছে। মেয়ের বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে করে তারসঙ্গে ঘর-সংসার করছে। এখানে আমি সেটা ঘটতে দিইনি। কৃষ্ণজীবন সংযত পুরুষ, থাকতে পারে তার একটা আকর্ষণ, তাই বলে সব ভেঙে দিয়ে চলে যাবে সেরকম পুরুষ সে নয়। সেটাই দেখিয়েছি।
অনিন্দ্য: পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, গ্রামের চিত্র আপনার সাহিত্যে যতটা জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য, শহরের ছবি তেমন নয়। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণের সাহিত্যেও এমন ঘটেছে। ‘পার্থিব’ ইত্যাদি উপন্যাসে শহরের কাহিনি বা উপকাহিনিগুলি কিছুটা দুর্বল, চরিত্রগুলোও যেন আবছা। ‘পার্থিব’-র অন্যতম চরিত্র হেমাঙ্গ অনেকটা ছায়া-ছায়া। অন্যান্য চরিত্রও একমাত্রার মানুষ। অন্যদিকে গ্রামের মানুষগুলো বেশ সজীব। যেমন কৃষ্ণজীবনের বাবা বিষ্ণুপদ আর মা নয়নতারা। এর কারণ আপনি ভেবে দেখেছেন কি?
শীর্ষেন্দু: এখানে তোমার দেখার বা বোঝার একটা ভুল হচ্ছে। সেটার কারণ তুমি দেখবে যে শহরের মানুষ নিজেদের অনেক কিছু গোপন করে রাখে। তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে না। গ্রামের মানুষের সেই প্রবলেমটা নেই। গ্রামের মানুষ, যেমন বিষ্ণুপদ, স্ত্রীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, সেটা খোলামেলা, গভীর ভালবাসা এবং নির্ভরতা তাদের সম্পর্কটার মধ্যে রয়েছে। খুব সামান্য তাদের প্রবলেম, অর্থকরী প্রবলেম খানিকটা আছে আর বুড়ো বয়সে খাবার লোভ হয়েছে, বউ তাকে গভীরভাবে শাসন করেছে। বিষ্ণুপদ আর তার স্ত্রীর সম্পর্ক আসলে সনাতন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আর শহুরে মানুষ যাদের দেখানো হয়েছে, বেশিরভাগই কমবয়সি। সেখানে বেশি বৃদ্ধ মানুষ কেউ নেই। আর এই যে জীবন কলকাতার, এইসব চরিত্র নিয়ে শহর। কাজেই শহরের একটা ধারা, গ্রামের আরেকটা ধারা। দুটোকে মুড়ি-মুড়কির মতো এক করে ফেলা যাবে না। সুতরাং দুটোকে সম্পুর্ণ কম্পার্টমেন্টালাইজ করতে হয়েছে। এতে আবছা কিছু নেই। যেমন তোমার ঐ যে কী যেন নাম?
অনিন্দ্য: হেমাঙ্গ।
শীর্ষেন্দু: হেমাঙ্গর জীবনে আবছা কিছু নেই। তার ভিতরে যতরকমের ইচ্ছা, গ্যারেজ-প্রীতি ইত্যাদি, খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার ভিতরে আছে, সেটাই আমি তার ভিতরে সঞ্চার করে দিয়েছি। এই চরিত্রগুলো আমার দেখা, আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত। এই কলকাতা এবং আরও কতকগুলো শহর আমার এত প্রিয় যে সেই শহরের বৃত্তান্ত যখন লিখি তখন আমি সেই শহরের মধ্যে ঢুকে যাই। কলকাতা শহরকে পঞ্চাশ বছরের ওপর দেখছি। শহরের প্রতিটি রাস্তাঘাট, সবকিছুর সঙ্গে আমার গভীর যোগাযোগ। হেঁটে-হেঁটে কলকাতা শহরকে আমি চিনেছি। কাজেই কলকাতা শহর আমার কাছে কোনও আবছা ব্যাপার নয়।
অনিন্দ্য: ঠিক তা নয়। শহরের পটভূমিতে যে চরিত্রগুলো –
শীর্ষেন্দু: চরিত্রগুলো ঠিকই আছে বলে আমার ধারণা।
অনিন্দ্য: অশুভ বা ইভিল আপনার সাহিত্যে খুব সহজে দেখা যায় না। যেমন ‘পার্থিব’ উপন্যাসের অজস্র চরিত্র, তবে খাঁটি ভিলেন কেউ নেই। যে খারাপ, উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে তার খারাপত্ব ফিকে হয়ে যায়। – এর কারণ যদি বলেন?
শীর্ষেন্দু: অশুভ চরিত্র তুমি চাইছ কেন?
অনিন্দ্য: তেমন মানুষ অনেক আছে সমাজে।
শীর্ষেন্দু: আছে। খুনে,গুণ্ডা, বদমাশ আছে। আমার লেখাতেও তেমন চরিত্র অজস্র আছে। কিন্তু আলটিমেটলি এই চরিত্রগুলির মধ্যে আমি হিউম্যান কোয়ালিটিজকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। আমার সঙ্গে সেই অর্থে খুনি গুণ্ডা – এইধরনের মানুষের পরিচয় ছিল। তাদের আমি খুব নিবিড়ভাবে দেখার চেষ্টা করেছি। তাদের কাজকর্ম নিয়েও তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তখন দেখেছি যে তারা কতকগুলো সিচুয়েশনের শিকার। একটা লোক যে খুনি বা নারী পাচারকারি হয়ে যাচ্ছে – সেও কিন্তু পরিস্থিতির শিকার। সেও সমাজে ছোরা হাতে ঢোকে নি। সে হয়তো খুব ভালো ছেলে ছিল। সেরকম একটি ছেলেকে চিনতাম – খুব কুখ্যাত গুণ্ডা। তাকে বাল্যকাল থেকে চিনত একটি লোক, সে আমাকে বলেছিল, একে যে দেখছেন আপনার সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে, সে অত্যন্ত সুন্দর ছেলে ছিল। সহজ-সরল ছবি আঁকত, গান গাইত, ভাবালু ধরনের ছেলে ছিল। বড় হয়ে শুনি সে একটা বড় গুণ্ডা হয়ে গেছে। আমি সেই গুণ্ডাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা কী করে হল? সে আমাকে বলল, শীর্ষেন্দুবাবু, কী আর বলব, আমার জীবনে অনেক ঘটনা। পরিস্থিতিই তাকে বাধ্য করেছে এমন হতে। হয়তো পেটের দায়ে অনেকে ড্রাগ চালান করে, চোলাই চালান করে, খুন-খারাপি করে। পরিস্থিতিটাই এমন আমাদের দেশে যে কিছু মানুষ খারাপ হয়ে যায়। তা বলে আদ্যন্তই হয়তো তারা খারাপ ছিল না। সেটিই আমি খুঁজে খুঁজে দেখার চেষ্টা করি। সবাইকে একেবারে ব্র্যাণ্ডেড করে দেব খারাপ বলে, এটা কেন!
অনিন্দ্য: ‘পার্থিব’-র নায়ক কৃষ্ণজীবন পরিবেশ দূষণ নিয়ে খুব চিন্তিত। নিউক্লিয়ার প্লান্ট, ডিজেল ইঞ্জিন, কম্প্রেসার, রাসায়নিক ধোঁয়াশা, ক্ষতিকারক গ্যাস – সবকিছুর বিরুদ্ধে তিনি। সারা বিশ্বে প্রগতির নামে বিপুল যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ। শিল্পায়ন ( ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন) থেকে তিনি সমাজকে মুক্ত করতে চান। এখানে আমার প্রশ্ন, ইন্ডাস্ট্রি আজকের যুগের পক্ষে অনিবার্য। সেটাকে বাদ দিলে দূষণ কমবে ঠিকই, তাতে সভ্যতাও কি পিছিয়ে পড়বে না?
শীর্ষেন্দু: মনে রেখো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে ভোগ্যপণ্য। যে পণ্যগুলোর আমাদের তেমন প্রয়োজন নেই। সেই পণ্য অজস্র তৈরি হচ্ছে। ফলে দেখবে যে দূষণ তুমি বাড়াচ্ছ – তারফলে একসময়ে তোমার শ্বাসবায়ুতে টান পড়বে। তোমাকে তিনটে কাজ করতে হবে। প্রথম কথা, জনসংখ্যা হ্রাস করতে হবে। অরণ্য অঞ্চল বাড়াতে হবে, যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড মিনিমাইজ করা যায়। আর তৃতীয় কথা, অপ্রয়োজনীয় শিল্পগুলোকে রোধ করতে হবে। আমি জানি, আধুনিক সভ্যতাকে বজায় রাখতে হলে সবরকম জিনিস দরকার। এতো আর ছেলেমানুষি কথা নয়। তুমি যদি জনসংখ্যা কমাও, দেখবে প্রয়োজনগুলো আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে। এগুলোর যে হিউজ ডিমান্ড তৈরি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ পিসেস তৈরি হচ্ছে, সেটা কমিয়ে আনা যায়। সেই কমিয়ে আনতে হলে জনসংখ্যা কমাতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা, তোমাকে উপায় বের করতে হবে যাতে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমিশানকে যদি অন্য কোনও ভাবে রূপান্তরিত করা যায় – ইন কার্বন বা সলিড কার্বন – মানে আমি চাইছি ধোঁয়াটা আকাশে বাতাসে না মিশে এটাকে যদি কোনও চেম্বারে ঢুকিয়ে সলিডিফায়েড করা যায় বা এটাকে যদি অন্য কোনও ভাবে ইউজ করা যায়। তৃতীয় কথা হচ্ছে, সাইকেল বেশি চলুক, রিক্সা বেশি চলুক। মোটরবাইক, গাড়ি নয়। গাড়ি এমনিতেই বেশিদিন চালাতে পারবে না কারণ পেট্রোল-ডিজেল থাকবে না। তুমি আজ যতই লাফালাফি করো, ফুয়েল না থাকলে ইন্ডাস্ট্রি চলবে কী করে! বিকল্প ফুয়েল এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, চেষ্টা হচ্ছে এই পর্যন্ত। বিকল্প ফুয়েল না থাকলে এমনিতেই ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে। তেল, কয়লা থাকবে না। বিকল্প যদি আবিষ্কার করতে না পারো, তাহলে একসময় তোমাকে সেই আরণ্যক জীবনই যাপন করতে হবে। আগে থেকে সংযত হলে সেই আরণ্যক জীবনযাপন বিলম্বিত হতে পারে। সেটাই কৃষ্ণজীবন বলেছে। সে আরও বলেছে যে কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে মহাকাশ বিজ্ঞানের পেছনে, ওটা কমাও। মকাহাশ বিজ্ঞান খানিকটা দরকার, তবে এতটা দরকার নয় যে ইথিওপিয়া মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন দেশ ধুঁকছে অস্তিত্বের সঙ্কটে, সেই দেশগুলোর উপকার না করে তুমি মহাকাশের পিছনে অত টাকা খরচ করছ। আগে পৃথিবীকে বাঁচাও তারপর মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করবে। তুমি যে ডালে বসে আছো সেটাই যদি কেটে ফেলো তাহলে তোমার মহাকাশ দিয়ে কী হবে! মহাকাশ তোমাকে রক্ষা করবে না। বিজ্ঞানী হকিংস বলছেন মানুষ অন্য গ্রহে গিয়ে বসবাস করবে। আগে এই গ্রহকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিৎ। অন্যগ্রহে বসবাস করবার মতো কোনও পরিস্থিতি নেই। সেখানে বসবাস করতে গেলে যে বিপুল সম্ভার পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হবে, তাতেই তুমি ফতুর হয়ে যাবে। সেখানে চাষবাস হবে না, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না। আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে এত জীব-অনুকূল পরিবেশ নেই। যেখানে জীবন-অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে গেলে বিপুল খরচ, সেখানে আরেকটা পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞানীরা হাস্যকর কথা বলছেন। এসব কথা শুনলে আমার মনে হয়, এত বড় বড় বিজ্ঞানী হয়ে এমন কথা কী করে বলছেন! মানুষ নাকি গ্রহান্তরে বসবাস করবে! পাগল ছাড়া এসব কথা কেউ বলে!
অনিন্দ্য: গল্প-উপন্যাসের বর্ণনায় আপনি অনেকক্ষেত্রেই উপমার ব্যবহার করেছেন – অন্য ধরনের উপমা। যেমন, ‘ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে’ (ওষুধ); ‘গাড়ির পেট একেবারে দশ মেসে হয়ে যাক’ (খগেনবাবু); ‘ডেড – এই কথাটা আবার হঠাৎ ভারি পাথরের মতো গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়’ (মুনিয়ার চারদিক); ‘গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে’ (ঘরের পথ)। এমন উপমা কি স্বত:স্ফূর্তভাবে কলমের সামনে চলে আসে, নাকি ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে লেখেন?
শীর্ষেন্দু: অত সহজ নয় ভাই। এসব নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সেজন্যই বলছিলাম যে লেখা এত সহজ নয়। লেখাটা অনেকে সহজ মনে করে বটে – আমি লিখলাম আর আমার রিকগনিশন হয়ে গেল – অত সোজা নয়। লেখার জন্য কী পরিশ্রম একটা মানুষকে করতে হয় সে যে করেছে সেই জানে।
অনিন্দ্য: কিশোর সাহিত্যে আপনার সাফল্য কম নয়। আমি স্কুলজীবনে ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’ পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। জানতে ইচ্ছে করছে, ছোটদের লেখায় কীভাবে এলেন?
শীর্ষেন্দু: আমি বড়দের লেখা লিখতাম, ছোটদের লেখা কখনও লিখব বলে ভাবিই নি। অনেকদিন আগে শক্তি, আনন্দবাজারে যে এক পাতার আনন্দমেলা বেরোয়, তারজন্য একটা গল্প লিখিয়েছিল আমাকে দিয়ে।
অনিন্দ্য: আপনি কি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন?
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ, তখন ও-ই পেজটা সম্পাদনা করত। আমাকে লিখতে বলল, আমি বোধহয় ‘চোর’ নামে একটা গল্প লিখেছিলাম। ছোট্ট একটা গল্প – খুব একটা কিছু হয় নি। তারপর ১৯৭৫-৭৬ বোধহয় হবে, সেই সময় নীরেনদা একদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি যাদবপুরে থাকি। উনি আনন্দমেলার সম্পাদক ছিলেন, এসে বললেন, ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখে দিতে হবে। ওঁকে বললাম, আমি কি পারব! ছোটদের জন্য আমি লিখিনি কিছু। তখন উনি বললেন, ‘চেষ্টা করে দেখ, পারবি। লেখ না একটা’। তখন লিখেছিলাম, ‘বিধূ দারোগা’। সেটা নীরেনদার খুব পছন্দ হল। উনি বললেন, ‘তুই পেরেছিস। আরেকটা লেখ’। তখন বোধহয় লিখলাম ‘গন্ধটা খুব সন্দেহজনক’। সেটা পাঠকের খুব পছন্দ হল। তারপর উনি আমাকে বললেন, ‘এবার একটা উপন্যাস লেখ’। তখন আমি বললাম, ‘পারব না, এটা সম্ভব না’। নীরেনদা বললেন, ‘বারো সংখ্যায় একটা উপন্যাস শেষ করে দিবি’। প্রায় জোর জবরদস্তি করে উনি আমাকে দিয়ে লেখালেন। সেই ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বেশ…
অনিন্দ্য: অ্যাপ্রিসিয়েশন?
শীর্ষেন্দু: হ্যাঁ, বেশ একটা আলোচনা হতে লাগল। পরের পুজো সংখ্যায়, ‘গোঁসাইবাগানের ভূত’। সেই যে শুরু হল, সেই থেকে আজ অবধি প্রত্যেক বছর আনন্দমেলা পুজো সংখ্যায় আমাকে একটা করে উপন্যাস লিখতে হচ্ছে – টানা লিখে আসছি তা প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর হয়ে গেল। মাঝখানে চার-পাঁচটা ধারাবাহিকও লিখতে হয়েছে ‘গোলমাল’ আর ‘হারানো কাকাতুয়া’ – এইসব।
অনিন্দ্য: কিশোর সাহিত্যে আপনি সাধুদের নিয়ে বেশ হাসি-ঠাট্টা করেন, অনেকক্ষেত্রে সাধুদের ভণ্ড হিসেবে চিত্রিত করেন। একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে সাধুদের এমনভাবে চিত্রিত করার কারণ আমার কাছে ঠিক বোধগম্য হয় নি।
শীর্ষেন্দু: সে কি! বোধগম্য হওয়া তো খুব সহজ। ধর্ম করি বলে আমি ভণ্ড সাধুদের মেনে নেব, এটা ঠিক নয়। ভণ্ড যে সে ভণ্ড আর যে খাঁটি সাধু সে খাঁটি। ভণ্ড আর খাঁটির মধ্যে যদি আমি বিভাজন না করতে পারি, তাহলে আমি ধার্মিক কিসের! আমি জানি কে ধার্মিক আর কে ভণ্ড। ভণ্ডামি পৃথিবীতে ভালোই আছে। ধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী জিনিস। সুতরাং এই জিনিসটাকে ভাঙিয়ে কিছু ভেজাল মাল তো ঢুকবেই। তারা এটা থেকে রুজি রোজগার করবে। ভণ্ড জ্যোতিষ, ভণ্ড সাধু থাকবেই। আমাদের দেশে সাধুদের কেউ ফেরায় না। বাড়িতে সাধু এলে লোকে ভিক্ষে দেয়। তীর্থক্ষেত্রে গেলে লোকে সাধুদের খাবার দেয়, ভাণ্ডারা দেয়, পূণ্য করে। সাধুদের খুব খাতির আছে আমাদের দেশে। সাধুরা কেউ না খেয়ে মরে না। সেজন্য অনেক গরিব-গুর্বো সাধু হয়ে যায়। ছেলেকে সাধু করে দেয়। সাধুদের ভিক্ষা, অন্নজল মেলে সেই হিমালয়ের প্রত্যন্ত জায়গায়, হৃষিকেশ, হরিদ্বার যেখানেই যাক। ভালো জায়গায় গেলে আরও ভালো। আশ্রম-আখড়ায় যুক্ত হতে পারলে তো কথাই নেই। সুতরাং ভণ্ড সাধু আর খাঁটি সাধু – দু’রকমই আছে। অনেকে দেখবে, ভণ্ড সাধু নয়, তারা সাজা সাধু। ইচ্ছে করেই সাধু সেজেছে, ছদ্মবেশি সাধু। আমি হাসি-মজা নিয়ে লিখি, কাজেই আমার ভণ্ড সাধুদের প্রয়োজন হয়। চরিত্রগুলোকে আমি নিজের সুবিধামতো সিলেক্ট করে নিই।
অনিন্দ্য: আপনার সায়েন্স ফিকশনগুলি আসলে ফ্যান্টাসিধর্মী রচনা, যেমন ’পাতালঘর’, ‘গোলমাল’ আর ‘বড় সাহেব’ বইয়ের বিভিন্ন ছোট গল্প। বিজ্ঞানের দিকটা সেখানে গৌণ। অন্যদিকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক ও আইজ্যাক অ্যাসিমভের লেখার ক্ষেত্রে সবসময় তা ঘটে না। বিজ্ঞানের বেস তেমন পোক্ত নয় বলেই কি আপনার ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে, নাকি হালকা চালে মজার গল্প লিখতে চান বলেই?
শীর্ষেন্দু: আর্থার সি. ক্লার্ক, অ্যাসিমভ – এই সমস্ত লেখকের লেখা আমি অনেক পড়েছি। অ্যাসিমভের একটা ফিউচারিস্টিক লেখা পড়েছিলাম। মজা হচ্ছে, উনি যা লিখেছেন, আজ থেকে ধরো পাঁচশো বছর পরের মানুষ। দেখা যাচ্ছে সেখানে মানুষের আচার-আচরণের কোনও পরিবর্তন হয় নি। শুধু কিছু জিনিস পালটে গেছে। হয়তো কেউ গাড়ি চড়ছে না, রকেটে করে এখান থেকে সেখানে যাচ্ছে। সেখানে নতুন নতুন যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। তবে কালের সঙ্গে সঙ্গে, বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও যে পালটে যাবে, তাদের চরিত্র পালটে যাবে, রিলেশন পালটে যাবে – সে দূরদৃষ্টি তাঁদের নেই। তাঁরা সেই সেন্টিমেন্টাল প্রেমের গল্প লিখেছেন যা আজ থেকে তিনশো বছর পরে ঘটবে না। তুমি যে ওগুলোকে সায়েন্স ফিকশন বলছ, শুধু যন্ত্রপাতির কথা বলছে বলে?
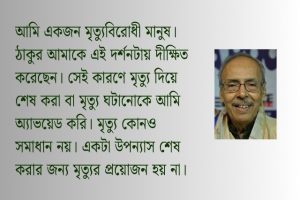
অনিন্দ্য: সায়েন্সের ব্যাপার বেশি আছে।
শীর্ষেন্দু: সায়েন্সের ব্যাপার বেশি জানার জন্য তুমি সায়েন্সের বই পড়ো। ফিকশন পড়বে কেন? এমন ফিকশন পড়তে হবে যার সঙ্গে জীবনের যোগ আছে। ফিকশন মানে সায়েন্স নয়। ওখানে এমন সব সায়েন্সের কথা বলা হয়েছে যা ইউটোপিয়া। যেগুলো সম্ভব নয় সেগুলো ওখানে লেখা আছে। সেগুলোকে সায়েন্স বলব কী করে! একটা ছোট ঘটনা বলি, পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র, ‘আলফা সেনটরি’। তার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ফোর লাইট ইয়ারস অর্থাৎ এখান থেকে যদি আলোর গতিতে কোনও রকেট ছাড়া যায় তাহলে সেটা সেখানে পৌঁছবে চার বছর পর। বাস্তবে আলোর গতিতে রকেট ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ আলোর গতিপ্রাপ্ত হলে যে কোনও জিনিস এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাবে। তাহলে তুমি কোন ফুয়েল দিয়ে রকেট ছাড়বে? আলোর গতি তুমি কী করে অ্যাটেন করবে! আলোর গতিতে গিয়েও নিয়ারেস্ট নক্ষত্রে পৌঁছবে চার বছর পর। তাহলে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে যে গল্পগুলো লেখা হচ্ছে সেগুলো বাজে কথা। সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, কখনই সম্ভব নয়। এই হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন। আমি যা লিখেছি আর্থার সি. ক্লার্ক, অ্যাসিমভও তাই লিখেছেন। তারচেয়ে বেশি কিছু লেখেন নি। ওঁরা আমার চেয়ে সায়েন্স নিশ্চয়ই ভালো জানেন কিন্তু যা লিখেছেন সেটা সায়েন্সের কথা নয়। এখনকার সায়েন্স দেখে আমরা অনুমান করতে পারছি এ জিনিস অ্যাটেন করা সম্ভব নয়। যদিও মানুষের ডিকসনারিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই বলা হয় তবে সেটা ঠিক নয়। অনেককিছুই অসম্ভব। টাইম অ্যান্ড স্পেসকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে চিরপ্রসারণশীল বিশ্বব্রহ্মান্ড – এর ঠিকানা পাওয়াই মানুষের পক্ষে অসম্ভব।
অনিন্দ্য: আপনার কিশোর সাহিত্যে সচরাচর কলকাতার পটভুমি থাকে না, মফস্বলের পটভূমিতেই আপনি লেখেন। এর কারণ কি জানাবেন?
শীর্ষেন্দু: আমি যে ধরনের গল্প-উপন্যাস লিখি তাতে মফস্বলে সুবিধা হয়। যে ভূত বা আজব ধরনের চরিত্র নিয়ে আসি – সেগুলো শহরে নেই। সেই পরিবেশটাও থাকে না। ধরো, বাঘ বা অন্য জন্তু কিংবা প্রকৃতি – এগুলো বাচ্চাদের লেখার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন। শহর নিয়ে লেখা যায় না এমন নয়। শহরেও এরকম উপাদান আছে, কিন্তু সেই পরিমণ্ডলে গিয়ে আমার গল্পের যে চরিত্র তা খানিকটা মার খায়। রসহানি হয়। সেজন্য আমি শহর অ্যাভয়েড করি, গ্রামে কিংবা উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাই।
অনিন্দ্য: আপনার গল্পের ভূতগুলো বেশ মজার – অনেকক্ষেত্রে সুপার হিরোর আদলে রচিত। কিশোর পাঠক স্বভাবতই তাদের ভয় পায় না। সেখানে গা-ছমছমে ভয়ের পরিবেশও থাকে না। ‘গোঁসাইবাগানের ভূত’ উপন্যাসের নিধিরাম তেমনই একটি চরিত্র। এমন ‘বন্ধু ভূতের’ আইডিয়া আপনার মাথায় কীভাবে এসেছিল?
শীর্ষেন্দু: আইডিয়া কীভাবে এল – বলা মুশকিল। ভূতকে বন্ধু আমি প্রথম থেকেই করে আসছি, সেই ‘গন্ধটা খুব সন্দেহজনক’ থেকেই। আমার সবগুলো উপন্যাস ভূতের নয়, অনেক উপন্যাস আছে ভূত ছাড়া। ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’তে ভূত নেই। তবে আমার অর্ধেকেরও বেশি উপন্যাসে ভূত আছে। আসলে কী লিখব না লিখব, তা আমি প্ল্যান করে লিখি না। যা মাথায় আসে আমি লিখে যাই। তারপর যা হবার হয়।
অনিন্দ্য: বন্ধু ভূত ব্যাপারটা কি আপনার নিজস্ব?
শীর্ষেন্দু: বাচ্চাদের লেখা, ভয় পাওয়ানো ভূতের থাকার কোনও মানেই হয় না। তুমি যে বললে সুপার হিরো, আমার ভূতগুলো তাই। হয়তো অতটা সুপার হিরো নয়, তাহলেও তারা হিরোর কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। তবে হিরোরা যেমন সিরিয়াস হয়, এরা তা নয়। এরা নানারকম মজা করে, তাতে অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। আমার উদ্দেশ্য মজা করা।
অনিন্দ্য: জে. কে. রাউলিঙের হ্যারি পটার সিরিজের লেখা নিশ্চয়ই কিছু পড়েছেন। পড়ে কেমন লেগেছে?
শীর্ষেন্দু: একটা উপন্যাস আমি পড়েছি তাও পুরোটা পড়তে পারি নি। রাউলিঙের লেখা আমার খারাপ লাগে না। যদিও আমাদের অনেক বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল রাউলিঙকে ভালো নয় বলে মনে করেন। তবে আমার মতে, রাউলিঙ নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব জগত তৈরি করতে পেরেছেন। আরেকটা জিনিস রাউলিঙের ভালো লাগে যে সমস্ত পৃথিবীর ছেলেগুলোকে আবার বইমুখি করেছেন। বইয়ের জন্য লোকে লাইন দিচ্ছে, এটা আমার ভালো লেগেছে। বইমুখিতা কমে যাচ্ছে। অন্তত সেদিক থেকে খুবই ভালো।
Tags: অনিন্দ্য সৌরভ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মুখোমুখি, সাক্ষাৎকার

মতামত
আপনার মন্তব্য লিখুন
আপনার ইমেল গোপনীয় থাকবে।