সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মুখোমুখি
লিখেছেন:সাক্ষাৎকারঃ অনিন্দ্য সৌরভ


[বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। বিখ্যাত অনুবাদক ও সম্পাদক অনিন্দ্য সৌরভের অনুমতিক্রমেই এই মূল্যবান আলাপটি ‘গল্পের সময়’ এর পাঠকদের জন্য ফের প্রকাশ করা হল।]
অনিন্দ্য: সাহিত্য সৃষ্টিতে কীভাবে এলেন? বাড়িতে কি লেখালেখির অনুকূল পরিবেশ ছিল?
সিরাজ: জ্ঞান হবার পর থেকেই বাড়িতে প্রচুর বই-পত্র দেখেছি। এরই মধ্যে বেড়ে উঠলে যা হয়, ইচড়েপাকা হয়ে গিয়েছিলাম। পাঠশালায় অক্ষর জ্ঞান হবার পর থেকেই আমার বই পড়া শুরু। আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল। বাবার সংগ্রহে নানা পত্রিকা বই ছিল। সেগুলো ছোটবেলা থেকেই পড়তাম। মা আনোয়ারা বেগম তখনকার দিনে মেয়েদের মোক্তবে ক্লাস ফোর অবধি পড়েছিলেন। বাবার সঙ্গে বিয়ে হবার পর তাঁর আরও বেশি পড়াশোনা করার আগ্রহ জন্মে, এই করতে করতে উনি নিজেও লিখতেন। কলকাতার পত্রিকায় ওঁর লেখা প্রকাশিত হত। ওঁর লেখা দেখে আমিও অনুপ্রাণিত হতাম।
অনিন্দ্য: মা লিখতেন?
সিরাজ: হ্যাঁ। বাবা সৈয়দ আবদুর রহমান ফিরদৌসি রাজনীতি করতেন। উনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কৃষক সভার নেতা ছিলেন। মুজফফর আহমেদ থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় নেতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এভাবে একদিকে রাজনৈতিক পরিবেশ আবার ঠাকুর্দা পার্সিয়ান-আরবিক বইপত্র পড়তেন, সেদিক থেকে ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ডও ছিল। অন্যদিকে হিন্দু বন্ধুবান্ধব, স্কুলের ছাত্রবন্ধু – আমার মনটা এইসব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে। এর বাইরে নিজস্ব একটা মন ছিল আমার, যাকে এখনকার ভাষায় বলা যায়, খুব প্রকৃতি অভিমুখী মন। খোলামাঠ, গাছপালা, নদী – উত্তর রাঢ় অঞ্চল, সেখানকার রাখাল, খেত-মজুর, জেলে-মাঝি – এই ধরনের পরিবেশেও খুব ছোটবেলায় আমি বই ফেলে চলে গেছি। বিলের জলে সাঁতার কেটেছি ওদের সঙ্গে। প্রকৃতির টান আমার মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই ছিল, যার ফলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। এতে একাডেমিক পড়াশুনোয় অনেক বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, অপরিচিত জায়গার লোকের সঙ্গে মিশবার আমার খুব আগ্রহ ছিল। অনেক সময় বাবা এসে খুব কঠোরভাবে শাসন করতেন। এমনকী, এমনও হয়েছে, তখন সিক্স কি সেভেনে পড়ি, স্কুলের মাইনের পয়সা নিয়ে আমাদের ওখান থেকে কর্ণসুবর্ণ স্টেশন (তখন নাম ছিল চিরুটি) চার মাইল, কী খেয়ালে বইগুলো বাড়িতে রেখে সেই স্টেশন থেকে কাটোয়া গেলাম, কাটোয়া থেকে ছোট লাইনের স্টেশন বড়গোলা। সেখান থেকে বাসে করে মঙ্গলকোট। এই মঙ্গলকোট অজয় এবং কুনুর নদীর ধারে। কুনুর খুব সুন্দর, ছোট্ট নদী। নদীর ধারে ঘাসে ভরা খুব সুন্দর উপত্যকা ছিল।
অনিন্দ্য: ওটা কি বীরভূম জেলায়?
সিরাজ: না, বর্ধমান। ছ’আনা পয়সা নিয়ে ওখানে হাজির হলাম, পিসিমার বাড়ি। স্কুলের মাইনে নিয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে। ওখানকার প্রকৃতি আমায় টানত। কুনুরের কালো জল, ওদিকে অজয়ের গাঢ় ঘোলাটে জল – দুটো জলের একটা সূক্ষ্ম রেখা, একেবারে মিশে যাচ্ছে না। দুটোর রঙ সম্পূর্ণ আলাদা – পাশাপাশি আলাদা আলাদাভাবে চলছে। এটা দেখতাম। কখনো নদী পেরিয়ে চলে যেতাম কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছে। প্রথম দিন তাঁকে দেখেছিলাম, একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে, গলায় তুলসীমালা, খালি গা, ফর্সা রঙ, বেঁটে মানুষ।
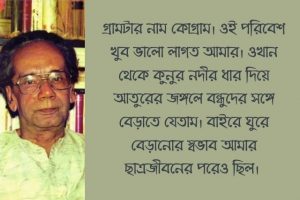
অনিন্দ্য: উনি কোথায় থাকতেন?
সিরাজ: গ্রামটার নাম কোগ্রাম। ওই পরিবেশ খুব ভালো লাগত আমার। ওখান থেকে কুনুর নদীর ধার দিয়ে আতুরের জঙ্গলে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। বাইরে ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব আমার ছাত্রজীবনের পরেও ছিল। আরেকটা পালানোর কথা বলি – যা আরও সাংঘাতিক। কলেজ থেকে পালিয়ে চলে গেলাম মেদিনীপুরের এক বন্ধুর সঙ্গে। তার বাড়ি ছিল পানিপারুলে। সে বলেছিল, আমাদের ওখান থেকে দীঘা যাওয়া যায়। ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পানিপারুল থেকে সোজা দক্ষিণে গিয়ে রামনগর। রামনগর অবধি তখন বাস যেত। হাঁটতে হাঁটতে ওখান থেকে বারো মাইল হবে, আমরা সন্ধ্যার মুখে দীঘায় পৌঁছলাম। তখন দীঘায় একটা রাজবাড়ি আর জেলেদের একটা বাড়ি ছাড়া কিছু ছিল না। বিশাল জমি জুড়ে ছিল বালিয়াড়ি আর কেয়াবন। ঐ বালিয়াড়ির ওপর দৌড়ে গিয়ে আমি প্রথম সমুদ্র দেখি। বিশাল সমুদ্র দেখার যে অনুভূতি … হাঁ করে তেড়ে আসছে ভয়াল সব ঢেউ। মনে আলোড়ন তুলেছিল প্রকৃতির শক্তি। ছোটবড় নানা জিনিসের মধ্যে প্রকৃতির শক্তির অনুভূতি – ছোটবেলাকার এই স্মৃতিগুলো আমাকে পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যেমন আমাদের গ্রামের দক্ষিণের দ্বারকা নদী, আরও দক্ষিণে নাবাল প্রান্তর, সেখানকার হিজল বিল। তারাশঙ্করের ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ এই হিজল বিলের পটভূমিতে রচিত। দ্বারকা নদীতে বন্যা আসত। একবার বন্যার সময় দাঁড়িয়ে আছি। বনগোলাপের ফুল, তার গায়ে প্রজাপতি উড়ছে, আস্তে আস্তে হ্রদটা ডুবে গেল বন্যায়, বোকা প্রজাপতিগুলো তখনো উড়ছে। এটা এক অদ্ভুত দৃশ্য। সব ডুবে গেল, তবু তারা ওখানে উড়ছে। ছোটবেলায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি।
অনিন্দ্য: আপনার ব্যক্তি-জীবনে কোন কোন মানুষের গভীর প্রভাব আছে?
সিরাজ: বাবার প্রভাব আছে। বেশি প্রভাব বোধহয় আছে আমার ঠাকুর্দার। উনি মৌলানা হলেও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ওয়াহাবি ছিলেন, ‘আংরেজ শাহি বারবাদ যাক’ বলে বেড়াতেন। বাবা আরবি পড়া ছেড়ে দিয়ে বেলডাঙা হাইস্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরে নন-কো-অপারেশন করতে গিয়ে জেলে যান। সেখান থেকে কমিউনিস্ট হয়ে বেরিয়ে আসেন। অনেকবার জেলে গিয়েছেন। মেদিনীপুর-মুর্শিদাবাদে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রতিবাদী চেতনার মানুষ বাবা কোথাও অন্যায় দেখতে পারতেন না। বাবাকে দেখেছি কম সময়, কারণ উনি বাইরেই থাকতেন। উনি চাইতেন, আমি যেন খুব নিয়মনিষ্ঠভাবে লেখাপড়া শিখি। আমাদের সৈয়দ পদবিধারীরা দাবি করেন যে তাঁরা হজরত মহম্মদের নাতির বংশধর। এদের জীবিকা যজমানী বামুনের মতো।
অনিন্দ্য: বাবা সেই লাইন থেকে…
সিরাজ: সেই লাইন থেকে সরে আসেন। ‘অলীক মানুষ’-এ যে মৌলানার চরিত্র এঁকেছি …
অনিন্দ্য: বদিউজ্জামান?
সিরাজ: খানিকটা আমার ঠাকুর্দার চরিত্র। উনি যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়…
অনিন্দ্য: যাযাবরের মতো?
সিরাজ: হ্যাঁ। কিছুদিন একদল শিষ্যের কাছে থাকলেন, তারপর… । আমাদের খোসবাসপুর গ্রামে আসার পর আর কোথাও যেতে পারেন নি, বাবা যেতে দেন নি। ঠাকুর্দা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি যে গান করতাম সেগুলো নিষিদ্ধ ওয়াহাবি সংস্কৃতিতে, উনি কিন্তু সেগুলো অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন, মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যদের শোনাতেন। মুসলিম মাইথোলজি আমি জেনেছিলাম ঠাকুর্দার কাছ থেকে। অন্যপক্ষে আমি প্রথমে পড়তাম গ্রামের পণ্ডিতের পাঠশালায় – সেটা ঠিক অপুর পাঠশালার মতো। পরে বাবা পাশের গ্রাম গোকর্ণে অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করালেন। ওখানে গিয়ে একটা লাভ হয়েছিল, প্রতিদিন বিকেল চারটার সময় ছুটির আগে উনি ছাত্রদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলতেন। এইভাবে তিন-চারটে বছর না-পড়েও পুরো রামায়ণ মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। মুসলিম ছেলে খুব কম ছিল সেখানে, হিন্দু-প্রধান গ্রাম। গল্প শোনার পর আমরা সবাই তীর-ধনুক-তলোয়ার নিয়ে রাম-রাবণ, মহাভারতের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতাম। পরে হিন্দু আর মুসলিম মাইথোলজি দুটোই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার এইসব স্মৃতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন হয়তো স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। বাড়ির পূর্বদিকে বাগান। তার পেছন দিক ধাপে ধাপে নেমে গেছে বিলের দিকে, সেখানে ভগবান মাঝি নামে গ্রামের এক চেনা লোক সে যাচ্ছে নদীর ধারে জাল নিয়ে। রাতে মাছ ধরবে। দৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গ ধরলাম, সে খুব মজার লোক, নানা ধরনের অদ্ভুত গল্প বলত – ‘রাত্রিবেলায় কি হয় জানো, বিলের ধারে দেখি, ঝাঁকে ঝাঁকে পরি নেমে এসেছে স্নান করতে’। একদিন আমি সত্যি সত্যি দেখেছিলাম নেমে আসছে একটা চাবুকের রেখার মতো। আমার অদ্ভুত লাগছে যে কী ওগুলো! ওগুলো আসলে বুনো হাঁস, জল হাঁস। তখনকার দিনে কেউ মারত না। সেগুলো দেখেই ও বলতো, ‘এই দেখো, শব্দ শোনো, পরীর ঝাঁক নামছে’। পরবর্তীকালে মনে হত, প্রকৃতির নাভিমূলে কোথাও একটা আলোড়ন হচ্ছে – সেটা আমি শুনেছি। আর একদিন আমি নদীর ধারে হিজলের বনে গিয়েছি, সেখানে দেখি, হিজলের ডালে শুয়ে আছে একজন খাকি হাফ প্যান্ট পরা লোক, টুপিতে চোখ আড়াল করা, পাশে বন্দুক। পরে বুঝেছি, লোকটি ছিল শিকারি। লোকটিকে তখন আমার অদ্ভুত মনে হয়েছিল, যেন প্রকৃতির অঙ্গ। এইসব স্মৃতি আমার গল্পে এসেছে।

অনিন্দ্য: ‘হিজলকন্যা’তে কিছুটা, ‘তৃণভূমি’তে বিস্তৃতভাবে এসেছে।
সিরাজ: অনেক জায়গায় এসেছে। এ ধরনের নানা স্মৃতির ভিতর দিয়ে আমার ছোটবেলা কেটেছে। … আর ঐ কবিতা, অন্যদের মতো আমাকেও কবিতা লিখতে হবে।
অনিন্দ্য: কবিতা ছেড়ে আপনি গদ্যে এলেন তারপর আর কবিতায় ফিরে গেলেন না। এর কারণ কী?
সিরাজ: আমার শেষ কবিতা বেরিয়েছে ১৯৫০ সালে, “শেষ অভিসার”। পরে অবশ্য আরও কিছু কবিতা লিখেছিলাম।
অনিন্দ্য: ছাপতে দেননি?
সিরাজ: ’৫০ সালে সদ্য বি.এ. পাশ করেছি। আসলে কবিতার জগৎ ছেড়ে এমন এক পরিবেশে …
অনিন্দ্য: আর সে পথে যাননি ?
সিরাজ: না। তবে তখনো গদ্য লেখার চেষ্টা করিনি। ছাত্র ফেডারেশন করতাম, মুর্শিদাবাদ জেলার আই পি টি এ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।
অনিন্দ্য: আপনি কি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
সিরাজ: হ্যাঁ। বাবা রাজনীতিতে ছিলেন, আমিও ছোটবেলা থেকেই… ।
অনিন্দ্য: রাজনীতির সঙ্গে আপনি কীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন?
সিরাজ: যুক্ত হয়েছিলাম হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকে। আসলে ১৯৪২-৪৩ এ ক্লাস নাইনে ওঠার পর আমার স্কুল পালানো আরম্ভ হয়ে গেল। কোথায় কোথায় চলে যাই, কোনও পাত্তা নেই, দু-দিন, তিন দিন। তখন বাবা আমাকে নিয়ে যান বর্ধমানের নবগ্রাম স্টেশনের কাছে ময়না নামে এক ছোট্ট গ্রামে, সেখানে ছিলেন আমাদের আত্মীয় মীর সাহেব, তার দুই ছেলে – বড় সৈয়দ জামাল আহমেদ, ছোট সৈয়দ জমিল আহমেদ। ওখানে আমায় রাখলেন। ওদেরও একটা লাইব্রেরি ছিল। সেখান থেকে অন্তত দু মাইল দূরে গোপালপুর মুক্তকেশী উচ্চবিদ্যালয়ে বাবা ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দিলেন। আমি কবিতা লিখি শুনে সেখানকার মাস্টারমশাইরা খুবই আনন্দিত। সংস্কৃতে একমাত্র মুসলমান ছাত্র ছিলাম আমি। অন্যদের মৌলবি সাহেব পড়াতেন, সেজন্য উনি আমাকে দেখতে পারতেন না। সংস্কৃত পড়তাম বলে অন্য শিক্ষকরা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।
অনিন্দ্য: এরপর?
সিরাজ: ১৯৫০-এ পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পার্টির অনেকে গা-ঢাকা দিলেন, জেলে গেলেন। ঐ সময় আমরা আই পি টি এ–র শিল্পীরা নানাধরনের ফর্ম খুঁজে গানটান করতাম। আমি লোকনাট্য আলকাপের দলে ঢুকে পড়লাম। ভালো বাঁশি বাজাতে পারতাম, গান গাইতে পারতাম। আলকাপের দলে প্রায় ছ’বছর, ’৫৬ সাল পর্যন্ত ছিলাম। বিশাল অঞ্চল জুড়ে তখন আলকাপ হত। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, পুরুলিয়া, বনগাঁ অঞ্চল – এইসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে আলকাপ করতাম। এই নিয়ে আমি ‘মায়ামৃদঙ্গ’ নামে উপন্যাস লিখেছি। আলকাপ লোকনাট্য নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছি।
অনিন্দ্য: লেখাটা আপনার ‘মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য’ বইতে আছে।
সিরাজ: ওতে আছে। তখন আমি বইয়ের জগৎ থেকে একেবারে বাইরে। নিজেরই ভাবতে অবাক লাগে, তখন সার্ত্রের দর্শন নিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা পত্রিকায় ‘অস্তিত্ববোদ্ধার মতবাদ’ নামে প্রবন্ধ বেরিয়েছে আমার, সেই ’৫০ সালেই। নিয়মিত কলকাতায় আসতাম। আই পি টি এ-র সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। একদিকে আমার ঐ ইচড়েপাকা জ্ঞান, মার্কসবাদ ইত্যাদি আর অন্যদিকে ছ’বছর ধরে ঐরকম একটা জীবন, অতবড় এলাকা ঘুরে বেড়ানো, যত্রতত্র খাওয়া এবং রাতজাগা। মাঝে মধ্যে অবসর পাওয়া যেত, তখন আরেকটা দলে গিয়ে তালিম দিতাম। তখন আমি দলের একজন হলেও কোথাও একটা পার্থক্য ছিল। ওরা আমাকে একটু অন্যভাবে দেখত।
অনিন্দ্য: আপনি তখন গ্রাজুয়েট।
সিরাজ: হ্যাঁ, আলকাপের দলে একজন বি.এ. পাশ এসেছে – দেখে আসি, এই হুজুগ ছিল। ওই সুযোগে আমি চাষিদের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে নাটক করেছি। এমনকী মার্চেন্ট অব ভেনিস-কে ভেঙে আলকাপের ফর্মে বহরমপুর শহরে পারফর্ম করেছিলাম। ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’ যে ওইভাবে হবে – কেউ কল্পনা করতে পারেনি। ঋণের জন্য চাষির বুকের মাংস কেটে নেওয়া হবে…

অনিন্দ্য: স্থানীয় পরিবেশে নাটকটাকে ঢেলে নিয়েছিলেন।
সিরাজ: হ্যাঁ। আলকাপের দলে আমার মতো অত লেখাপড়া শিখে যারা যায় নি, তারা যতখানি স্বচ্ছন্দ, আমি ততখানি স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। কিন্তু আমার ওই নিচের স্তরের জীবন আরও বিস্তৃতভাবে জানা হয়ে গেল। এদেশের চাষি কী চায়, চাষির সঙ্গে জমির সম্পর্ক কী, কীভাবে তাদের জীবন চলে- এগুলো নিবিড়ভাবে জানতে পেরেছিলাম।
অনিন্দ্য: মানে গ্রাসরুট লেভেল…
সিরাজ: গ্রাসরুট লেভেল আমি ভালোভাবে জানতে পেরেছিলাম। ’৫৬ সালে আলকাপে আস্তে আস্তে ভাঙন ধরছে। তখন কলকাতা থেকে যাত্রা যাচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা চলছে। গ্রামের পরিবেশ, মানুষজন বদলে যাচ্ছে। যার ফলে আলকাপ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বুঝলাম শেষ অবধি কিছুই করা যাবে না, এইসবের একটা সীমা আছে।
অনিন্দ্য: চাকরির চেষ্টা করেননি?
সিরাজ: চাকরির চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। কারণ পিছনে রাজনৈতিক ছাপ। প্রাইমারি স্কুল-টিচারের ইন্টারভিউ দিয়েও আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম।
অনিন্দ্য: যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি করতেন?
সিরাজ: ঐ বাড়ির জন্য চাকরি হয়নি। তারপর আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। এখানে বলা দরকার, আমার ন’বছর বয়সে মা আনোয়ারা বেগম মারা যান। তারপর আমার মা’র বিধবা বোনকে বাবা বিয়ে করেন। তখন আমরা একেবারে ছোট। দু’বছর করে তফাত ছিল ছোট ভাইদের সঙ্গে। আমাদের দেখবে কে? ঠাকুমা বুড়ো মানুষ। তাই বাবা মাসিকে বিয়ে করেছিলেন – তাঁর কাছেই আমরা মায়ের আদর পেয়েছিলাম। মাসিমারও স্বভাব ছিল ঠিক মায়ের মতো – বই পড়া। নানা জায়গা থেকে তাঁকেও বই এনে দিতে হত। কাজেই লেখাপড়ার চর্চা পরিবারে ছিল। উনি একদিন হঠাৎ আমাকে একটা ছবি বের করে দেখিয়ে বললেন, দ্যাখো, মেয়েটিকে পছন্দ হয়? বিয়ে করবে? আমি ‘হ্যাঁ’ বললাম। জীবনটা বদলাতে ইচ্ছে করছে তখন। বাবা শুনে খুব খুশি। আমার শ্বশুর ছিলেন বহরমপুর কালেক্টরিতে অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট। উনি মারা যাবার পর আমার ভাবি স্ত্রী হাসনে আরাকে নিয়ে আমার শাশুড়ি দেশের বাড়িতে আসেন। যাইহোক, এইসময় আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর জীবন একটু অন্যরকম মনে হল।
অনিন্দ্য: লেখালেখি?
সিরাজ: আমার স্ত্রী শহরের মেয়ে, খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়ত। সাহিত্য, গানবাজনা, নাচ-অভিনয় – এগুলো ভীষণ করত। আমার সঙ্গে বিয়ের পর ওদিকে কোনও বাধা রইল না। ও তাগিদ দিত। আমি বসে থাকতাম চুপচাপ। ভাবতাম, কবিতা লিখছি না কেন! কবিতা লিখতাম – তবে যা লিখতে চাইতাম তা আসত না। মনে হত, আরও যেসব কথা আছে – তা গদ্যে বলতে হবে। কোনও একটা অভিজ্ঞতা আমাকে চাপ দিচ্ছে লেখার জন্য। আমার স্ত্রী সবসময় বলত, তুমি বসে থাকো, ঘুরে বেড়াও, গান করো – তখন, আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শেখবার চেষ্টা করছি। ও বলত, তুমি লিখছ না কেন? তুমি লিখবে। তখন খাতা কলম নিয়ে লেখা শুরু করলাম। প্রথমেই লিখলাম একটা দীর্ঘ উপন্যাস, সেটা অনেক পরে বেরিয়েছিল – ‘কিম্বদন্তীর নায়ক’। মাঠে ফসল পাহারা দেয় এক শ্রেণির লোক, লোকের ধান যাতে পায়রা খেয়ে না নেয়, কেউ চুরি না করে। তার বদলে সামান্য কিছু ধান পায়। ওদের জীবন নিয়ে উপন্যাস।

অনিন্দ্য: গল্প না লিখে সরাসরি উপন্যাস?
সিরাজ: একেবারে সরাসরি উপন্যাস।
অনিন্দ্য: একটিও ছোটগল্প লেখেননি?
সিরাজ: না, তখনো কিছুই লিখিনি। ১৯৫৬ থেকে ’৫৮ দু’বছর ধরে ওটা লিখেছি। বহরমপুরের প্রাইমারি স্কুল টিচারদের ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকা, আমাদের পাশের গ্রামের একটি ছেলে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে একদিন হঠাৎ এসে বলল, ‘আপনি কি লেখেন?’ লিখি মানে তখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, গোকর্ণে শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি মন্দির, আমার বাবার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি, ওইখানে হাতে লেখা পত্রিকা ‘অঙ্কুর’ বের করা হত। হাতের লেখা থেকে ছবি আঁকা – সব আমিই করতাম। এইভাবে রটে ছিল যে আমি লিখি। ছেলেটি গল্প লিখে দিতে অনুরোধ করে। তাকে ‘কাঁচি’ নামে একটা প্রতীকী গল্প লিখে দিয়েছিলাম। তখনো আমি জানিনা পকেটমাররা কী দিয়ে পকেট কাটে। আমার মাথায় এল শুধু ‘কাঁচি’। কাঁচি কীভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে কাটছে – মানুষের পকেট কাটছে, জীবন কাটছে, আয়ু কাটছে। গল্পে ফিলোসফিক্যাল হবার চেষ্টা করেছি। তবে ভয়ে নিজের নামে না দিয়ে ‘ইবলিশ’ ছদ্মনামে লেখাটা দিলাম। ইবলিশ মানে শয়তান। তাকে স্বর্গের সবচেয়ে জ্ঞানী ফেরেস্তা বলা হত। সে বলেছিল, মাটিতে গড়া মানুষকে আমি প্রণাম করব না। কারণ আমি পরমসত্তা থেকে জন্ম নিয়েছি। পরমাত্মার অভিশাপে সে ইবলিশ হয়ে গেল। এইভাবে সে ঘুরছে মানুষের আশেপাশে। যেহেতু তখন আমি চারপাশে দেখছি, প্রচুর টাকা আসছে সরকার থেকে, লোকে দুহাতে ওড়াচ্ছে, মেরে দিচ্ছে – এর প্রতিবাদ স্বরূপ ইবলিশ নাম নিলাম। গল্পটা বেরলে একটা ছোট সার্কেলে হলেও খুব প্রশংসা…
অনিন্দ্য: আপনার গল্প সমগ্রে ওটা নেই।
সিরাজ: না, নেই। দু-তিনটে গল্প ওখানে লেখার পর, আরও যে সমস্ত লিটল ম্যাগাজিন ওখানে বেরুত, তারা আমার কাছে লেখা চায়। পত্রিকায় চিঠি বেরুল, লেখক স্বনামে আত্মপ্রকাশ করুন। পরিচয় হল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বহরমপুরে থাকে, জাহাজে ঘুরে ঘুরে দেশে এসে একটা চাকরির ট্রেনিং নিচ্ছে। অতীন ‘সমুদ্র মানুষ’ উপন্যাসটি লিখে এনে পড়ে শোনাত। আমার বাড়িতে আসত, আমিও ওর বাড়ি যেতাম। এইভাবে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমিও গল্প লিখি। অতীনের গল্প তখন অমৃত, দেশ-এ বেরিয়ে গেছে। আমিও দেশ, অমৃত- এ গল্প পাঠানো শুরু করলাম। ছাপা হয় না, ফিরে আসে। এখনো মনে পড়ে, সাইকেলে করে যেতাম পোস্ট অফিসে। ফেরত আসা গল্প পেতাম সেখান থেকে। ভাবতাম, ছাপা কেন হচ্ছে না? আবার ভালো করে পড়তাম-যেসব গল্প বেরুচ্ছে। এই করতে করতে বাইরের কাগজে আমার গল্প বেরুল। ‘ছোটগল্প’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, তাতে ভাগাড়ের উপর চোখে দেখা অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা গল্প বেরুল। তখন পাঁচ টাকা করে ডাক নিত ভাগাড়গুলো। লোকে ভাগাড়ে গরু মোষ ফেলে দিত। এখন ফেলে না, সব কেটে হাপিস করে দেয়, আমি মুসলমানদের কথাই বলছি। আমাদের পাড়ার ভাগাড়ের পাশ দিয়ে সাইকেলে করে আসছি প্রচন্ড খর রৌদ্রে, দেখছি সেখানে একটি বাচ্চা মেয়ে একটা কঞ্চি নিয়ে শকুনগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করছে, কারণ ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন এসেছে। মেয়েটি ‘ও বাবা, ও বাবা’ বলে চিৎকার করছে। ওর বাড়ি অনেক দূরে। পরে দেখলাম ওর বাবা দৌড়ে এসে, চারপাশের কুকুর-শকুনদের সঙ্গে লড়াই করে, চামড়া ছাড়িয়ে খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে গেল। সে এক মর্মান্তিক সংগ্রাম। তখন গাঁয়ের লোকে মরা গরুর মাংস খেত। অভিজ্ঞতাটা আমি সরাসরি লিখেছিলাম ছোট গল্পে। প্রবোধ মজুমদার লখনউ থেকে গল্পটি হিন্দিতে অনুবাদ করে ‘সারিকা’য় পাঠিয়েছিলেন। কমলেশ্বর ও নিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন।
অনিন্দ্য: ‘ভাগাড়’ গল্পটা?
সিরাজ: হ্যাঁ। এতে খুব প্রেরণা পেলাম। ওরা আবার লিখলেন আমাকে, শারদীয় সংখ্যার জন্য গল্প পাঠান। আমি সেই সময় দেশ-এ গল্প পাঠিয়ে যাচ্ছি, অতীনের লেখা বের হচ্ছে। তারপর হঠাৎ চোখ গেল বরেনের একটা গল্পের দিকে, ‘মৃত ইলিশের চোখে’। দেশ পত্রিকায় গল্পটি পড়ার পর বুঝতে পারলাম, ‘নতুন রীতি’ বলে যে আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে…
অনিন্দ্য: বিমল করের নেতৃত্বে।
সিরাজ: সেটা ঠিক কী! গল্পের ভাষা, টেক্সচার, স্টাইল – সব অন্যরকম। আমাকে তেমন চেষ্টা করতে হলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেটাকে মেশাতে হবে। মেশাতে গিয়ে আমি এক দুপুরে গ্রামের বাড়িতে একটা গল্প লিখতে শুরু করে দিলাম – দুটি ছেলে মেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে প্রেম করে, বাইরে বিয়ে করবে। একটা ছোট স্টেশন, গল্পের নাম ‘ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন’। ওটি পরিবেশ প্রধান গল্প। বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশন-মাস্টার তাদের দেখে বলে, ট্রেনের চাকা যাচ্ছে নরক থেকে নরকে। যেদিকেই যাবে দেখবে নরক। চারদিকে জীবন এরকম দুঃসহ হয়ে গেছে। গল্পটা পাঠানোর পর নভেম্বরেই ছাপা হয়ে গেল।
অনিন্দ্য: দেশ পত্রিকায়?
সিরাজ: হ্যাঁ।
অনিন্দ্য: এটাই কি ওখানে আপনার প্রথম গল্প?
সিরাজ: হ্যাঁ। ১৯৬২-তে বেরিয়ে গেল। তখন চীন–ভারত যুদ্ধ চলছে। আমি অমৃত-তে লেখা পাঠাই, ছাপা হয় না। যুগান্তরে যুদ্ধের রিপোর্ট বের হত। তখন আমি ‘সীমান্ত থেকে ফেরা’ নামে একটি গল্প লিখে পাঠালাম।
অনিন্দ্য: সেটি কি অমৃত পত্রিকায় বেরিয়েছিল?
সিরাজ: হ্যাঁ। দুটো কাগজে অল্প কিছু লেখা ছাপার পর কোনওটাতেই বেশি ছাপা হত না। বিমল করের সঙ্গে আলাপের পর জানতে পারলাম, ওখানে ছাপলে এখানে ছাপতে একটু অসুবিধা হয়।
অনিন্দ্য: ওখানে মানে অমৃত?
সিরাজ: অমৃত তখন সমানে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। ঐ ভালো কাগজটাকে উঠতে দেবেনা। তখন দেশ-এ লিখতাম। কিন্তু অমৃত-র মনীন্দ্র রায় আমাকে প্রথম উপন্যাস লেখার চান্স দিলেন। ওখানে ‘বন্যা’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম।

অনিন্দ্য: অমৃত পত্রিকায় প্রথম উপন্যাস বন্যা লিখলেন?
সিরাজ: না, অমৃতে প্রথম নয়। প্রথম লিখেছিলাম, পত্রিকার নাম ভুলে গেছি, বালিগঞ্জ থেকে বেরুত, ‘প্রান্তরে কিছু নেই’ নামে একটা উপন্যাস। সেটা আমার স্কুল জীবন, নবগ্রাম-ময়নার যে গোপালপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তাম সেই জীবন নিয়ে। সেটা বড় কিছু নয়। ছোট উপন্যাস – ধারাবাহিকভাবে বেরিয়ে ছিল।
অনিন্দ্য: সেটা ‘কিম্বদন্তীর নায়ক’ এর আগে না পরে?
সিরাজ: ‘কিম্বদন্তীর নায়ক’ আমার সর্বপ্রথম লেখা গদ্য ।
অনিন্দ্য: তারপর এটা?
সিরাজ: হ্যাঁ।
অনিন্দ্য: তারপর বন্যা?
সিরাজ: হ্যাঁ। এখানে এসে ‘বন্যা’ শুরু করলাম। সাহিত্যে তখন একটু সেক্সের চর্চা চলছিল। কর্তৃপক্ষ তাগিদ দিচ্ছেন। মণীন্দ্রদা আমাকে বললেন, চলছে যখন, চলতে দাও। রসের অভাব থাকবে কেন! (হাসি) । উপন্যাসটা লেগে গেল, যাকে বাজারে বলে। মনোজ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স করতেন, উনি ডেকে পাঠান প্রফুল্লকে দিয়ে। প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে তখন আমার আলাপ হয়েছে। ওঁর ‘পূর্ব পার্বতী’ যখন ধারাবাহিক বেরুচ্ছিল, তখন গ্রামে আমরা স্বামী-স্ত্রী দু’জনে পড়তাম। খুব ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম লেখাটার। মনোজবাবুর সঙ্গে কথা হল বন্যা ছাপা হবে। মনোজবাবু একদিন দুপুরবেলায় (এতদিন কাউকে বলিনি, তবে বলা উচিত) কেউ কাছে ছিল না, হঠাৎ খুব চাপা স্বরে বললেন, ‘তুমি যে মুসলমান, তোমাকে বেশি দূর এগুতে দেবে না’। শুনে আমি মনে মনে বলেছিলাম , এটাকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। তাতে…
অনিন্দ্য: ক্ষতি কিছুই হয়নি।
সিরাজ: ক্ষতি হয়নি। যাই হোক, ওখান থেকে বই বেরুল। কফি হাউসে আড্ডা হত। প্রথমে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল। দেখলাম তরুণ লেখক মহলে আমাকে নিয়ে উৎসাহ ছিল। তারপর আলাপ হয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সন্দীপন রেগুলার আসত। কফি হাউসে প্রত্যেকে পত্রিকা গুঁজে দিত। কাজেই লিটল ম্যাগাজিনে প্রচুর লিখতে হত আমাকে। দেখলাম, আমি বেশ ভালো পরিবেশে এসে পড়েছি। এটা বলার কারণ, ‘বন্যা’রও আগে অয়ন নামে একটি পত্রিকায় আমার প্রথম উপন্যাস ছাপা হয়েছিল। একটি মেয়ে – নয়নতারা নাম- তার একটা বাচ্চা ছিল। তারা নানারকম খেলা দেখাত, ময়াল সাপ, বাঘ, শজারুকে নিয়ে। সঙ্গে শিশুটিকে জুড়ে দিত। তার আড়ালে জুয়া খেলা চলত। বাবুদের ছেলেদের টাকা তারা এভাবে হাত করত। ওসব নিয়ে নয়নতারা নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। একদিন বরেন এসে বলল, তোর উপন্যাসটি ‘নবপত্র’র প্রসূনবাবু ছাপবেন, দেখা করিস। দেখা করলে প্রসূনবাবু বললেন, একটু বাড়িয়ে দিতে হবে, কারণ আকারে ছোট হচ্ছে। উপন্যাসটা আমি বাড়িয়ে দিলাম। অমিয়ভূষণের ‘নয়নতারা’ নামে একটা উপন্যাস ছিল, তাই নাম বদলে ‘নীল ঘরের নটী’ নামে সেটা ১৯৬৬ সালে ছাপা হয়। এরপর প্রকাশকরা ডাইরেক্টলি আমার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বড় পত্রিকা থেকে তখনো উপন্যাস লেখার কোনও প্রস্তাব পাইনি।
অনিন্দ্য: এটা কি ‘বন্যা’ লেখার আগে?
সিরাজ: হ্যাঁ, ‘বন্যা’ লেখার আগে। ‘বন্যা’ লিখেছি ১৯৬৮ সালে। তখন থেকে বছরে চারটে-পাঁচটে করে বই বেরুচ্ছে। ঘরে নয়, কলকাতায় বসে লিখছি, প্রকাশক এসে খেপ নিয়ে যাচ্ছে। এখন বুঝতে পারি, সাহিত্য জীবনে কত অন্যায় করেছি, যার ফলে সাহিত্যজগতে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারিনি ঠিকভাবে। তখন করতে হত, উপায় ছিল না। একটা ছোট চাকরি করতাম।
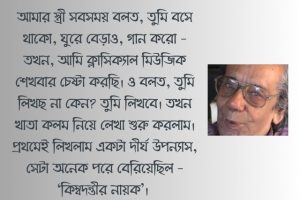
অনিন্দ্য: ভাণ্ডার পত্রিকায়?
সিরাজ: হ্যাঁ। কো-অপারেটিভ থেকে বেরুত। শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য ‘শেষ অভিসার’ কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। উনিই আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডার পত্রিকাটির স্বত্ব রাজ্য-সমবায় ইউনিয়ন কিনে নিয়েছিল। সহ-সম্পাদকের কাজ, ১২৫ টাকা মাইনে, তাতে সংসার চলত না। তখন ঐভাবে লিখছি, নিজেরই বিরক্তি লাগত যে এইভাবে লেখা হয় না। আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ছিল। শঙ্করের বাড়িতে, দেশপ্রিয় পার্কের দিকে সুতৃপ্তি রেঁস্তোরায় আড্ডা দিতাম। সেখান থেকে দলবেঁধে সন্দীপন, দিব্যেন্দু পালিত – সবাই বাড়িতে এসে বসতাম। দুপুরবেলায় গল্প পড়া হত। প্রতিদিন কফি-হাউসের আড্ডা ছিল। আড্ডায় এসে মনে হত সাহিত্যের মধ্যেই আছি। বই বের হচ্ছে, বড় বা ব্যবসায়িক পত্রিকায় গল্প লিখতে বলে, কখনো বা উপন্যাসও লিখতে বলে – সাধারণ সংখ্যায়। শারদীয় সংখ্যায় ডাকে না বিশেষ। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের একদিন আমি ক্যানটোফার লেন থেকে পদ্মপুকুর চুল কাটতে গেছি।
অনিন্দ্য: জায়গাটা কি ক্যানটোফার লেন?
সিরাজ: হ্যাঁ, ওখানে তারাশঙ্করও থাকতেন একসময়। রায়টের পর ওখানকার হিন্দুরা সব চলে যান।
অনিন্দ্য: ছেচল্লিশের রায়টে?
সিরাজ: হ্যাঁ। মিলটন স্ট্রিটের পাশে, সেখানে নরেন্দ্রনাথ মিত্র থাকতেন। আমি ওখানে চুল কাটতে গেছি, হঠাৎ সামনে কালো অ্যাম্বাসাডর থেকে আমার বড় ছেলে অভিজিৎ নামল। সঙ্গে নামেন একজন কালো, লম্বা তাগড়াই লোক। আমাকে বলেন সন্তোষ কুমার ঘোষ বলেছেন, যেখানে যে অবস্থায় পাবেন, তুলে নিয়ে আসুন। সন্তোষদার সম্পর্কে খুব কুখ্যাতি শুনতাম, খুব রাগি মেজাজি লোক। শক্তি আমাকে বলেছিল, সন্তোষদা তোর লেখাটা পড়েছেন। ‘বন্যা’ সম্পর্কে সন্তোষদা বলেছেন, এটা কিছু হচ্ছে না। বলো, এটা বন্ধ করে দিতে। … তখন আমার উপায় ছিল না। ‘বন্যা’ ভালো উপন্যাস হয়নি – এটা আমি এখনো বলি। … কী করব, ওর সঙ্গে গেলাম। সন্তোষদা ভবানীপুরে থাকতেন। পাশে বসে বললেন, ‘আপনার লেখায় তারাশঙ্করে মাটি ও মানুষ কেন থাকে?’ তখন সদ্য ‘প্লাবন’ নামে আমার একটা গল্প সাপ্তাহিক ধ্বনি পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ওঁকে বললাম, ‘আমি লিখি আমার এলাকার কথা’। উনি জানতে চান, ‘কোথায় আপনার এলাকা?’ জানালাম, কান্দি মহকুমা অঞ্চলে। তা হঠাৎ উনি আমার হাত ধরে বললেন, ‘তুমি কি জানো তারাশঙ্করকে আমি আমার দ্বিতীয় পিতার তুল্য মনে করি”। সেই থেকে গল্প আরম্ভ হয়ে গেল, তুমি সম্বোধনে। উনি তারাশঙ্করের খুব ভক্ত ছিলেন। যাই হোক, আমার লেখায়, তারাশঙ্করের ছাপ ঐ-প্রথম দিকের কিছু লেখায়। ‘কিম্বদন্তীর নায়ক’ পরে বই হয়ে কথাশিল্প থেকে বেরুল। তখন দেশ পত্রিকায় বলেছিল, ওঁর লেখা তারাশঙ্কর-‘গন্ধি’। এটা স্বাভাবিক। যদিও আমি তারাশঙ্করকে তখনো তত পড়িনি, কারণ আলকাপ করার সময় আমি ৫-৬ বছর খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িনি। কাজেই প্রভাব পড়ার তেমন সুযোগ ছিল না। আসলে যে মানুষগুলোকে, যে পরিবেশ নিয়ে আমি লিখি…
অনিন্দ্য: দু’জনেরই রাঢ় বাংলার পরিবেশ।
সিরাজ: হ্যাঁ, তাই। তখন থেকে আমি একটু আলাদা হবার, সচেতনভাবে ওঁর থেকে দূরে সরে আসার চেষ্টা শুরু করলাম। ঐ অঞ্চলের মানুষ নিয়ে লিখেছি মানে ঐ আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক চরিত্র নিয়ে। শাক্ত এলাকা, আমাদের ওখানে স্বৈরিনী মেয়েদের খুব প্রাবল্য। আমার অনেক গল্প উপন্যাসে মেয়েরা খুব সাহসিনী, এটা এসে গেছে আপনা আপনি। আমার ‘উত্তর জাহ্নবী’ উপন্যাসটি গঙ্গাসাগরের পটভূমিকায়। একা একটি মেয়ে স্বর্ণ, তার বাবা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিল, মিথ্যা অপবাদে তাকে জেল খাটাল … স্বর্ণ একা সব করত।
অনিন্দ্য: মনে হয় এসব আপনার দেখা চরিত্র।
সিরাজ: দেখা। কিছুকাল আগেও দেশ পত্রিকায় একজন সমালোচক লিখেছেন, অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান কুড়িয়ে লেখার ব্যাপারে ইনি তারাশঙ্করের সমগোত্রীয়। আমার ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’ বইতে ঐ কথাটি উল্লেখ করে বলেছি যে তিনি হিমালয়, আমি উইঢিপি। তাই ঐ প্রশ্ন আসে না। তবে অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করি এই অর্থে যে আমি অবনির্মাণ করি, ডি-কনস্ট্রাকশন করি। এখানে আমার ‘গোঘ্ন’ গল্পের কথা বলি। আমাদের গ্রামের পাশের পাকা রাস্তায় পুজোর সময় বেড়াতে বেরিয়েছি, একা একা বেরিয়ে পড়তাম, হাতে বাঁশি থাকত। বাঁশি বাজাতাম। দেখছি, একটা লোক কথা বলতে বলতে আসছে আর গরুর গাড়ির চাকার শব্দ, তখন ট্রাক ইত্যাদি ছিল না। তারপর দেখি লোকটা গাড়ির জোয়ালের একদিক ধরে টানছে, সেই সঙ্গে একটা রুগ্ন গরু বেধে দিয়েছে, সেটা আস্তে আস্তে আসছে। লোকটা গাড়ি টানছে আর বলছে, বাঘড়ি এলাকার লোকের ভাষায়, ‘আদমি হয়ে তোর যন্তন্না বুঝতে পারলাম।‘ লাইনটা আমার মাথায় স্ট্রাইক করল।
অনিন্দ্য: ‘গোঘ্ন’ খুব ভালো গল্প। তবে আপনার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সংকলনে ওটা নেই।
সিরাজ: ওতে বাদ গেছে… দেশ, আনন্দবাজারে আমাকে সন্তোষদা নিয়ে গেলেন। আস্তে-আস্তে ওখানেই থিতু হলাম। তারপর এই বাড়িতে চলে এলাম।
অনিন্দ্য: সেটা কবে?
সিরাজ: ১৯৭০ সালে। তখন লেখার খুব চাপ। আগের চাকরি ছেড়ে আনন্দবাজার-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। পাঁচশ টাকা দিত আর বিভিন্ন ধরনের কাজ… টুকরো-টাকরা অনুবাদ , হয়তো কোথাও পাঠাল।
অনিন্দ্য: ফ্রি লান্স করতেন?
সিরাজ: ফ্রি লান্সই বলা চলে, আমাকে ওঁরা রেখেছিলেন ঠিকা শ্রমিকের মতো। পাঁচ’শ টাকা তখন যথেষ্ট। ওখানে থাকতে থাকতে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস, হঠাৎ একদিন সন্তোষদা বাড়িতে এসে হাজির। যখন-তখন আসতেন। বাবার সামনে এসে বললেন, ‘সিরাজের চাকরি করে দিয়েছি। সাব-এডিটরের চাকরি।‘ অশোকবাবু আমাকে প্রথম থেকেই স্নেহ করতেন কিন্তু ওঁর কাছে সন্তোষদা অমিতাভ চৌধুরীকে এগিয়ে দিতেন। অশোকবাবু বলতেন, ‘ও ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মুসলমান। সাংঘাতিক। ওকে চাকরি দেব’!
অনিন্দ্য: কেন , ধুতি পরা মুসলমান চলবে না?
সিরাজ: (হেসে) পরে একদিন আমার নিয়োগপত্রে সই করে দিলেন।
অনিন্দ্য: সেটা কোন সাল?
সিরাজ: ১৯৭৩ এর মার্চ। সেই চাকরি-জীবন চলল ১৯৯৩ পর্যন্ত। সে জীবন আলাদা, সাংবাদিক জীবন। আনন্দবাজারে থাকার জীবন একদিক থেকে ভালো – সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল। রমাপদ চৌধুরীর ঘরে কিংবা ‘দেশ’ পত্রিকার বিমলদার কাছে আড্ডা হত। অনেক সাহিত্যিক আসতেন, দিনগুলো খুব ভালো কাটত। অন্যদিকে ওখানে একটা পারস্পরিক চাপা দলাদলি ছিল। কী করে অমুককে বসানো যায়, অমুককে তোলা যায়।
অনিন্দ্য: কারা করত এসব? মালিকপক্ষ?
সিরাজ: মালিকপক্ষের ইচ্ছেতেই করত। আমি সন্তোষদার লোক, এটা সাগরদার কাছে … সাগরদা এমনিতে ভালোই কথা বলতেন, আড্ডা দিতেন। সবই ঠিক ছিল। উনি আমাকে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বলেছিলেন। আমি তৈরিও হচ্ছিলাম। ‘মায়ামৃদঙ্গ’ সেখানেই বড় আকারে বেরুত। সন্তোষদার ‘শেষ নমস্কার: শ্রীচরণেষু মা’কে শেষ হলে ওখানে আমারটা বেরুনোর কথা। ইতিমধ্যে দে’জ থেকে আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিল। তাই দে’জ-এ লেখাটা দিয়ে দিলাম।
অনিন্দ্য: ‘মায়ামৃদঙ্গ’ ?
সিরাজ: দিয়ে দিলাম। না-দিলেই ভালো করতাম।
অনিন্দ্য: বড় করতে পারতেন।
সিরাজ: অনেক বড় হত। পড়লেই বোঝা যায় সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে।
অনিন্দ্য: দে’জ থেকে বেরুনোর পর সেই সুযোগ থাকল না।
সিরাজ: যাই হোক, সাগরদা এটা ভালোভাবে নেননি।

অনিন্দ্য: ‘মায়ামৃদঙ্গ’-এর ঝাঁকসা ওস্তাদ চরিত্রটার সঙ্গে আপনার ব্যক্তি-জীবনের সম্পর্ক কতখানি?
সিরাজ: ‘মায়ামৃদঙ্গ’-এ যা লিখেছি, তার অধিকাংশই অভিজ্ঞতা প্রসূত। বানাতে খুব কম হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবেই হয়েছিল। আমাদের তিনজনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দলে। আমি লক্ষ করতাম আলকাপের নাট্য রীতিটা উনি কীভাবে করছেন। সেই জন্য আমি ওঁকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।
অনিন্দ্য: উপন্যাসটির কোনও চরিত্রের ওপর আপনার সরাসরি প্রভাব আছে?
সিরাজ: সনাতন মাস্টার আমিই।
অনিন্দ্য: সেখানে বানানো কিছু নেই?
সিরাজ: সামান্য আছে, প্রেমের ব্যাপারটা।
অনিন্দ্য: ভ্রাম্যমান জীবনে ছেলেরাই মেয়ের রোল করতেন। ‘মায়ামৃদঙ্গ’-এ তেমন কিছু চরিত্র আছে। দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সমকামী ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রকৃত স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হয়ে মেয়ে সাজা ছেলেদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলত। এটা কি ভ্রাম্যমান জীবনে নারীসঙ্গের অভাব থেকেই ঘটত?
সিরাজ: অভাব নয়। নারীসঙ্গের সুযোগ বেশি ছিল ওই জীবনে। কারণ আলকাপ মেয়েরাই বেশি শুনতে আসত।
অনিন্দ্য: যতদূর জানি আপনাদের দলে কোনও মহিলা ছিলেন না।
সিরাজ: না, মহিলা ছিলেন না।
অনিন্দ্য: ফলে শারীরিক আর মানসিক দিক থেকে নারীসঙ্গের অভাব ছিল।
সিরাজ: অভাব খানিকটা ছিল। আলকাপের নেশাই এমন যে সব কিছু ভুলে থাকত। মাঝে মধ্যে সবাই বাড়ি যেত। একটা সিজনে ওরা কাজ করত।
অনিন্দ্য: শুধু ‘মায়ামৃদঙ্গ’ই নয়, আপনার ‘সাজ ভেসে গেল’ আর ‘বাগাল’ গল্পেও কিছু চরিত্র নারী হয়েও নারী নয়, পুরুষ হয়েও পুরুষ নয় – এক ধরনের মিশ্রণ। আপনার আলকাপ দলের অভিজ্ঞতা আছে, এরকম ফিলিং কি হত?
সিরাজ: হ্যাঁ, আমি শেষ যে ছোঁড়াটাকে তালিম দিয়ে তৈরি করেছিলাম, সে আমার বাড়িতে শেষ অবধি ছিল। ছেলেটির নাম আজিজুল। ফর্সা, একেবারে মেয়ে। ওরকম অনেক ছিল। দেশ পত্রিকায় যার ছবি ছেপে ছিল, ফ্রক পরা অবস্থায়, তাকে মেয়ে ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। ছোটবেলা থেকে মন, পোশাক – সব দিক থেকে ঐভাবে তৈরি হয়েছে।
অনিন্দ্য: স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে নিশ্চয় তাদের অসুবিধে হত?
সিরাজ: যাদের যোগ্যতা থাকত তাদের অসুবিধে হত না।
অনিন্দ্য: তারা অন্য জীবিকায় গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারত?
সিরাজ: যারা পারত না তাদের সমস্যা হত। এরকম অনেক ছোকরা শেষ দিকে নানারকম নেশা করে নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছিল। মনসুর নামে একটা ছোকরা ছিল আমার, ’৮৪-’৮৫ তে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, তার বয়স তখন অনেক। প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। ও নিজের নাম বলায় আমি বললাম, ‘তোর চেহারা এরকম হয়ে গেল কেন’? ও বলল, ‘কী করব! গাঁজা খাই, নেশা ভাঙ ছাড়া থাকতে পারি না’। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। গাঁজা খেতে খেতেই পরে মারা গেল।
অনিন্দ্য: অবাস্তব কৃত্রিম একটা জগতের মধ্যে…
সিরাজ: ঐ জগতে থাকতে যে মূল্য পেত গ্রাম সমাজের কাছে, পরবর্তী জীবনে সেটা আর পায়নি। যদি তার আরও গান চালিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা থাকত… ‘মায়ামৃদঙ্গ’-এ যে সুবর্ণ তার আসল নাম সুধীর দাস। আলকাপের পর সুধীর কীর্তনের দল করেছিল। বহরমপুরে একজন আমার নাটক করেছে ‘মায়া’ বলে।
অনিন্দ্য: ‘মায়ামৃদঙ্গ’ অবলম্বনে?
সিরাজ: হ্যাঁ। কলকাতায় হয়েছে রবীন্দ্র সদনে। ওস্তাদ ঝাঁকসার জীবন নিয়ে।
অনিন্দ্য: সনাতন মাস্টার আপনি। আলকাপ দলের মাস্টার ছিলেন।
সিরাজ: হ্যাঁ। গোকর্ণে আমি একজনের কাছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখতাম। তখন আমি থিয়েটার করি। সকালবেলা বাড়িতে রেওয়াজ করতে বসলেই আমার ছেলে অভিজিৎ হামাগুড়ি দিয়ে এসে কিছুতেই গান করতে দিত না। এভাবেই সব শেষ হয়ে গেল। এখন আর বাঁশি বাজাতে পারি না। দুটো বাঁশি রেখে দিয়েছি স্মৃতি হিসেবে। ওটা অন্যরকম জগৎ ছিল অনেকদিন ধরে আমার স্বপ্নে, আমার চেতনায়। এতবছর পর সবই হাস্যকর মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনের ছ’টা বছর নষ্ট করিনি তো! কথাটা দীপেনের কাছে বলেছিলাম।
অনিন্দ্য: লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়?
সিরাজ: হ্যাঁ, কফি হাউসে। বলেছিলাম, যদি ঐ সময় পার্টির কাজ করতাম কিংবা পড়াশুনা করে এম. এ. করতাম। সব শুনে ও বলল, ‘বলেন কী মশাই। আপনার মতো লাভবান ক’জন হয়েছে? আপনি যে এভাবে ছ-বছর ঘুরেছেন, দেশের তৃণমূল স্তরের মানুষদের দেখেছেন, পার্টির কোনও সদস্য, কোনও কৃষক সভার নেতা – কেউ পারবে না’।
অনিন্দ্য: আপনি এতে করে গ্রামজীবন যেভাবে চিনেছেন অন্য কোনওভাবে তা পারতেন না। বাড়িতে বসে কিংবা কলকাতায় বসে বই পড়ে ঠিক…
সিরাজ: হত না, ও আলাদা জিনিস। নানা বাড়ির খাওয়া, একেক অঞ্চলে একেক ধরনের লোক।
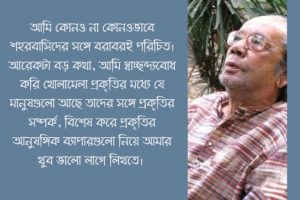
অনিন্দ্য: বিভিন্ন পেশার লোক।
সিরাজ: ঠিক তাই। অনেক ধরনের মানুষ।
অনিন্দ্য: আমার মনে হয় ওই ছ’বছরের অভিজ্ঞতা লেখক হিসেবে আপনাকে সমৃদ্ধ করেছে।
সিরাজ: দেশের নিম্নবর্গের আত্মার কন্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম। সেই স্তরে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নেই। ‘সাজ ভেসে গেল’ নামে আমার একটা গল্প আছে।
অনিন্দ্য: পড়েছি।
সিরাজ: ওতে যা লিখেছি তার অনেকটাই সত্যি। লোকটার আসল নাম মোল্লা বক্স। তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না, হ্যারিকেন জ্বালিয়ে গান হত। হ্যাজাকের আলোও অনেক জায়গায় থাকত না। শেষের দিকে ইলেকট্রিসিটি আসার পর সেই আলোতেও অনেক জায়গায় আলকাপ হয়েছে। তবে ’৬২ সালেই গ্রামের আলকাপ শেষ হয়ে গেছে।
অনিন্দ্য: রায়গঞ্জে আমার বাড়ি, ছেলেবেলা সেখানেই কেটেছে। সেখানে মালদার গম্ভীরা গান অনেক শুনেছি। গম্ভীরার সঙ্গে আলকাপের পার্থক্য ঠিক কোথায়?
সিরাজ: পার্থক্য হচ্ছে, গম্ভীরা হল শিবকেন্দ্রিক। শিবের বন্দনা করে শুরু হত। কিন্তু নাটকগুলো ইচ্ছে মতো চলত। মানে…
অনিন্দ্য: কোনও লিখিত…
সিরাজ: নাটক নেই। লিখিত গানও বিশেষ নেই বললেই চলে। আলকাপকে গম্ভীরা সরাতে পারেনি কারণ গম্ভীরা ধর্মকেন্দ্রিক ছিল।
অনিন্দ্য: গম্ভীরা এখন টিকে আছে কিনা সন্দেহ… মটরবাবু ছিলেন।
সিরাজ: মটরবাবু! উনি কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে গ্রামেগঞ্জে গান করতেন।
অনিন্দ্য: গ্রামের মানুষ হলেও আপনি দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী। ‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’, ‘প্রেম ঘৃণা দাহ’ প্রভৃতি উপন্যাস কলকাতাকেন্দ্রিক। তা সত্ত্বেও আপনার গল্প-উপন্যাসে গ্রামজীবনই ঘুরে ফিরে এসেছে। গ্রামজীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে কি আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?
সিরাজ: অবশ্যই করি। কারণ শহরে জন্মে বড় হয়ে উঠলে যে উপলব্ধি হয় বা যে আনুষঙ্গিক বোধ তৈরি হয় মনের মধ্যে সেটা আমার থাকার কথা নয়, যদিও আমি কোনও না কোনওভাবে শহরবাসিদের সঙ্গে বরাবরই পরিচিত। আরেকটা বড় কথা, আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে যে মানুষগুলো আছে তাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, বিশেষ করে প্রকৃতির আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার খুব ভালো লাগে লিখতে। আমার ওরকম একটা গল্প আছে ‘বৃষ্টিতে দাবানল’।
অনিন্দ্য: গল্পটা পড়েছি।
সিরাজ: ওটা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনায় লেখা হয়েছিল ‘পড়তে গা ঘিনঘিন করে’। বুঝলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বৃষ্টির দিনে গ্রামের প্রকৃতি এমন আচ্ছন্ন হয় – কিছু করার থাকে না মানুষের। মানে ধীরে ধীরে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া। সেই অবস্থায় জনমজুর খেটে খাওয়া একটা মানুষ। তার স্ত্রী নেই, গৃহ নেই – কিছুই নেই। যেখানে যাচ্ছে দেখছে লোকেরা বউ নিয়ে আনন্দ করছে। আর কিছু করার নেই, কী করবে! এর মধ্যে তার আদি রিপু … প্রকৃতির কাছে না থাকলে, এগুলো বোঝা যায় না। এ অভিজ্ঞতা আমার এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে,… দেখেছি, গোটা গ্রাম যেন একটা আদিম অন্ধ-কামনার মধ্যে বুঁদ হয়ে যায়, এই অনুভূতি গাঁয়ে না জন্মালে, পর্যবেক্ষণ না-করলে বোঝা যায় না। সেই নারাণ কত অপকীর্তি করে, শেয়াল ঠাকুরের জন্য রেখে যাওয়া ভাত খেয়ে খিদে মেটায়, অবলা-বোবা মেয়েটির ওপর অত্যাচার করে – শেষে সে থানায় এল কেন – এটা সমালোচকের মাথায় ঢুকল না। সে ‘বাবু, আমার একটা কথা আছে’ বলে পুলিশের সামনে বারে বারে বলেছে, ‘শরীর বড় গন্ডার, সে কিছু মানে না’। নিজের শরীরকে শাস্তি দিতে চাইছে, সে চায়, পুলিশ তাকে মেরে ফেলুক। ইচ্ছে করলে সে পালিয়ে যেতে পারত। একজন মানুষ ধরা দিতে এসেছে গভীর অনুশোচনায়, একটি বোবা মেয়েকে আমি অন্ধ প্রবৃত্তির বশে নষ্ট করেছি, এর শাস্তি সে নিজেকে দিতে এসেছে। এখানেই মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটেছে তার। এটা সমালোচকের মাথায় এল না? এই গল্পের শেষাংশ আমার চোখে দেখা, মঙ্গলকোট থানায়, পিসিমার গ্রামে। বৃষ্টির দিন, সন্ধ্যেবেলায় একটা লোক কাঁদতে-কাঁদতে থানায় এসে বলছে, ‘আমাকে মারুন, মেরে ফেলুন। আমার শরীর বড় গন্ডার’। কথাটা আমার মাথায় থেকে গিয়েছিল।

অনিন্দ্য: আপনার অনেক গল্প উপন্যাসে শহরের চরিত্র গ্রামে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, জেগে উঠেছে তাদের অবচেতন মন। ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা আপনার উপন্যাস ‘বেদবতী’র নায়িকা হিন্ডা প্রকৃতির কন্যা। কিশোর-পাঠ্য রহস্য-কাহিনির কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারও প্রকৃতি-প্রেমিক। ‘তৃণভূমি’র নায়ক নিশানাথও তাই। আপনার সৃষ্টি করা প্রকৃতি-প্রেমিক অনেক চরিত্রই ক্রমশ অসামাজিক, এমনকী নিষ্ঠুর হয়ে যায়। ‘তৃণভূমি’র একটি চরিত্র প্রকৃতির মধ্যে একজনকে খুন করে বসে।
সিরাজ: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে বলেছেন ঘাতক মোটিফ। মোটিফটা আমার সব জায়গায় আছে। ছেলেবেলা থেকে যা সব দেখেছি আমাদের অঞ্চলে, উত্তর রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করে, কী হিন্দু কী মুসলমান, ঘোর শাক্ত, এদের মধ্যে রক্তের স্পৃহা যেন প্রবল। এটা…
অনিন্দ্য: রুক্ষ।
সিরাজ: রুক্ষ এবং কর্কশ।
অনিন্দ্য: আমি শান্তিনিকেতনে দু-তিন বছর ছিলাম। রাঢ় অঞ্চল যে লাল মাটির দেশ, সেই পরিবেশ, গ্রাম-জীবনও কিছুটা দেখেছি। সেখানে আমিও এই রুক্ষতা অনুভব করেছি।
সিরাজ: এটা ছিল। ঘাতক মোটিফ ব্যবহারের একটা কারণ, প্রকৃতি যেন অন্ধচেতনার বশে থাকে। জিম করবেটের একটা লেখায় পড়েছিলাম, হরিণীর সদ্যোজাত বাচ্চাকে বাঘ তুলে নিয়ে গেল। হরিণী কিছুক্ষণ উদাস চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর আবার গাছের পাতায় মুখ দিল। প্রকৃতিতে রক্তের কোনও মূল্য নেই। সেখানে শোক-কান্না কিছু নেই। সৃষ্টি আর ধ্বংস – দুই-ই সেখানে সমার্থক। হাজার-হাজার মানুষ ভেসে যাচ্ছে বন্যায়, আবার দেখা যাচ্ছে, সবুজ ফসল জন্ম নিচ্ছে মানুষের হাতে। ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি, এটা আমাকে খুব ভাবায়। আমি চোখে দেখেছি, আগে যে প্রজাপতির কথা বলেছি, সব ডুবে গেল তবু উড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির কাছে মানুষও ঠিক তেমনি অসহায়। আরেকটা ঘটনা আমার মনে আছে, যে হিজল অঞ্চলের কথা বলেছি, ছেলেমেয়েরা সেখানে সবাই খুব ডাকাবুকো ছিল। এখন অবশ্য ওখানে সবই বদলে গেছে। একটা আলকাপ দল আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে রিহার্সাল শেষ হয়ে গিয়েছে, দোতলায় শুয়ে আছি। যে লোকটা দল চালাত সে দুর্দান্ত খুনে বদমাশ। বাশির তার নাম। অনেক রাতে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে এসে বলল, ‘আমি কি আসব?’ বললাম, ‘চলে এসো’। তার এক হাতে হেঁসো আর এক হাতে লাঠি। সারা গায়ে জল, গা-হাত ধুয়ে এসেছে। কাছে এসে বলল, ‘কিছুক্ষণ আগে আমি হাজি সাহেবকে খুন করে এলাম’। বলেই হাউমাউ করে পা ধরে কান্না ‘মাস্টার-মশাই কেন আমি এরকম করি! আমার মধ্যে এটা কী করে জাগে! আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, কিছু একটা দিন’। সে তখন প্রচন্ড অনুতপ্ত। পরবর্তীকালে আমি চলে এলাম। লোকটা পরে একটা গ্রামে বদমায়েশি করতে গিয়েছিল, গ্রামের লোকে তাকে মেরে এমন করেছে যে, রিক্সায় যখন তুলছে সে ‘পানি, পানি’ বলে চিৎকার করছে আর লোকে তার মুখে পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে। কী নির্মম প্রকৃতি। মনে হত, কেউ কি নেই মাথার উপরে দেখবার মতো! হাজার-হাজার মানুষ মরে গেল হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মরে যাচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে – তারা কোনও দোষ করেনি। প্রকৃতির কী অন্ধচেতনা! মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। এই ভেঙ্গে যাওয়া গড়ে ওঠা অথচ আমরা প্রকৃতির হাত ধরে আছি।
অনিন্দ্য: আপনি মনে হয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন?
সিরাজ: না, আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী নই। … এইগুলো আমাকে বিশেষবোধে উদ্রিক্ত করে। সেটাই আমি সবক্ষেত্রে লিখি।
অনিন্দ্য: প্রকৃতিচেতনা আপনার লেখক জীবনের গোড়ার দিকে যেমন ছিল, আজও কি ঠিক তেমনই আছে?
সিরাজ: আজও তাই। বিশ্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, সেগুলো আমার বিশ্বাসকেই সমর্থন করছে। মানুষ হাজার-হাজার বছর ধরে এই করে আসছে। আগে একভাবে, এখন অন্যভাবে করছে। এটাই কি প্রকৃতির, ইতিহাসের নিয়ম?
অনিন্দ্য: আপনার কিছু শহুরে চরিত্র আছে, যারা গ্রামে এসে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। এতে একভাবে প্রকৃতিবাদকে আপনি সমর্থন করছেন।
সিরাজ: হ্যাঁ, তাই।
অনিন্দ্য: আজকের যুগে আমরা প্রকৃতিবাদকে কতটুকু সমর্থন করতে পারি? এটা কতখানি বাস্তবসম্মত?
সিরাজ: এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। আমি আমেরিকায় গিয়েছি। ওখানে প্রকৃতি এত সাজানো-গোছানো, প্রকৃতিকে এত ভালোবাসা- এখানে দেখেনি। প্রকৃতির সান্নিধ্যে না-থাকলে যে মরে যাবে, ওরা এটা বুঝেছে। পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে ওরা খুবই সচেতন। ওখানে আমি একটা সাদা সোয়েটার কিনেছিলাম। প্রায় চারমাস ওখানে ছিলাম। সেটা বেশ সুন্দর ছিল, যেই কলকাতায় এলাম- ময়লা হয়ে গেল।
অনিন্দ্য: পরিবেশের কারণে?
সিরাজ: পরিবেশ-দূষণ এখানে অত্যন্ত বেশি।
অনিন্দ্য: আপনি ওখানে আইওয়া ইউনিভার্সিটির ডাকে…
সিরাজ: হ্যাঁ, ওদের ডাকে গিয়েছিলাম।
অনিন্দ্য: সেই পরিবেশ নিয়ে আপনি ‘আন্তর্জাতিক’ নামে একটা গল্পও লিখেছেন। মার্কিন-প্রবাস আপনার চেতনায় কোনও প্রভাব ফেলেছে কি?
সিরাজ: মার্কিনদের যে কনজ্যুমার লাইফ…আজকে একটা গাড়ি কিনলাম, পরে অন্য মডেলের গাড়ি এল, পুরনো ফেলে দিয়ে আরেকটা কিনলাম। এই ক্রমাগত কেনায় ওদের যে আনন্দ, এতেই জীবনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা – এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
অনিন্দ্য: এটা অনেকদিন ধরেই…
সিরাজ: অনেকদিন ধরেই চলছে এই ভোগবাদ, কনজ্যুমারিজম। আমেরিকায় যা দেখে এসেছি, আমাদের এখানেও সেইটাকেই ফলো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে অনেক বিষয়েই ওরা এখন সচেতন। আমি শনি আর রবিবার – দু’টো দিন একটা ফার্ম হাউসে ছিলাম। সেটা এক চাষির বাড়ি, তার পাঁচশো একর জমি। একা বুড়ো নিজে যন্ত্র চালিয়ে ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করে। যন্ত্র দিয়েই ফসল গুদামজাত হয়। বুড়ো-বুড়ি থাকে। তাদের এক নাতনির বাবা মারা গিয়েছেন – সে-ও তাদের কাছে থাকে। বয়স হবে ন-দশ বছর। ওখানে গিয়ে মনে হল যেন নিজের আত্মীয় বাড়িতে এসেছি। বাচ্চা মেয়েটি আমার হাত ধরে ছিল, ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দেওয়াতে সে বলল, ইন্ডিয়ান! তবে মাথায় পালক কোথায়?
অনিন্দ্য: রেড ইন্ডিয়ান ভেবেছে।
সিরাজ: হ্যাঁ। পরে বুঝতে পেরে বলল, ও, ইউ আর ওরিয়েন্টাল। ওর সঙ্গে অনেক গল্প হল। চাষি হলেও ওরা বেশ ধনী। বাড়িতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শনিবার গেস্ট এসেছে শুনে ঘনিষ্ঠজনরা সব চলে এল, সারারাত নাচ-গান করল। ওখানকার কান্ট্রিম্যানরা অত্যন্ত ভালো মানুষ।
অনিন্দ্য: ‘উড়ো চিঠি’ গল্পে আপনি অতীতের গ্রামজীবনকে ইউটোপিয়ার মতো করে দেখিয়েছেন, সমস্ত গ্রাম একটা সুখী-পরিবারের মতো। কোথাও দ্বন্দ্ব, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা নেই। বর্তমানই যা কিছু নোংরা। – অতীতের গ্রামজীবনে কি সত্যিই আদর্শ সমাজ ছিল?
সিরাজ: এই ধরনের গ্রাম ছিল। আমাদের গ্রামে রাস্তাঘাট আছে, সড়কের সঙ্গে, রেলস্টেশনের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। তবে এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বর্ষার পর ধান তুলে নিলেই গরুর গাড়ি ঢোকে। সেই ধরনের গ্রামে এই ধরনের আত্মীয়তা দেখেছি। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে মাসির ছেলের সঙ্গে বা কাকার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়। ফলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয়, সেখানে এই ধরনের সরলতা দেখেছি। … ঐ বদরু আর সদরু দুই বুড়ো দুই জায়গার। এই বদরু আর একটা চরিত্র আমার লেখায় অনেকবার এসেছে- প্রহ্লাদ খুড়ো। এই প্রহ্লাদ খুড়ো আমার দেখা চরিত্র। দ্বারকা নদীর ধারে নবগ্রামে বাড়ি তার। জাল বুনত আর বসে-বসে অদ্ভুত ধরনের গল্প করত। প্রহ্লাদ খুড়োকে নিয়ে ‘একটি অনুসন্ধান’ নামে গল্প লিখেছি – পরে আরও অনেক গল্প লিখেছি। বদরু বুড়ো একালের কিছু দেখতে পারে না। চিঠি – চিঠি কেন? কী দরকার! তার কাছে চিঠি মানে ভয়ঙ্কর কিছু। এরকম মানুষ দেখেছি আমি।
অনিন্দ্য: পুরনোপন্থী?
সিরাজ: হ্যাঁ, তাই। আমি যে ধরনের গল্প লিখি, তাতে খুব একটা কল্পনা করতে হয় না, এসে যায়। তবে সব গল্পই যে ভালো হবে তার কোনও মানে নেই। … এখন আর সে গ্রাম নেই। গ্রাম শেষ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চায়েত ঢুকে। আজকে গ্রামে কোনও মানুষকে আপনমনে গান করতে শুনি না। এর চেয়ে সাংঘাতিক কি কিছু হতে পারে! আগে গ্রামে গেলে, রাত্রিবেলায় গান গাইতে গাইতে লোকে বাড়ি ফিরছে – শুনতে পেতাম। এখন কেউ গান গায় না, শুধু পঞ্চায়েতি আর দলাদলি।
অনিন্দ্য: আপনার অনেক গল্পই উত্তমপুরুষে লেখা। ‘রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র’, ‘আশ্রয়’ ইত্যাদি উপন্যাসও তাই। এই পদ্ধতিতে লিখলে কি টেকনিক্যালি বেশি সুবিধা পাওয়া যায়?
সিরাজ: একটু বেশি সুবিধা হয়, উত্তম পুরুষে নিজেকে বেশি করে উন্মোচন করার সুযোগ থাকে। তবে আমার মনে হয়, এই রীতি পাঠকের কাছে বড় বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উত্তমপুরুষে এক একটি চরিত্র…
অনিন্দ্য: ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’-তে আছে।
সিরাজ: ‘রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র’-তে আমি ইচ্ছে করেই এটা করেছিলাম, চরিত্রগুলো যাতে নিজেদের একটু বেশি করে উন্মোচন করতে পারে।
অনিন্দ্য: তবে মানুষ নিজের চরিত্রকে নিজে ঠিক মতো বিশ্লেষণ করতে পারে না। এটা এই রীতির লিমিটেশন।
সিরাজ: লিমিটেশন আছে স্বীকার করি। সেজন্য আমি ওভাবে লেখার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি।
অনিন্দ্য: আপনাকে অনেক সময় বর্ণসচেতন লেখক বলে মনে হয়। গোড়ার দিকের গল্প ‘অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ’-এ বর্ণ-সচেতনতা দেখা গেছে। ‘অলীক মানুষ’ও বেশ বর্ণবহুল। শুধু সাদা-কালো নয়, নানাবর্ণের ঘনঘন উল্লেখ উপন্যাসের বর্ণণা অংশকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমি জানতে চাইছি, ‘অলীক মানুষ’-এ বর্ণসচেতনতা কি স্বাভাবিকভাবে এসেছে, নাকি নতুন ধরনের উপন্যাস লিখবেন বলে?

সিরাজ: ‘অলীক মানুষ’-এ এটা অন্যভাবে এসেছে। এর কারণ আমাদের দেশে বরাবরই ধর্মগুরু এক বিশেষ শ্রেণির মুখপাত্র। এখানে সৈয়দদের কথা বলছি। আমি আমার ছেলেদের নাম থেকে সৈয়দ বাদ দিয়েছি। এই পুরুষ পরম্পরা যেন কোথাও আলাদা করে রাখে মানুষকে। এটা কিন্তু ওদের প্রয়োজন ছিল। ঐ ওয়াহাবি মৌলানাকে ঘিরে এমন মিথ তৈরি হতে থাকল যে তিনি সেই মিথের জালে বন্দি হয়ে গেলেন। সে এক অসহায় অবস্থা। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘আমাকে সাদা জিনেরা শাহি তক্তে বসাইল। কিন্তু আমার হৃদয় মাটির আকাঙ্ক্ষী’। এই মিথের জালে মানুষের বন্দি হয়ে পড়া, সেই মিথকে ভাঙতে গেলেও ভাঙে না। ছেলে শফিউজ্জামানের ব্যাপারেও তাই হয়েছে। শফি যা করেছে তাতে সে জীবদ্দশায় মিথ হয়ে উঠেছে। আমরা জানি, আলেকজান্ডার তাঁর জীবদ্দশায় মিথ হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই – মিথ ভেঙ্গে সে আর বেরুতে পারে না। শফি খুনি, সে অ্যানার্কিস্ট। যখন দেখল রাজনৈতিক দলে গিয়ে কিছু হবে না, তখন যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানে সে নরহত্যা করে যাচ্ছে। ঘাতক প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে তার নামে মিথ সৃষ্টি হয়েছে বলে। একটা এপিসোডে বাইবেলের ঢঙে বলা আছে, সে একটা কালো অশ্বে চড়ে আসছে। চারদিকে চিৎকার করে গাছপালা, নদীর কাছ থেকে ‘স্বাধীনতা’, ‘স্বাধীনতা’ উচ্চারিত হত। এটা প্রকৃতির মতো স্বাধীন হওয়া। একটা গাছ যেভাবে স্বাধীন, নদী বয়ে চলেছে নিজের স্বাধীনতায়। এই স্বাধীনতার স্রোতই তার কাম্য। প্রকৃতির মধ্যে এই স্বাধীনতার স্রোত আমাকে খুব টানে। আমার ‘অগ্নিবলয়’ গল্পে এর উল্লেখ আছে। প্রকৃতি চাইছে স্বাধীনতা। সূর্যাস্ত হচ্ছে, আকাশে নক্ষত্র উঠছে। সেই অপার স্বাধীনতা, বাধা দেবার কেউ নেই। এই স্বাধীনতাবোধ প্রকৃতির মধ্যে গেলে টের পাওয়া যায়। রায়ট হবার পর আমি গ্রামের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, লিখেওছিলাম দেশ-এ, এখানে কোনও দাঙ্গাবাজ নেই, পুলিশ নেই, এখানে কাউকে বাধা দেবার কেউ নেই। কী বিশাল স্বাধীনতা আমার সামনে। মাঠের মধ্যে একা-নিজেকে সম্রাট মনে হচ্ছে। এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা আমাকে আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশি। মানুষের মধ্যে আমি সেটাই দেখতে চাই। সাম্যবাদের সঙ্গে, মার্কসিজমের সঙ্গে এই স্বাধীনতাবোধের কোনও পার্থক্য নেই। মার্কসও ঠিক এই স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন ব্যক্তির।
অনিন্দ্য: বদিউজ্জামান না শফিউজ্জামান – আপনি কাকে ‘অলীক মানুষ’ বলছেন?
সিরাজ: দু’জনেই, দু’দিক থেকে। বদিউজ্জামান ঈশ্বরিক মার্গে। উনি চাইছিলেন ইসলাম ধর্মকে যুক্তির ভিত্তিতে রাখতে। মানুষ সংযত জীবনযাপন করবে। ওঁর নিজস্ব যুক্তি ছিল। এই করতে গিয়ে উনি দেখলেন, সবাই ওঁকে পির ভাবছে। উনি নাকি জিনের সঙ্গে কথা বলেন, এটা ওটা করেন – এই সব গল্প রটছে। অনেক লোককে ঘিরেই এমন গল্প রটে, হিন্দু সাধুদের নিয়েও রটে থাকে; ফলে সেই লোকটির আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ থাকে না। যদি ফিরে আসতেও চায়, সেখানে আঘাত পায়। বদিউজ্জামান প্রথমে গিয়ে যে মেয়েটিকে দেখতে পেলেন, ব্রাহ্মণী নদীর ভাঙা সাঁকোর কাছে, তিনি ঐ শরীর দেখেই প্রেমে পড়েছিলেন। যে কোনও সচেতন মানুষ তা করতে পারে। পরবর্তীকালে মেয়েটিকে উনি বিয়ে করেন। মেয়েটিকে বিয়ে করায় ওঁর ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। কারণ ডাইনিবিদ্যা মেয়েটির আয়ত্ত, সে নিজের প্রবৃত্তি ছাড়বে না। ফলে বাধ্য হলেন তালাক দিতে, ওইভাবে নিজের মহত্ত্ব বজায় রাখলেন।
অনিন্দ্য: ছেলে শফি?
সিরাজ: ছেলে একেবারে তার বিপরীত। সে-ও মিথিক্যাল ম্যান। লোকের চোখে সে বিদ্রোহী চরিত্র।
অনিন্দ্য: ‘গিলগামেশ’ মহাকাব্যের নায়ক এক অত্যুগ্র প্যাশন, বিপুল বাসনায় আক্রান্ত। হিংসা ও হননে সে বারবার প্রবৃত্ত। কারণ তার ভিতরে কাজ করছে গভীরতর এক অতৃপ্তি। তার সঙ্গে শফিউজ্জামানের অ্যানার্কিস্ট প্রবণতার গভীর…
সিরাজ: ঠিকই বলেছেন, তেমন প্রবণতা আছে। ওটা আমার মনে ছিল। তলস্তয়ও আমার মনে হয় এক অর্থে অ্যানার্কিস্ট ছিলেন। উনি বলতেন, পেশি শক্তি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। অতএব রাষ্ট্র না-থাকাই বাঞ্ছনীয়। এদিক থেকে অ্যানার্কিজম আমার মধ্যেও কাজ করে। এর সঙ্গে প্রাকৃতিক স্বাধীনতার যোগ আছে।
অনিন্দ্য: ঘাতক প্রবৃত্তিও কি এর সঙ্গেই সম্পর্কিত?
সিরাজ: তাও আছে।
অনিন্দ্য: ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রই মানসিক বিকৃতির শিকার। ইকরাতুন, শফি, পান্না পাশোয়ারি, এমনকী বদিউজ্জামান। উপন্যাসটি যেন বিকৃত মানুষের মিছিল।
সিরাজ: খানিকটা তাই। এই বিকৃত মানুষগুলো শফিকে গড়তে, চরিত্রটিকে দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে। এদের স্নেহ-প্রেম পেলে সে ওরকম হত না। মানুষ একটা আশ্রয় চায়। মুশকিল হল, বাস্তবে সে প্রতিক্ষেত্রেই হেরে যাচ্ছে। রত্নময়ীকে সে চেয়েছিল, রত্নময়ীও তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করত। তবে সে দেখল মেয়েটি পূজারিণী হয়ে গেছে। এই চরিত্রগুলো স্বাভাবিক হলে শফিকে আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম না।
অনিন্দ্য: শফি যদি স্বাভাবিক পরিবেশ পেত- তাহলে অন্যরকম…
সিরাজ: আলাদা মানুষ হয়ে যেত।
অনিন্দ্য: শফিকে ওভাবে গড়ে তোলার জন্যই সচেতনভাবে…
সিরাজ: সচেতনভাবে নয়, এটা হয়েছে আমার অবচেতনে। আমি নিজেও তাই ভেবেছি। এসব তো ঠিক হচ্ছে না! কেমন যেন… কিন্তু আমি লিখতে লিখতে শেষের দিকে দেখলাম, এরকম না হলে শফি চরিত্রটি দরিয়ায় পড়ে যাবে। ছোটবেলায় সিতারা ডেকেছিল তাকে। তখন বয়স কম, যেতে পারেনি। ও যদি সিতারার সঙ্গেও চলে যেত, তাহলেও এমন পতন ঘটত না।
অনিন্দ্য: এরা প্রায় প্রত্যেকেই অ্যাবনর্মাল। একটা অসুস্থ পরিমন্ডল নিয়ে…
সিরাজ: এই বোধ আমার মধ্যে বরাবরই কাজ করে। এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি আমরা – যা ঠিক নর্মাল মানুষের বাসযোগ্য নয়। সবসময় অ্যাবনর্মালিটির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হয়।
অনিন্দ্য: আপনার এই প্রবণতা আমিও লক্ষ করেছি। ‘অলীক মানুষ’-এ ভাষা আঙ্গিক নিয়ে যে পরীক্ষা করছেন, সেটি কি পূর্ব- পরিকল্পিত? এই কাহিনিতে কোলাজ রীতি, সাধু-চলিত – দু’ধরনের গদ্য আছে – এটা কি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন?
সিরাজ: না, করিনি। ব্যাপার হল, সাত-আটটা চ্যাপ্টার লেখার পর আমি হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। বলে পাঠালাম, আমি অসুস্থ, লিখতে পারব না এই উপন্যাস। আসল কারণ, যেভাবে আমি উপন্যাসটাকে ধরতে চেয়েছি, সেভাবে যদি এগোই ন্যারেটিভ রীতিতে যেমন বিমল মিত্র বা অনেকেই লিখেছেন, সেই ধারায় লিখলে আমার হাজার পাতা লেগে যাবে। এদিকে সম্পাদক আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। যেভাবেই হোক লিখতে বললেন। আমার টেবিলে নানারকম বই সাজানো থাকে। একটা বই তুলে নিলাম, সেখানে একটা লাইন পেলাম। আমি সেটা থেকে নতুন চ্যাপ্টারের নাম দিলাম। এইভাবে লিখতে লিখতে দেখলাম, অতীত ভবিষ্যতে চলে আসছে।
অনিন্দ্য: টাইমের…
সিরাজ: টাইমের কন্টিউনিটি থাকছে না।

মতামত
আপনার মন্তব্য লিখুন
আপনার ইমেল গোপনীয় থাকবে।