এক বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতকার
লিখেছেন:অজয় বিশ্বাস
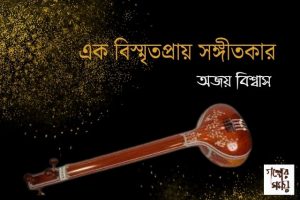
 [ মূল্যবান এই লেখাটি লেখা হয়েছিল অনেক আগেই, সেই আশির দশকে।সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুমতিক্রমে এই বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতকারের কথা প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল সেই সময়ের ‘দেশ’ পত্রিকার পাতায়।কিন্তু বিশেষ কারণে তা না হওয়ায় এতদিন লেখাটি অজান্তেই বাক্স বন্দি হয়ে পড়েছিল লেখকের কাছে। হঠাৎ তা মিলে যাওয়ায় লেখক তা সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছেন ‘গল্পের সময়’কে।]
[ মূল্যবান এই লেখাটি লেখা হয়েছিল অনেক আগেই, সেই আশির দশকে।সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুমতিক্রমে এই বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতকারের কথা প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল সেই সময়ের ‘দেশ’ পত্রিকার পাতায়।কিন্তু বিশেষ কারণে তা না হওয়ায় এতদিন লেখাটি অজান্তেই বাক্স বন্দি হয়ে পড়েছিল লেখকের কাছে। হঠাৎ তা মিলে যাওয়ায় লেখক তা সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছেন ‘গল্পের সময়’কে।]
১৯৩২ সালের গোড়ার দিকের কথা। সেই সময় দৈনিক সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন বের হচ্ছিল কিছু দিন ধরে। হেকিমী ওষুধের বিজ্ঞাপন। ‘ফিন যৌবন আয়েগা’ –এমন ওষুধ যা খেলে বৃদ্ধও ফিরে পাবে হারানো যৌবন! বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ফিরে পাওয়া সেই যৌবনের পেশী বহুল ছবি। সঙ্গে দিল্লির একটা ঠিকানা।
মেদিনীপুরের নিভৃত গ্রাম পঁচেটের সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যমণি বৃদ্ধ ওস্তাদের কাছে পৌঁছে গেল এই বিজ্ঞাপনের কথা। একশ’ পার করে আরও একটা গোটা যুগকেই চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যেতে দেখেছেন তিনি। এই বয়সেও শক্ত সমর্থ। কিন্তু তাহলে কি হবে যৌবন ফিরে পাওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল। হাতের কাছে এমন ওষুধ থাকতে তিনি বৃদ্ধ হয়ে থাকবেন! জ্ঞানেন্দ্রনন্দন, অনাদিনন্দনের মত এমন গুণী শিষ্য পেয়েছেন তাঁদের কাছে যৌবনের সেই দিনগুলির ঐশ্বর্য উজাড় করে দেবেন না তাও কি হয়?
ডাক পড়ল শিষ্যদের। ‘ইয়ে দাওয়া চাহিয়ে’। এ ওষুধ আমার চাই।
– ‘কিন্তু ওস্তাদজী এ সব ঠিক নয়। সব ঝুটা বাত!’
– ‘ক্যা তুমহি খুদ সচ বলতে হো? মুঝে ইয়ে দাওয়া চাহিয়ে।’
– ‘মগর ইসনে কোই ভী খতরা হো জায়ে তো?’
শিষ্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করে গুরুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করতে। কিন্তু বৃদ্ধ ওস্তাদের মাথায় তখন যৌবন ফিরে পাওয়ার নেশা। যৌবনের দিনগুলোতে সংগীত নিয়ে তো শুধু বেসাতিই করেছি। কাউকেই শিখাইনি কিছু। আজ যদি একবার সেই ফেলে আসা দিনগুলোর শক্তি হাতের মুঠোয় পাই তবে –।
– মুঝে দাওয়া চাহিয়ে। নহী তো খানা ছোড় দুঙ্গা!’
সত্যি সত্যি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিলেন। একদিন, দু’দিন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জেদের কাছে নতি স্বীকার করতেই হল। ওষুধের জন্য দিল্লিতে চিঠি গেল দেখে তবে তিনি জল গ্রহণ করলেন।
‘বুড়া মানুষ না খেয়ে মারা যাবে! বাধ্য হয়েই সেই ওষুধ আনতে রাজি হতে হল’ পঁচেটের জলসাঘরে বসে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনন্দন পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে সেই সময়ে পাড়ি জমাচ্ছিলেন। ওষুধ এল। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ছাড়ানো হল ভি পি পি। তিন শিশি। ‘ফিন যৌবন আয়েগা’। মাঝারী শিশিতে ভরা কালো রঙের আরক।
প্রথম দিনেই উৎসাহের আতিশয্যে এক বোতল আরক ঢকঢক করে খেয়ে ফেললেন ওস্তাদজী। এরপর দিন দুয়েক চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখালেও বেশ উৎফুল্লই মনে হল তাঁকে। ‘লেকিন জোয়ানী কঁহা?’ লম্বা চুলে চিকন কালো জেল্লা নেই, হাত মুখে চামড়াও তেমন টান টান হয় নি!
– ‘হাফিজান দুসরা বোতল লাও। সকাল বেলা নিয়ম মাফিক আফিং এর মৌতাত কাটতে না কাটতেই হুকুম হল মেয়ের প্রতি। হাফিজান ওস্তাদজীর পালিতা মেয়ে। কিন্তু বৃদ্ধ আব্বাজানের সেবাযত্নে হাফিজানের নিষ্ঠা আপন আত্মজার কাছ থেকেও মেলে না সবসময়।
– ‘লেকিন’ – একটু মৃদু আপত্তি জানাবার চেষ্টাও করেছিল সে। কিন্তু তাকে পাত্তা দেয় নি বৃদ্ধ। যৌবন ফিরে পাবার বাসনা তখন তাঁর সত্তাকে গ্রাস করেছে। শুরু হল হম্বিতম্বি, চেঁচামেচি। হাফিজানের পক্ষ সমর্থন করতে এসে অন্যেরাও গালমন্দ শুনলেন। বাধ্য হয়েই দ্বিতীয় বোতলটিও এগিয়ে দিতে হল।
একবারেই পুরো বোতলটা গলায় ঢেলে দিলেন বৃদ্ধ। সেদিনটা কাটল ওভাবেই। সন্ধ্যায় গানের আসরেও বসলেন। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি জড়িয়েই রইল। আসর জমল না।
পরের দিন সকাল থেকেই শরীর খারাপ হতে শুরু করল। জ্বর জ্বর ভাব। সেই সাথে দু একটা ফুস্কুরি দেখা দিল শরীরে। মুখ চোখও বেশ ফুলে গেল। খেলেনও না কিছু। এমনকি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেতেও আপত্তি জানালেন। আব্বাজানের শরীরের অবস্থা দেখে হাফিজান কান্নাকাটি শুরু করল। সেদিনও কাটল।
তারপর দিন সকাল হতেই হুকুম হল, ‘ঘোড়া লাও!’ ঘোড়া এল। প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ে খড়ুইতে যেতেন ওস্তাদজী। সঙ্গী হতেন জ্ঞানেন্দ্রনন্দন। সেদিনও সঙ্গী হলেন। ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার আগে দু’চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ‘মুঝে জানে দো। আউর ঘুমে গা নহী।’
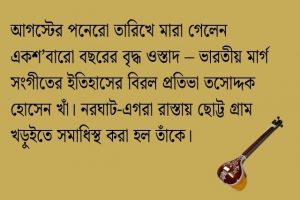
‘সেই চলে গেলেন ওস্তাদজী। এরপর দিন সাতেক বেঁচেছিলেন। একদিন সকালে নাক দিয়ে রক্ত পড়ল, ব্যস!’ জ্ঞানেন্দ্রনন্দনের বিষণ্ণ স্মৃতিচারণের শেষ পর্বটুকুতে বাতাস একটু ভারী ভারী হয়ে উঠল।
আগস্টের পনেরো তারিখে মারা গেলেন একশ’বারো বছরের বৃদ্ধ ওস্তাদ – ভারতীয় মার্গ সংগীতের ইতিহাসের বিরল প্রতিভা তসোদ্দক হোসেন খাঁ। নরঘাট-এগরা রাস্তায় ছোট্ট গ্রাম খড়ুইতে সমাধিস্থ করা হল তাঁকে।
আমার দুঃখ কালে খাঁ, তসোদ্দক হোসেন (তাজ খাঁর ভাগ্নে), আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ গোছের কোনও গায়ক বর্তমানে জীবিত নেই। – এখনকার শ্রোতাদের দূর্ভাগ্য বলবো।’ সুরসাধক সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণে কালে খাঁ কিংবা ফৈয়াজ খাঁয়ের মত সংগীত প্রতিভার সংগে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় ওস্তাদ তসোদ্দকের জীবন কিন্তু এক টুকরো বিস্মৃতিতেই ঢাকা রয়েছে এতকাল। সেই বিস্মৃতির আবরণ সরিয়ে তাঁর দীর্ঘ বিচিত্র জীবনচর্যার কাহিনী তেমন করে আলোয় আনেননি কোনও ইতিহাসকার। সেই অনধিত অধ্যায়ে রয়েছে টুকরো টুকরো কত বৈচিত্র্যের সমাহার—
লখনৌয়ের নবাব ওয়াজেদ আলি তখন কলকাতায়। নজরবন্দী। কিন্তু বন্দী হলেও সংগীত বিলাসী নবাবের জলসাঘর ভাঙে নি। লখনৌয়ের গোটা সংগীত দরবারটাই তিনি তুলে এনেছেন মেটেবুরুজে। এসেছেন একশ’একুশ জন সংগীত শিল্পী আর দু’জন নর্তকী। এরা ছাড়াও মেটেবুরুজের নবাবী মাইফিলে তখন সারা ভারতেরই সংগীত গুণীদের আনাগনা। পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ, প্যারে খাঁ, বাসিত খাঁ, কাশিম খাঁ, জাফর খাঁ, যদুভট্ট কে নেই তাঁদের মধ্যে? নানা ঘরানা, বহু সংগীত প্রতিভার মিলনক্ষেত্রে সংগীতের বিচিত্র বৈভব প্রতিদিন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।
এই গুরু সভাতেই মামা তাজ খাঁ ধামারীর সঙ্গে সুদূর রামপুর বেরিলী থেকে এসে উপস্থিত হলেন তরুণ সুর সাধক ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই সংগীত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিলেন তসোদ্দক।
সেই সংগীত আসরের টুকরো স্মৃতি তিনি এক দিন কথাচ্ছলেই বলেছিলেন তাঁর এক অনুরক্ত শিষ্যকে। ‘ক্যা জুলুস থা ওহ মাইফিল মে …’ সেই উজ্জ্বল আসরে তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে নবাব তাঁর বহুমূল্য শাল ছুঁড়ে দিয়ে সাবাশী জানিয়েছিলেন!
এরপরই নবাব অনুরক্ত হয়ে পড়েন তাঁর প্রতি। যতবারই যাবার কথা উঠেছে বাধা দিয়েছেন। এ আসর সে আসর ঘুরে আবার ফিরে যেতে হয়েছে মেটেবুরুজে। এরই মধ্যে ধ্রুপদ-ধামারিয়া তসোদ্দক আয়ত্ত্ব করেছেন খেয়ালের জটিলতম সুর রহস্য।
মেটেবুরুজে থাকার সময়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। নবাব বাড়ির আশেপাশে একটা লোককে প্রায়ই ঘোরাঘুরি করতে দেখতেন তসোদ্দক। উৎসুক ভাবে তাকিয়ে ত্থাকেন ওস্তাদদের যাতায়াতের পথের দিকে। মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করেন নামী ওস্তাদদের কন্ঠের সুর বিহার।
এক দিন, দু’ দিন, তিন দিন। এমনি করে কয়েকদিন দেখার পর একটু কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞেস করেন, ‘ক্যা মাংগতে হ্যায় আপ?’
সৌম্য দর্শন তরুণ ওস্তাদকে দেখে বুকে একটু ভরসা লাগে তাঁর, ‘অন্দর যানা’। লখনৌ, বেনারস, গোয়ালিয়র ভারতের বহু সংগীত সভায় গান শুনেছেন নামী-দামী ওস্তাদদের। তাঁর খুব ইচ্ছে নবাবের এই সুরের আসরে শ্রোতা হওয়া। ‘ক্যা আপ লে যাওগে না?’
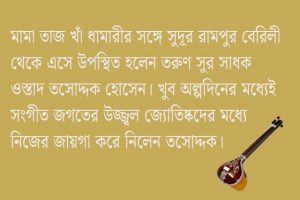
সংগীত পাগল মানুষটির আন্তরিক আকুতিতে মুগ্ধ হলেন তসোদ্দক। কিন্তু নবাবের সংগীতের আসরে তো সাধারণ শ্রোতার কোন প্রবেশাধিকার নেই। বললেন, তুমি কাল সন্ধ্যেবেলায় এসো। কোন একটা উপায় ভেবে রাখব। কোই ভি ফিকর শোচ কর রাখুঙ্গা।
সন্ধ্যেবেলায় তিনি আসতেই উপায় বাতলে দিলেন তসোদ্দক, ‘তুমি একটা তানপুরা কিনে আনো। ওস্তাদ সেজে ঢুকে যাবে। জামকুণ্ডাকা রইস ধামারি ওস্তাদ সুরেন্দ্রনাথ ভুইঞা।’ ওস্তাদের পরামর্শ শুনে জামকুণ্ডার সংগীত রসিক জমিদার সুরেন্দ্রনাথের তো চক্ষু চরক গাছ। রসিক শ্রোতা তিনি, তাই বলে নিজে তো ওস্তাদ নন।
সুরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরে আশ্বস্ত করেছিলেন তাঁকে, ‘উহ সব হামারা খ্যাল হ্যায়’। সব মনে আছে আমার । তুমি ওস্তাদ সেজে ঢুকে যাও। গান শুনো, নাচ দেখো। যখন তোমার পালা আসবে -। বাকিটুকু বলার আগেই আঁচ করে ফেলেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।
সেই দিনই সন্ধ্যায় নবাবী মাইফিলের বহিরাগত ওস্তাদদের লিসটে নাম উঠেছিল জামকুণ্ডার ওস্তাদের। তারপর কয়েকদিন নবাবী বদান্যতায় বেশ কয়েকটি সংগীত মুখর সন্ধ্যা কেটেছে। প্রতিটি সন্ধ্যার শেষেই কৃতজ্ঞতায় আনত হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। তারপর যেদিন তাঁর পালা এসেছে সেদিন আর তাঁকে দেখা যায় নি মেটেবুরুজের কাছাকাছি। ভোর রাতেই তানপুরা হাতে বেরিয়ে ওস্তাদজী নাকি আর ফেরেন নি!
সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তারপরেও দেখা হয়েছিল তসোদ্দক হোসেনের। সেও এক উৎসবের আসরে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ওস্তাদী জীবনের আর এক অধ্যায়। সে কাহিনী আরও কিছুকাল পরের।
তসোদ্দক হোসেনের বাবা মহম্মদ হোসেন ছিলেন রবাবী। কিন্তু বাবার কাছে সুর শিক্ষার কোন সুযোগ মেলে নি তাঁর। মহম্মদ হোসেন দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। মামা তাজ খাঁর কাছে তাঁর সংগীত শিক্ষা। ধ্রুপদ ধামারের শিল্পী হিসেবে ওস্তাদ তাজ খাঁ ছিলেন সে যুগের কিংবদন্তী। মেটেবুরুজের শাহী মাইফিলে তাজ খাঁর উপস্থিতি বর্ণণা প্রসঙ্গে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ‘বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি’র পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘… সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমাণ্য গায়ক তাজ খাঁ এঁদের মধ্যে ছিলেন। তিনি সভায় এলেই অন্য গুণীরা ‘ওস্তাদকা আওলাদ (গুরু বংশ) বলে উঠে দাঁড়াতেন… ।’
বাবার সঙ্গ পান নি তসোদ্দক, মানুষ হয়েছেন মামার কাছে। তবে কিতাবী পড়াশোনার দিকটি তেমন জোরদার ছিল না কোনদিনই। সংগীতে দুরূহ তাল, লয়, মাত্রা সহজাত প্রতিভা দিয়ে আত্মসাৎ করতেন। নিজের নামটিও সই করতে পারতেন না। পারতেন শুধু এক দুই তিন … করে কুড়ি পর্যন্ত গুণতে। নিজেকে প্রায়ই ‘অনপড়’ বলতেন। সে বলায় এতটুকু গ্লানির চিহ্ন ছিল না কোথাও।

১৮৮৭ সালে মারা গেলেন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। ভেঙে গেল মেটেবুরুজের কিংবদন্তীর সংগীতের আসর। কলকাতায় মার্গ সংগীত চর্চায় যে জোয়ার এসেছিল, এই মৃত্যু তাতে ভাঁটার টান ধরিয়ে দিল। ভাঙা দরবার ছেড়ে শিল্পীরা ছড়িয়ে গেলেন ভারতের বিভিন্ন রাজ দরবার কিংবা নবাবী পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধানে। ঠিক যেমন করে একদিন দিল্লির শাহী দরবার ছেড়ে সংগীত গুণীরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে।
দরবার ভাঙলো। বাসিত খাঁ গেলেন গয়ায়। তার আগেই কাশিম খাঁ গেছেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্র মাণিক্যের দরবারে। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সংগীতাচার্য যদু ভট্টের। সেই পরিচয়ের চিত্তাকর্ষক বর্ণণা শুনিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সে কাহিনী এখনই নয়।
মেটেবুরুজের সোনালী দিনগুলিতে যখন ধূসর ছায়া ঘন হচ্ছে সে সময়েই নেপাল রাজ দরবারের সংগীত সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ওস্তাদ তাজ খাঁ। এতদিন যান নি। শাহী মাইফিল যখন পুরোপুরি ভেঙে গেল ভাগ্নে তসোদ্দকের সঙ্গে তিনি পাড়ি জমালেন নেপালে। সেই দরবারে তখন রয়েছেন আরও কয়েকজন গুণী কন্ঠশিল্পী ও সেতারী রামসেবক মিশ্র, সরোদিয়া নিয়ামতুল্লা, ও মুরাদ আলি খাঁ। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ধ্রুপদীয়া তাজ খাঁ এবং তসোদ্দক। তসোদ্দক যে ইতিমধ্যে খেয়াল শিখেছেন তা তো আগেই বলেছি।
নেপালে থাকতে থাকতেই তসোদ্দকের কাছে এল কাশী রাজসভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। বেনারস যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন তিনি। সেই কবে ঘর ছেড়েছেন মামার সঙ্গে। এতগুলো বছর তাঁকে পরম স্নেহে আগলে রেখেছেন তাজ খাঁ। শৈশবে পিতৃহারা এই একমাত্র ভাগ্নের প্রতি অসীম মমত্ব তাঁর।
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিদায় নিলেন তসোদ্দক। শুরু হল হিন্দুস্থানের এক নবীন ওস্তাদের একক পরিক্রমা। মামার সঙ্গে আসর থেকে আসরে ঘোরার সময়েই অবশ্য সব ঠাট-ঠমক, আদব কায়দা রপ্ত হয়ে গেছে। নেপাল থেকে তসোদ্দক পৌঁছে গেলেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বেনারসে। অভ্যর্থনা পেলেন আন্তরিক। ওস্তাদ বাসিত খাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেন খাঁ। রাজ-দরবারের সংগীতসভায় তখন ছয় উজ্জ্বল প্রতিভার মহার্ঘ সমাবেশ – মিঞা তান সেনের পুত্র বংশের শেষ সংগীত রত্ন মহম্মদ আলি খাঁ, স্বরোদিয়া গফর খাঁ, মুতুক মিঞা, আবু ধামারী, পশ্চিম ভারতীয় সেনী ঘরানার ধ্রুপদীয়া দৌলা খাঁ, ওস্তাদ রসুল বক্স।
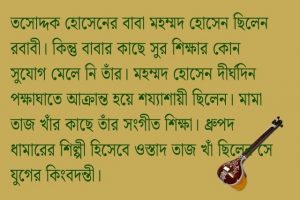
ওস্তাদ তোসাদ্দক হোসেন বেনারস রাজ দরবারে ছিলেন বছর দশেক। বেনারস থাকার সময়ে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যেত রামপুর-বেরিলির গ্রামের বাড়ির কথা। বিবি-বাচ্চা। কত বড় হয়ে গেছে বাচ্চাটা? নির্ঘাৎ জোয়ানী এসে গেছে। শাদিউদি ভী হো সকতা! অনেক চেষ্টা করেও ছোট্ট ছেলেটার জোয়ান মুখ মনে করতে পারলেন না। চোখের জলে ধূসর হয়ে যেত দৃষ্টি, স্মৃতি। সেই কবে মামার হাত ধরে ঘর ছেড়েছেন। শাদি দিয়েছিলেন মামাই। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে ঘর গেরস্থালীও চলেছে। ছেলে হতেই একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বিবি-বাচ্চা না থাকলে ঘরের টান থাকবে না ওস্তাদ বাওরা হয়ে যাবে। ইতনি হাসিন এ নশাঁ!
‘তসদোসক তুনে বাওরা হো গ্যয়া ক্যা?’ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে তখন জ্যোৎস্না আর জলে মাখামাখি। ‘লেকিন উন দোনো ইনসান কী ক্যা গুস্থাকি?’ কিন্তু ওরা কী দোষ করল? ব্যস পরের দিনই বেনারস ছাড়লেন তসোদ্দক। সঙ্গে জিনিসপত্র লটবহর। বুকের কাছে ধরা মখমলের কাপড়ে মোড়া তানপুরা। রামপুর-বেরিলির সেই গ্রাম, সেই ঘর এতদিন সুরের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষটাকে টানছে। কত স্বপ্ন, কত কল্পনা। কিতনি খোয়াব দেখা থা ম্যায়নে! সেই স্বপ্নের টানে চলতে চলতে…
‘উস্তাদজী আজহি লৌট হ্যায় ক্যা?’ গ্রামে ঢোকার মুখে সন্ধ্যার আলো আঁধারীতে তাঁকে চিনতে কষ্ট হয়নি মাস্টারজীর। মাইলখানেক গেলেই পৌঁছে যাবেন ঘরে। বড় অদ্ভুত অনুরোধ করে বসেন তিনি, আজ রাত কো মেরা গরীবখানা মে ঠরে যাইয়ে না। ইতনি আন্ধেরা হয়।
– ‘ইয়ে আপকাহিঘর হ্যয়। লেকিন… ‘ আবার পায়ে পায়ে চলেছেন ঘরের টানে। রাস্তায় মুখোমুখি হয়েছেন আরও কয়েকজনের। তাঁকে দেখে একটু চমকেই উঠেছেন তাঁরা। তিনি কিন্তু থামেন নি।
সন্ধ্যে তখন ঘন হয়ে রাত। একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে … ঘরের দাওয়ার আলোর দু’একটা টুকরো চলকে এসে সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠছে। অনেক বদলে গেছে তাঁর দেখা সেই পুরনো গ্রাম। দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা করুণ দেহাতী সুর … ঠিক যেন বেহাগের মোচড়ের মত হৃদয় ছোঁয়া।
বাধা পেলেন আবারও। এবার তাঁর পরিচিত গ্রাম সম্পর্কে চাচেরা ভাই এসে দাঁড়ালেন সামনে । সঙ্গে আরও জনা দুয়েক। মনে হল তাঁর ঘর ফেরার খবর এঁরা আগেই পেয়েছেন। কুশল বিনিময়ের পর টুকটাক দুয়েকটা কথাবার্তা শেষ করে ঘরের পথে পা বাড়াতে যাবেন ঠিক এমন সময়েই অদ্ভুত অনুরোধ করলেন তাঁর ভাই,’আজ রাত য়ঁহা ঠর যা তসদোক। কিতনি সাল বাদ মে তম সে মিলি। কাল সুবে ঘর যানা’।
– এ তুম ক্যা বোলতে হো রহিম ভাইয়া! পহলে তো উন দোনো সে মিলনা চাহিয়ে। দুস্রা কোই রোজ তুমহারে য়ঁহা … কথা শেষ না করেই আবার চলতে শুরু করেছেন। এক টুকরো সন্দেহের দোলাচলে দুলছে তাঁর মন। এরা এমন করে তাঁকে আটকাতে চাইছে কেন?
ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে একটু খটকাই লাগে । চারদিক শুনশান। অন্ধকার। ঘরে কি আলোও জ্বালে নি? ওরা কি কেউ নেই? কোথায় গেল? চিন্তার ঝড় বইছে মনের গভীরে। দ্রুত হয়েছে পায়ের গতি। বুকের কাছে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছেন তানপুরা।
ঘরের কাছে যেতেই খোলা দরজার ভেতর থেকে একটা কুকুর ছিটকে বেড়িয়ে এসে এক ছুটে অন্ধকারে মিশে গেছে। খাঁ খাঁ অন্ধকারে ঢাকা শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে একটা শব্দও বের হয় নি তাঁর মুখ দিয়ে। চারপাশে জড়ো হওয়া প্রতিবেশীদের মুখের কথার টুকরো বলে দিয়েছে দিন সাতেক আগের এক মর্মান্তিক দিনের ইতিবৃত্ত। একই দিনে কলেরায় মারা গেছেন মা আর ছেলে। ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেনের জলুস দেখার জন্য সাতটা দিনও সময় দেন নি।
শোকস্তব্ধ তসোদ্দর কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে এই স্মৃতির পথ ধরে সময় ডিঙোতে ডিঙোতে তা আর মনে করতে পারেন নি।শুধু মনে আছে বুকের কাছে সেই তানপুরাকে আরও গভীর করে জড়িয়ে ধরে সোজা চলতে শুরু করেছিলেন। পিছনে পড়েছিল ঘর, প্রতিবেশী, জিনিসপত্র, লটবহর। আর কতকগুলো সোনালী দিনের স্মৃতি।
– কি নাম রেখেছিলে ছেলের?
– উসসে আজ ক্যা ফায়দা? মেরে বাচ্চা, মেরে লাল …… চোখের জলে সিক্ত হয়েছেন বৃদ্ধ তসোদ্দক।
– উসকে বাদ ওস্তাদজী উসকে বাদ …?

– ফির তো চলনা শুরু কিয়া। চলতে চলতে এক নদীর ধারে গভীর জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গেলেন। ওখানে পৌঁছেই কানে ভেসে এল এক মধুর সংগীতের সুর। বিধ্বস্ত মনের উপর দিয়ে যেন এক ঝলক শান্তির বাতাস বয়ে গেল। এত বছর এত আসরে ঘুরেছেন কই কোথাও তো এমন মধুর সুর শোনেন নি! যত শোনেন ততই শান্ত হয়ে আসে মন। শব্দের উৎসের দিকে পায়ে পায়ে এগোতে থাকেন তিনি।
কিছু দূর এগোবার পরই তাঁর দেখা পান তিনি। গাছের তলায় বসে এক সৌম্য সন্ন্যাসী মধুর কন্ঠে ওঁকার সংগীত করছেন। সেই সুরের মাধুর্যে মুগ্ধ তসোদ্দকের মনে হয় তাঁর এত দিনের সাধনা আর চর্চা কত ম্লান, কত অর্থহীন! পায়ে লুটিয়ে পড়ে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করেন,তিনি তাঁর শিষ্য হতে চান।
তসোদ্দকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘ঠিক হ্যায় বেটা, তুম নাহাকে আও।’
স্নান করে ফিরে এসে আর তাঁর দেখা পান নি তসোদ্দক। শুধু তাঁর উপস্থিতির দু’টি চিহ্ন পড়েছিল সেখানে!
‘দিনভর ঢুঁনডা। লেকিন উন মহাজন সে ফির মিলনে নহী সকা!’ আর তাঁর দেখা মেলে নি। কিন্তু মনের ঝড় তাঁর থেমে গেছে পুরোপুরিই। দারা-পুত্র হারাবার শোক থিতিয়ে গেছে বুকের গভীরে!
‘এই কাহিনী যখন শোনাতেন তখন তাঁর মুখে আশ্চর্য এক প্রশান্তি ফুটে উঠত। বেশ কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকতেন। মনে হত কিসের যেন ধ্যানে বুড়া মানুষটা ডুবে আছে। আমরা উঠে আসতাম চুপি চুপি …।’
ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেন আবার ফিরে এলেন কলকাতায়।মেটেবুরুজের সুরসভা স্তব্ধ হয়েছে বছর তেরো আগেই।ছন্নছাড়া কলকাতায় মন বসল না তাঁর।১৯০১ সালে চলে এলেন মেদিনীপুরে।মার্গ সংগীতের একটা মহৎ পরিবেশ তখন গড়ে উঠেছে সেখানে। পঁচেটের চৌধুরী পরিবার, মহিষাদলের দাস ও নাড়াজোলের খান পরিবারে তখন সংগীতের আসরে নতুন জোয়ার এসেছে। এঁরা যে শুধু মার্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয়, পারিবারিক চর্চার ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি থাকায় এই সাংগিতীক পরিমণ্ডলে ভিন্নতর মাত্রা সংযোজিত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তখন নামী কলাকারেরা আসছেন। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, বদল খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, ককুভ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও , শ্রীজান, গওহর জান, বামাচরণ ভট্টাচার্য, যদু রায়, মসিদ খাঁ, হায়দরী বাই, ফকির বক্স কত নাম কত বিচিত্র সুরস্রস্টাদের আনাগোনা। কখনও দোল-দুর্গোৎসব-রাসে, কখনও বা পারিবারিক জলসায় খুলে যাচ্ছে সুরের ঝর্ণা ধারা, পিলু-বেহাগ-মাড়োয়া-বিলাবল, সেতার-স্বরোদ-খুরবাহার-পাখোয়াজে, ঠাট-ঠমক-তান-আলাপ-বোলের বোলবোলাতে মেদিনীপুরের বাতাসে তখন সুরের আমেজ। আসা-যাওয়া, শোনা আর শোনানোর মধ্যে দিয়ে মার্গ সংগীতের বিভিন্ন ধারা-ঘরানার মুক্তবেণী রচনা হচ্ছে প্রতিদিন।
সুরের আসরে এসে তসোদ্দক ফিরে পেলেন নিজেকে। কলকাতার ভাঙা আসরের বেদনাও ভুলে গেলেন। পারিবারিক শোকের গভীর ক্ষতের উপর প্রলেপ বুলিয়ে দিল বন্ধু ধ্রুপদিয়া আমীর খাঁ।আমীর খাঁর বাড়িতেই তাঁর অস্থায়ী আস্থানা ছিল। এই সময়ে তিনি শিষ্য হিসেবে পেয়েছেন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজেস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জমিদার যামিনী মল্লিক এবং প্রবোধচন্দ্র দত্তকে। পরিচয়ের সূত্র বিস্তৃত হয়েছে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। সংগীত রসিক যাদুগোপাল বাবুর বাড়িতে তখন প্রায় প্রতিদিনই গানের আসর বসত…
‘মেদিনীপুর এসে আমার মন বেঁচে থাকত সুবিখ্যাত গায়ক তস্দিক হোসেন ও আমার পিতার বন্ধু ডা. রূপনারায়ণ দত্তকে নিয়ে। তস্দিক হোসেন তাজ খাঁ নামক তানসেন বংশের সুবিখ্যাত গায়কের ভাগ্নে। ১৮৫৬ সালে লক্ষ্মৌয়ের নবাব ওয়াজেদ আলীকে কলকাতার নিকট মেটেবুরুজে নজরবন্দী করে রাখে ইংরেজ। তাঁর সঙ্গে একশ জন গায়ক-গায়িকা আসেন ফলে কলকাতায় বাংলায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রচলন বৃদ্ধি পায়। সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বমান্য গায়ক তাজ খাঁ এদের মধ্যে ছিলেন। … আমি গানের চেয়ে তস্দিক হোসেনের কাছে নেপালের গল্প শুনতে ভালবাসতাম। তস্দিক হোসেন আরও বলতেন, – বাঁচতে হলে মরদের মতো বাঁচা দরকার। সর্বস্ব গিয়ে যদি একটুখানি কুঁড়ে বাঁধার জায়গা স্বাধীনতা থাকে, তাহলে সেটুকুই স্বর্গের চেয়ে মহত্তর।’
যাদুগোপালবাবুর বাড়ির সংগীতের আসর যে বিপ্লববাদী আন্দোলনের নেতাদের মেলামেশার একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্র ছিল সে ভাবনায় বোধহয় অতিরঞ্জন নেই। অশীতিপর বৃদ্ধ তসোদ্দক হোসেনও যে সেই স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তা তো যাদুগোপালবাবুর মন্তব্যেই স্পষ্ট। কিন্তু এই একাত্মতা যাদের ভাল লাগার কথা নয় তাদের নজরও বরাবরই অনুসরণ করেছে তাঁকে। পুলিশের নজরদারী থেকে সরে থাকতে পারেন নি তিনি। প্রয়োজন ছিল শুধু অজুহাতের।
সেই অজুহাত মিলতেও দেরি হল না। ১৯০৮ সালের ৩১ আগস্ট আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজসাক্ষ্মী নরেন গোঁসাই মারা গেলেন দুই বিপ্লবী সত্যেন-কানাইলালের গুলিতে। পুলিশী তাণ্ডবের ঝড়ও ওই দিনই বয়ে গেল মেদিনীপুরের ঊপর দিয়ে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র মেদিনীপুরে গ্রেফতার হলেন সতাধিক। নাড়াজোলের জমিদার নরেন্দ্রলাল খান, ‘মেদিনী বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ, জমিদার যামিনী মল্লিক, বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত অনেকেই জড়িয়ে পড়লেন বোমার মামলায়। আর এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য খাঁ সাহেবের নামও সন্দেহভাজনের তালিকায় উঠে গেল। শুরু হল পুলিশী আনাগোনা।
কে জানে কবে হাতে ধরিয়ে দেবে গ্রেফতারি পরোয়ানা। আশি পেরিয়ে এসে জেলের ঘানি টানার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ঢের ভাল। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। একদিন রাতে সবার অলক্ষ্যে মেদিনীপুর ছাড়লেন। সঙ্গে দুই সঙ্গী আমীর খাঁ এবং গায়ক গোলাম রসুল। আবার শুরু অনির্দেশ্য চলা। রেল গাড়িতে চেপে মেদিনীপুরের সীমানা ডিঙিয়ে ওড়িশায়। সামন্ত রাজাদের আসরে আসরে গান গেয়ে ফেরা। কিন্তু থিতু হতে পারলেন না কোথাও। প্রায় বছর খানেক এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এলেন মেদিনীপুরে।
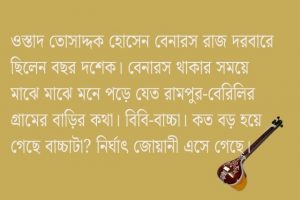
মেদিনীপুর তখন অনেকটাই শান্ত। আমীর খাঁর বাড়িতে কাটল আরও কিছুদিন। এই সময় আমন্ত্রণ এল বলধার জমিদার নরেন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে। ওস্তাদ তসোদ্দক রওনা হয়ে গেলেন একরকম দ্বিধাহীন ভাবেই। ঢাকার সংগীত জগতের কেন্দ্রেই তখন রয়েছেন বিখ্যাত খেয়াল গায়ক গুলাম আলি খাঁ এবং তাঁর আত্মীয় লাহোরের ওস্তাদ কালে খাঁ প্রমুখ গুণীজন।
ঢাকাতে থাকার দিনগুলিতে তিনি শিষ্য হিসেবে পেয়েছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে। পরিচয় হয়েছিল তবলিয়া আতা হোসেনের সঙ্গেও। আলাউদ্দীনকে তিনি শিখিয়েছিলেন বাহার তেলানা, বিলাসখানি তোড়ি, কাড়ানা প্রভৃতি বেশ কয়েকটি রাগ। কখনও শিক্ষকতা আর কখনও মাইফিল জমিয়ে ঢাকার দিনগুলো বেশ কাটছিল। কিন্তু অলক্ষ্য বিহারী বিধাতা পুরুষের ইচ্ছা বোধহয় অন্যরকম ছিল।
ঢাকাতে হঠাৎ একদিন গিয়ে পৌঁছালো এক দুঃসংবাদ। পরম সুহৃৎ আমীর খাঁর এন্তেকাল হয়েছে। খবর পেয়ে আর দেরি করেন নি তসোদ্দক হোসেন। ফিরে এলেন মেদিনীপুরে। সময়টা ১৯১৬ সাল।
ফিরে এসেই জীবনের আর এক রূপ চোখে পড়ল তাঁর। আমীর খাঁর বিধবা বেগম আর শিশু পুত্র কবীরকে নিয়ে জড়িয়ে পড়লেন জটিলতর সাংসারিক আবর্তে। নতুন করে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেলেন। সব সংকট মেটাতে বৃদ্ধ বয়সে নিকা করলেন বন্ধুপত্নীকে। কবীরকে দিলেন নিবিড় অপত্য স্নেহ।
জামকুণ্ডার সেই সংগীত রসিক জমিদার সুরেন্দ্রনাথ ভুইঞাকে মনে আছে নিশ্চয়ই। সেই নকল ওস্তাদ সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্য করে আসর জামকুণ্ডায়। সে আসরে আমন্ত্রিত সুকন্ঠী ধ্রূপদীয়া হায়দরী বাঈ, আলরাখী বাঈ, পাখোয়াজী ফকির বক্স। আমন্ত্রণ পেয়েছেন ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেনও। মেটেবুরুজের সেই দরবারী আসরের স্মৃতি সুরেন্দ্রনাথ ভোলেন কি করে? শুধু আমন্ত্রণ নয়, লাখ টাকার আনন্দ উৎসবে তিনি ওস্তাদজীকে নিয়ে এলেন মেদিনীপুর গিয়ে।
লাখ টাকার উৎসব। শুনতে অবাক লাগলে ও জাকজমক আর জৌলুসের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করাটা প্রায় রীতিতেই পরিণত হয়েছে। জলসা ঘরে ঝাড়বাতিতে রামধনুর রোশনাই। রোশন চৌকিতে অবিরাম সানাই। গোটা জমিদার বাড়িতে নতুন সাজ। আতসবাজির জলুস। গোলাপ জল- আতরের খুশবুর সঙ্গে মোগলাই খানার গন্ধ মিলেমিশে সে এক এলাহী কাণ্ড! হাতির উপর হাওদা চাপিয়ে কিংবা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে, পালকী চেপে আমন্ত্রিত রাজা-জমিদাররা আসছেন। বাতাস ভরে যাচ্ছে আতরের মিষ্টি গন্ধে। খস্, গুলাব, জুঁই, চামেলি কত ফুলের নির্যাস।।
জামকুণ্ডার মত ছোট খাটো জমিদারের এই বিপুল বৈভবে কিঞ্চিৎ খটকা যে লাগতো না কারো মনে তাও নয়! যারা সোজা পথে ভাবনা চিন্তা করতেন, তাঁদের ধারণা এই বিলাসের কারণ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান লাভের প্রকাশ। কিন্তু মূল রহস্য ছিল অন্যত্র ।
কয়েক পুরুষ ধরেই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটছে ভুইঞা পরিবারে। পুত্র নাবালক থাকার সময়েই মারা যাচ্ছেন পিতা। জমিদারীর দায়দায়িত্ব সবই চলে যাচ্ছে কোরট অব ওয়ারডসের হাতে। তাঁরাই নাবালক জমিদারের সাবালক হয়ে ওঠার আগের দিন পর্যন্ত সামলাচ্ছেন সবকিছুই। এমনকি পুরনো ধারদেনাও শোধ করছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে।
এ ঘটনা নজর এড়ায়নি জনৈক বুদ্ধিমান জমিদারের। অত্যন্ত সহজভাবেই তিনি শুরু করেছেন ‘ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ’ নীতি। ঋণ যা হবে তা পরিশোধের দায়িত্ব ত ও সরকারেরই । সুতরাং।
সুতরাং অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই একটু বেশি বয়সে হওয়া পুত্রের অন্নপ্রাশনের বেলাতেও যে সুরেন্দ্রনাথ মহাজনপন্থা অবলম্বন করবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপলেও বিলাসের আয়োজনে নবাবী জলুসকেও ম্লান করে দেওয়ার একটা প্রবণতা ছিল। কিন্তু এরপরের ব্যাপারটুকু একটু অন্যরকম হয়েছিল।
মানুষের হিসেব নিকেশের সঙ্গে বিধাতার ইচ্ছের মিলের চেয়ে গরমিল মাঝেমধ্যে বড় বেশি প্রকট হয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথের বেলাতেও তাই-ই হয়েছিল। নাবালক পুত্র আর জমিদারী ধারদেনা কোরট অব ওয়ারডের হাতে জমা দিয়ে তিনি যে নিশ্চিন্ত মনে ইহলোক ছাড়বেন তা আর হয়ে ওঠে নি! সুতরাং।সে সবই ভবিষ্যতের ব্যাপার।
বিষণ্ণ ভবিষ্যতের কথা থাক। আসুন সুরের আসরে। হায়দরী বাঈয়ের গান শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তার সুরের আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে। আফিমের কালো ডেলা মুখে দিয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিলেন খাঁ সাহেব। মাঝে মাঝে তদগতভাবেই সাবাশী জানিয়েছেন হায়দরীকে। এমনি করে গভীর হয়েছে রাত। এক আঁজলা রূপোলী তারা কে যেন কখন ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশ জুড়ে। ঝাড়ের বাতি উসকে দিয়ে আরও রঙদার করা হয়েছে। মিঠে তামাকের একটা হালকা গন্ধ থমকে আছে।
সবশেষে উঠলেন খাঁ সাহেব। ধ্রুপদ নয় খেয়াল ধরলেন। রাগ মালকোষ, বিলম্বিত এক তাল। ‘… লাগি রাহে আলি তেরে নাম কি আশা’ মালকোষের রূপটি যেন একটু একটু করে খুলতে লাগল। স্থায়ী-অন্তরা-আভোগ-সঞ্চারীতে ঘণ্টা চারেক মন্ত্রমুগ্ধ প্রহর কাটল। হেমন্তের শেষ রাতে সমঝদার শ্রোতাদের সামনে শান্ত গম্ভীর ‘বীরৈধূর্তা বৈরিকপালামালা’ মোহনরূপটি সুরের বিচিত্র বিন্যাসে ফুটে উঠল। এতটুকু চঞ্চলতা নেই, হাতের মুদ্রায় সুরের ভারসাম্য, সেখানেও শান্ত সমাহিত ভাব। সংগীত নয় আত্মমগ্ন সাধকের সুরের অঞ্জলি!
খাঁ সাহেবের নিবেদনের আন্তরিক আকুতি ছুঁয়ে গেল আর এক রসিক শ্রোতার হৃদয়ে। রামপুরের মার্গ সংগীতের সোনার খনি থেকে যিনি সঞ্চয় করে এনেছেন সেনী ঘরানার ঐশ্বর্য, পঁচেটগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ-র প্রথম পূর্বাঞ্চলীয় শিষ্য। সে ইতিহাসের রোমাঞ্চ এখনও মার্গসংগীতের প্রক্ষিপ্ত ইতিহাসে অধরাই রয়ে গেছে। সেই সংগীত চর্চা আর চর্যায় কাহিনী এই পর্বে নয়।
ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেনের সঙ্গে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ-র শিষ্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দনের এই পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। রাসযাত্রা আর দোল-ঝুলনের গানের আসরের টানে খাঁ সাহেব প্রায়ই এসেছেন পঁচেটগড়ে। চারদিকে সবুজ গাছগাছালি সবুজ শান্ত সমারোহের মধ্যগড়-হাবেলি, মন্দিরে সন্ধ্যারতির অপার্থিব পরিবেশ তার মনের গভীরে একটু একটু করে ডালপালার শিকড় ছড়িয়েছে।
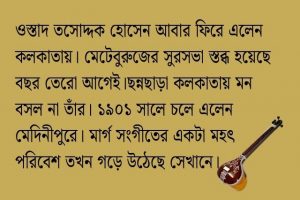
পঁচেটগড়ের জলসাঘরকে সাময়িক সংগীত বিলাসের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে মার্গ সংগীতের চর্চা ও শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলার একটা ইচ্ছা যাদবেন্দ্রনন্দনের মনের গভীরে লুকিয়েছিল বহুদিন। সংগীত অনুরাগী চৌধুরী পরিবারে বহু গুণিজনই এসেছেন নানা সময়ে। শিক্ষক হিসেবে তিনি তো সংগীতাচার্য যদু ভট্টকেও পেয়েছেন। কিন্তু পরিবারের গণ্ডী নয়, তাঁর সংকল্প রূপায়ণের জন্য তিনি চেয়েছেন স্থায়ীভাবে কয়েকজন প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞকে। রাজি হয়েছেন পাখোয়াজী ফকির বক্স, রাজি হলেন ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেনও। কলকাতায় প্লেগ মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় হায়দরী বাঈও চলে এসেছেন পঁচেটগড়ে। শুরু হল সুর-সভা।
সেই এসেছিলেন খাঁ সাহেব আর ফিরে যাননি। প্রতিদিন চার টাকা করে খোরাকি পেতেন। আর পেয়েছিলেন আঠারো বিঘা জমির জায়গীর। খেয়াল শেখাতেন তিনি যাদবেন্দ্রনন্দনের পুত্র অনাদিনন্দন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনন্দনকে। আরও দু’জন শিক্ষার্থী ছিলেন পুলিনবিহারী অগস্তী ও কৃত্তিবাস দাস।
‘বড় মেজাজী লোক ছিলেন খাঁ সাহেব। মুখও চলত খুব। গালাগাল দিতেন। একদিন হয়েছে কি, মিঞা কি মল্লার শেখাচ্ছেন। সন্ধ্যে বেলায় বসেছি রাত দশটা বেজে গেল কিন্তু কিছুতেই আর তাঁর মন পাই না। শেষে বিরক্ত হয়ে লাথি মেরে দিলেন! সেই বুড়া বয়সেও কি জোর ঠ্যাঙে!’
‘নিজে যখন গাইতেন তখন একেবারে একাত্ম হয়ে যেতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে যে কেটে যেত! আহা কি গলা! ‘ বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনন্দন সড়ক ধরে পিছু হাঁটেন, গুণগুণিয়ে ওঠেন …
কৌন যাত ব্রজ মে
দধি বেচনে
রঙদারী শাড়ি হো
চুনরিয়া…
খাঁ সাহেব গাইতেন পিলু রাগের এই হোরির গান! কত গান! ক’টা বলব,…
… হোরি খেলে নন্দলাল
ক্যা লালে লাল পর
উড়ন্ত গুলাল…’
জলসা ঘরের টিমটিমে হ্যারিকেনের ম্লান আলোর হাত ধরে আত্মমগ্ন বৃদ্ধের সুরের জোয়ারী ছড়িয়ে যায় বাইরের অন্ধকারে। যেখানে একদিন ঢেউ তুলেছে গুরু ওস্তাদ তসোদ্দক হোসেনের সুরের যাদু!
‘দু’বেলাই প্রসাদ খেতেন। প্রণামও করতেন। ধর্মের কোনও গোঁড়ামি ছিল না তাঁর মধ্যে। আমাদের পরিবারেও নয়। গানের আসরে বসলে খাঁ সাহেব অন্য মানুষ। কিন্তু এমনি সময়ে একেবারে ছেলে মানুষ। একশ’দশ বছরের বুড়া বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে দুলে দুলে হাত তালি দিয়ে গান গাইছেন, খুনসুটি করছেন…
‘… বাজে তা তা তায়
নাতনি তেরে দেখে দেখে
হামার হাসি পায়…’
টুকরো টুকরো কথা গেঁথে গেঁথে স্মৃতির মালা সাজাচ্ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনন্দন। ‘খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর কতকগুলো অদ্ভুত খেয়াল চাপত। আফিম তো খেতেনই। একটু আধটু নয়, এই অ্যাত্তো বড় এক দলা। আফিম মুখে দিয়ে এক গ্লাস পেস্তা বাদাম বাটা মেশানো দুধ খেয়ে মৌতাতে বসতেন। সপ্তাহে একটা দিন তাঁর ডিমের হালুয়া চাই। একটি দুটি নয়, ষোলটা ডিম দিয়ে সে হালুয়া বানাতে হবে। কম হলে চলবে না। আমাদেরই মাঝে মাঝে ভয় হত এই বয়সে সহ্য করতে না পারলে তো মারা পড়ে যাবে। কিন্তু দেখতাম বুড়া দিব্যি আছে!’
বড় জেদী আর মেজাজী হয়ে গিয়েছিলেন শেষ দিকটায়। জেদ যা ধরতেন ,না করে ছাড়তেন না। সেই জেদের জন্যই শেষ পর্যন্ত …।
Tags: A forgotten musician, Ajoy Biswas, Galper Samay, Tasoddak Hossain Khan, অজয় বিশ্বাস, এক বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতকার

মতামত
আপনার মন্তব্য লিখুন
আপনার ইমেল গোপনীয় থাকবে।